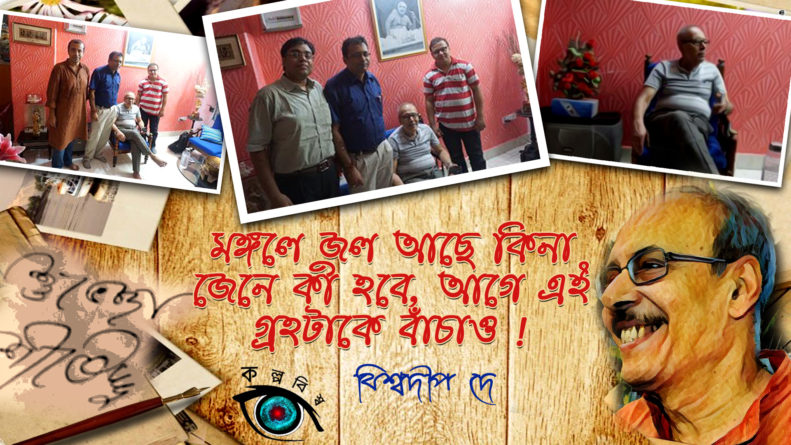শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায়ের সাথে কল্পবিশ্বের আড্ডা
লেখক: বিশ্বদীপ দে
শিল্পী: দেবজ্যোতি ভট্টাচার্য (চিত্রচোর)
“মঙ্গলে জল আছে কিনা জেনে কী হবে, আগে এই গ্রহটাকে বাঁচাও”
তিনি হেঁটে আসছেন। দু-হাতে বাজারভরতি ব্যাগ। মাথায় টুপি। পরনে টি শার্ট-পাজামা। আমাদের দেখেই মুখে খেলে গেল হাসি, ‘ও তোমরা এসে গেছ?’ এমন করে বললেন যেন কতদিনের চেনা। আসলে যে সকলকেই প্রথমবার দেখছেন বোঝা মুশকিল। আমরা ক্যাবলার মতো হাসছিলাম আর অবাক চোখে তাকিয়ে ছিলাম তাঁর দিকে। আমাদের সামনে দাঁড়িয়ে শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায়! সেই ছোটোবেলার ‘গোঁসাইবাগানের ভূত’, ‘মনোজদের অদ্ভুত বাড়ি’, ‘বনি’, ‘পটাশগড়ের জঙ্গলে’ পেরিয়ে বড়বেলার ‘ঘুণপোকা’, ‘পারাপার’, ‘মানবজমিন’, ‘পার্থিব’… একের পর এক বইয়ের পাতা যেন ফড়ফড় করে উড়ে যাওয়ার শব্দ পাচ্ছিলাম। এত বছরের লালিত মুগ্ধতার রেশ কাটিয়ে মুখে বাক্য সরছে না যেন।
এরই মধ্যে এসে বসেছি ওনার সুসজ্জিত চমৎকার ড্রয়িংরুমে। আমি, সুপ্রিয়, দীপ, প্রলয়। আর অবশ্যই জগৎরঞ্জন সর্দার। যাঁর চেষ্টা ছাড়া আজ শীর্ষেন্দুবাবুর সঙ্গে এই সাক্ষাৎ সম্ভব হত না।
দাদুকে দেখে ছুটে আসছিল ছোট্ট নাতনি। আর পালিয়ে যাচ্ছিল কতগুলো অচেনা হুমদো চেহারার লোককে দেখে। তাই দেখে দাদু তো হেসে কুটিপাটি, ‘আরে কাকুগুলো খুব ভালো। এসো এখানে…’ কিন্তু নাতনি তাও কনভিন্সড নয়। শেষমেশ হাল ছেড়ে দিয়ে চেয়ারে গা এলিয়ে স্মিতহাস্যে শীর্ষেন্দুবাবু বললেন, ‘বলো কী সব প্রশ্ন-টশ্ন করবে?’
বললাম, ‘আমাদের পত্রিকা তো কল্পবিজ্ঞানের, তাই প্রশ্নও মূলত…’
—বেশ তো। বলো।
—আপনার ছোটোদের লেখার একেবারে শুরু থেকেই সায়েন্স ফিকশনের একটা ছোঁয়া ছিল। প্রথমে ‘মনোজদের অদ্ভুত বাড়ি’। সেখানে কুমড়ো আর লাউ মিলিয়ে লামড়ো বা গরিলা আর হনুমান মিলিয়ে তৈরি গরিমানের দেখা মেলে। তারপর ‘বক্সার রতন’-কে তো অনেকটাই সায়েন্স ফিকশন-ধর্মী বলা যায়। এরপর যা-ই লিখেছেন অধিকাংশতেই এই মেজাজটা ছিল। সাহিত্যের এই ধারা সম্পর্কে এত আগ্রহ কবে থেকে?
—সে অনেক অল্প বয়স থেকেই। আসলে আমার সায়েন্স নিয়ে বরাবরই একটা আগ্রহ ছিল। কেবল আগ্রহ নয়, বলতে পারো, একটা ফ্যাসিনেশন ছিল। আমি সায়েন্স নিয়ে পড়াশুনো করিনি ঠিকই, কিন্তু পপুলার সায়েন্স পড়তাম। পাশাপাশি সায়েন্স ফিকশনও পড়তাম। তবে সায়েন্স ফিকশনের একটা জিনিসে আমার আপত্তি ছিল। অনেক বিখ্যাত সায়েন্স ফিকশনই ফিউচারিস্টিক। পঞ্চাশ বছর পরে পৃথিবী কোন পথে যাবে তা নিয়ে লেখা। কিন্তু লক্ষ করেছি, সে কথা বলতে গিয়ে টেকনোলজির উন্নতির কথা বলা হচ্ছে ঠিকই, কিন্তু মানুষের ভাষা, চরিত্র, আচার-ব্যবহার এসবও যে পালটাচ্ছে, সেই দিকটা নিয়ে কিছু লেখা হয় না। আমি যখন এই ধরনের লেখা লিখেছি, তখন সেই দিকটা তুলে ধরতে চেষ্টা করেছি। তবে কেবল ছোটোদের লেখাই নয়, বড়োদের লেখাতেও এসেছে কল্পবিজ্ঞান। আমি একটি উপন্যাস লিখেছিলাম—‘বনবিবি ও পাঁচটি পায়রা’। সেটা কিন্তু বড়োদের সায়েন্স ফিকশন। মনে পড়ছে একটা গল্প লিখেছিলাম, সেটাও বড়দেরই, যেখানে ভবিষ্যৎ থেকে মানুষ এসে সাধুভাষায় কথা বলছে। কিন্তু আসলে তারা সাধুভাষায় কথা বলছে না। তারা যে সময় থেকে এসেছে ততদিনে ভাষা এত বদলে গেছে, তা সাংকেতিক হয়ে পড়েছে। অতীতের মানুষদের সঙ্গে কথা বলতে গিয়ে তারা যন্ত্রের সাহায্যে বিশুদ্ধ বাংলায় কথা বলছে। যাই হোক, এরকম অনেক কিছুই আমার লেখায় আমি এনেছি বিভিন্ন সময়ে।
—আপনার লেখায় এই বিজ্ঞানচেতনার পাশাপাশি ভগবান কিংবা ভূতও এসেছে। অর্থাৎ মিরাক্যাল আর সায়েন্স আপনার লেখায় পাশাপাশি অবস্থান করছে। এটাকে কীভাবে ব্যাখ্যা করবেন?
— দ্যাখো আমি অনেক নাস্তিককে মিট করেছি, তারা কিছু না জেনেই বলে দিচ্ছে, ঈশ্বর নেই। অর্থাৎ এটা তাদের বিশ্বাস। এদিক থেকে আস্তিক আর নাস্তিক যেন এক হয়ে যাচ্ছে। একদল স্রেফ বিশ্বাসের ভিত্তিতে বলে দিচ্ছে, ঈশ্বর আছে। অন্য দল বলছে, নেই। ঈশ্বর যে আছে এটা প্রমাণ করার মতোই, ঈশ্বর যে নেই এটা প্রমাণ করাও খুব শক্ত। আসলে আমাদের যে পাঁচটা ইন্দ্রিয়, আমরা যা কিছু অনুভব করছি সব এগুলো দিয়েই। এখন আমার কথা হচ্ছে, এর বাইরেও অনেক কিছু থাকতে পারে, যাকে রিসিভ করার ক্ষমতা আমার ইন্দ্রিয়র নেই। ধরা যাক, এক্ষুনি কেউ যদি একটা রেডিয়ো চালিয়ে দেয়, তাহলে আমরা এই ঘরে বসেই গান বা কথা শুনতে পাব। অর্থাৎ এটা আমার চারপাশের অ্যাটমসফেয়ারেই আছে। আমি শুনতে পাচ্ছিলাম না। রেডিয়ো সেটা আমার কাছে পৌঁছে দিচ্ছে। অর্থাৎ এই যে একটা শূন্যতা আমার চারদিকে রয়েছে, সেখানে কী আছে না নেই আমি সেটা কতটুকু জানি? সুতরাং প্রেতাত্মা বা পরলোক নেই এটা আমি কী করে নিশ্চিত হয়ে বলব? বলার তো আমার অধিকারই নেই। আমার ইন্দ্রিয়ের বাইরে আমার ক্ষমতা কোথায়? ধরো কুকুর অনেক গন্ধ পায়, মানুষ যেটা পায় না। আমরা পিঁপড়ের কথা শুনতে পাই না। আমাদের কানের তা শোনার ক্ষমতা নেই। অনেক পাখি বা জীবজন্তুরই দৃষ্টিশক্তি বা শ্রবণশক্তি আমাদের থেকে তীক্ষ্ণ। কাজেই আমাদের ইন্দ্রিয়ের ক্ষমতা যে সীমাবদ্ধ, সেটা বোঝাই যায়। বিবেকানন্দের লেখায় পড়েছি, ধ্যান করলে মানুষের চৈতন্য আস্তে আস্তে শার্প হতে থাকে। তখন একটা ছুঁচ পড়ার শব্দও আমরা পেতে পারি। কিন্তু সাধারণ অবস্থায় এটা পাওয়া যায় কি? আসলে বিজ্ঞান এখনও অবধি খুব সামান্যই জেনেছে। একটা জায়গার বেশি সে পৌঁছোতে পারেনি। এই যেমন ধরো ইনফিনিটি। একে কি ব্যাখ্যা করা গেছে? তারপর ধরো প্রাণের উৎপত্তি… জড় থেকে প্রাণের চৈতন্য—এই ট্রান্সফরমেশনের ধাপগুলো কী কী? হ্যাঁ, নানারকম থিয়োরি আছে বটে। স্ট্রিং থিয়োরি ইত্যাদি। কিন্তু নিশ্চিত করে…
—আপনার কী মনে হয়, অদূর ভবিষ্যতে বিজ্ঞান এগুলো জানতে পারবে?
সুপ্রিয়র প্রশ্ন শুনে মাথা নাড়লেন শীর্ষেন্দুবাবু, ‘একটা লিমিটেশন তো থাকবেই। মহাকাশবিজ্ঞানের কথাই ধরো। ব্রহ্মাণ্ডের পরিধি কি বিজ্ঞান মাপতে পেরেছে? কোনওদিনও পারবে না। কারণ এর বিরাট ব্যাপ্তি সম্পর্কে ধারণাই করতে পারে না আমাদের ব্রেন…’
—অন্য নক্ষত্রমণ্ডলীতে পৌঁছোনো তাহলে অসম্ভব?
প্রলেয়ের কথা শুনে সামান্য হাসলেন শীর্ষেন্দুবাবু, ‘তাই তো মনে হয়। যদি আলোর বেগেও যাই, তাহলেও সবচেয়ে কাছের নক্ষত্র আলফা সেন্টারাইতে যেতেই সময় লেগে যাবে চার বছর। আমি পৌঁছে গেছি এই বার্তা পৃথিবীতে পাঠাতে লেগে যাবে আরও চার বছর। (হাসি) কাজেই ভেবে দ্যাখো। শুধু ছায়াপথ, যেটায় আমরা রয়েছি, আমাদের ফ্যামিলি… তারই এক এক্সট্রিম পয়েন্ট থেকে অন্য পয়েন্টের দৈর্ঘ্য এক লক্ষ লাইট ইয়ারের চেয়েও বেশি!’
মনে পড়ল ‘পাতালঘর’-এর কথা। সেই সূত্র ধরে জিজ্ঞেস করলাম, ‘আপনার পাতালঘরে যেমন আছে, সেরকম ঘুম পাড়ানোর ব্যাপারটা থাকলে… মানে যাকে হাইবারনেশন বলে…’
—হাইবারনেশনেও হবে না… আইনস্টাইনের থিয়োরিতে আছে যা কিছু আলোর বেগ প্রাপ্ত হবে সেটাই আলো হয়ে যাবে। কাজেই ওই গতিবেগে তুমি চলবে কী করে? তোমার মনুষ্য শরীরটাই তো থাকবে না। মানুষ তো সুপারসনিক গতিটাই সহ্য করতে পারে না। তার জন্যে আলাদা করে ট্রেনিং নিতে হয়। তাছাড়া, ওই ডিসট্যান্স যাওয়ার ফুয়েলটাই বা কী হবে? অনেকেই অ্যান্টি ম্যাটারের কথা বলে। কিন্তু সেটাও ধারণযোগ্য নয়। কাজেই অত দূরের কথা না ভাবাই ভালো। বড়জোর সোলার সিস্টেমের কথা ভাবা যেতে পারে। সেখানেও তো কিছুই করতে পারিনি এখনও। এত বিপুল অর্থ খরচ করে আমরা মহাকাশযান পাঠাচ্ছি অন্তরীক্ষে, তা থেকেই বা কী এমন জ্ঞান আহরণ করা গেছে? তাছাড়া জেনেই বা কী হবে? মঙ্গলে জল আছে কিনা জেনে আমার কী লাভ? আমার মনে হয়, এসব বন্ধ করে সবার আগে এটা খেয়াল রাখতে হবে কী করে এই গ্রহটা বাঁচবে। মানুষ তো আত্মহননের পথে চলেছে। তাই না? সারা পৃথিবী জুড়েই তো অশান্তি চলছে। আর ক’দিন পরে কয়লা সহ সমস্ত জ্বালানিও ফুরিয়ে যাবে। কী হবে তখন? গাড়ির ব্যবহার কমাও। তার জায়গায় সাইকেল ট্র্যাক বানানো হোক। ইচ্ছেমতো গাছ কাটা থামাও। এসব নিয়ে মাথা না ঘামিয়ে খামোখা আকাশ নিয়ে চর্চা করে লাভটা কী?
দেখলাম হতাশা আর বিরক্তি ছেয়ে ফেলছে শীর্ষেন্দুবাবুর মুখ। বোঝাই যাচ্ছিল, সংযম ও নিয়ন্ত্রণের তোয়াক্কা না করে এগিয়ে চলা মনুষ্য সভ্যতা সম্পর্কে একটা তিক্ততা তাঁর ভেতরে কাজ করছে। নিয়মনিষ্ঠ সংবেদনশীল একজন মানুষের পক্ষে সেটাই স্বাভাবিক। খানিকক্ষণের একটা নীরবতা। তারপর যেন খানিক সংবিৎ ফিরে পেয়ে বললেন, ‘যাক। বলো আর কী…’
জানতে চাইলাম, ‘ছয়ের দশকে সত্যজিৎ রায়, প্রেমেন্দ্র মিত্র, অদ্রীশ বর্ধন এবং আরও অনেকে মিলে বাংলা কল্পবিজ্ঞানে একটা জোয়ার এনেছিলেন। কিন্তু পরবর্তী সময়ে সেই জোয়ারটা স্তিমিত হয়ে গেল। মুষ্টিমেয় কয়েকজন ছাড়া বাকিরা সায়েন্স ফিকশনে আগ্রহ দেখালেন না কেন? এই ধারাটা নেগলেক্টেডই রয়ে গেল।’
—আসলে অনেকেই সাহস পায় না। অনেকে চেষ্টা করেও পারেনি। এই যেমন সমরেশ মজুমদার লিখেছিলেন। কিন্তু সেগুলো তেমন ভালো লাগেনি আমার। সুনীলও সেভাবে…
—ওনার নীল মানুষ নামে একটা চরিত্র…
—ওগুলো সেরকম একটা… সুনীলের এই ঘরানার সিরিয়াস লেখা আমার সেভাবে চোখে পড়েনি। হুমায়ুন আহমেদ আমাকে একবার ওর কিছু বই পাঠিয়েছিল। সেগুলো অবশ্য ভালোই ছিল। কিন্তু বেশি সায়েন্টিফিক জার্গন থাকলে যা হয় আর কী… সাধারণ পাঠকের পড়তে অসুবিধে হয়… সেগুলো ওই লেখায় পেয়েছিলাম।
‘এই জিনিসটা একটু জানতে চাইব,’ দীপ বলল, ‘কল্পনা আর বিজ্ঞানের অনুপাতটা…’
মনে পড়ল একই প্রশ্নের উত্তরে অনীশ দেব বলেছিলেন, ‘বিজ্ঞান তিরিশ আর কল্পনা সত্তর।’ শীর্ষেন্দুবাবু অবশ্য সেরকম কোনও অনুপাত বললেন না। কেবল জানিয়ে দিলেন, ‘সাধারণ পাঠকের যাতে বোধগম্য হয়, সেটা সবসময় খেয়াল রাখতে হবে। তা নাহলে কিন্তু মুশকিল হয়ে যাবে। পাঠক আগ্রহ হারাবে।’
সুপ্রিয় এতক্ষণ হয়তো গ্রহান্তরে যাওয়ার বিষয়েই ভাবছিল। তাই পুরোনো প্রশ্নটাই আবার করল, ‘গ্রহান্তরের ব্যাপারটা আরেকটু যদি বলেন। আপনার কি মনে হয় সত্যিই মানুষ কোনওদিনই অন্য গ্রহে গিয়ে থাকতে পারবে না?’
—আমার মনে হয় না সুদূর ভবিষ্যতেও সেটা মানুষ পারবে বলে। অনেক লেখায় দেখা যায়, মানুষ পৃথিবী থেকে গিয়ে অন্য গ্রহে বসবাস করছে। প্রথম কথা সোলার সিস্টেমে সেরকম কোনও গ্রহ নেই। আর অন্য নক্ষত্রে যাওয়ার কথা তো আগেই বললাম। তাছাড়া মানুষ যে যাবে, তার বাক্স-বিছানা-পোঁটলা-পুঁটলি নিয়ে, যাবেটা কোথায়? তার থাকার জন্যে ঠিক এই পৃথিবীর মতোই একটা গ্রহ চাই। সেটা সে পাবে কোথায়? ধরো এমন গ্রহে গেল যেখানে বাতাস পৃথিবীর থেকে ভারী। তাহলে তার শ্বাস নিতে কষ্ট হবে। আবার হালকা হলেও কষ্ট হবে। এই যে স্পেসে গিয়ে অনেকে কিছুদিন কাটিয়ে আসছে, পৃথিবীতে ফিরে তাদের অনেক সমস্যা হচ্ছে। বেশ সময় লাগছে সেই শারীরিক সমস্যাগুলোকে কাটিয়ে উঠতে। কাজেই এই গ্রহান্তরে যাওয়া-টাওয়া আমার নিতান্তই কবির কল্পনা বলে মনে হয়। যদিও পৃথিবীজুড়ে অনেক অসামান্য লেখা বা সিনেমা হয়েছে এই নিয়ে, কিন্তু আমার মনে হয় মানুষ কোনওদিনও এটা পারবে না। এখনও পর্যন্ত একটা জায়গাতেই মানুষ যেতে পেরেছে, চাঁদে, সেটাও অত্যন্ত সন্দেহজনক। আরে চাঁদের যা তাপমাত্রা, তাতে তো অভিযাত্রীদের শরীর পুড়ে যাওয়ার কথা। বলা হয়, তাপমাত্রা নিয়ন্ত্রণ করতে জলের পাইপলাইন ছিল। কিন্তু জলও তো ওই তাপমাত্রায় বাষ্প হয়ে উড়ে যাওয়ার কথা। পাইপও ফেটে যাবে। তাহলে? এরকম অনেক যুক্তি আছে। আসলে তখন অন্যান্য দেশ এতটাই পিছিয়ে ছিল মহাকাশবিজ্ঞানে, তারাও কোনওরকম ট্রেস করতে পারেনি। আমি পড়েওছিলাম এক জায়গায়, রাশিয়া একমাত্র পারত। কিন্তু তারাও নাকি আমেরিকার থেকে টাকা খেয়েছিল। তাই তারা আর উচ্চবাচ্য করেনি। আমার কথা হচ্ছে, আমেরিকা যদি সত্যিই গিয়ে থাকে পরে আর তারা চাঁদে গেল না কেন? এখন তো মহাকাশবিজ্ঞানে অনেক উন্নতি হয়েছে। আসলে ওরা বুঝে গেছে, এখন আর চালাকিটা চলবে না। এটা একটা বিরাট ধাপ্পা। তো চাঁদেরই এই অবস্থা। মঙ্গলগ্রহে যাওয়ার ব্যাপারটা তো আরও কঠিন। কাজেই অন্য গ্রহে যাওয়া-টাওয়া…
দীপ সিনেমার পোকা। ওর এই প্রসঙ্গে মনে পরে গেল ‘মার্শিয়ান’ ছবিটার কথা। বলল, ‘মঙ্গলে যাওয়া নিয়ে কিছুদিন আগে একটা ছবি এসেছিল। মার্শিয়ান। দেখেছেন?’
শীর্ষেন্দুবাবু মাথা নাড়লেন, ‘না, ওটা দেখা হয়নি। তবে অবতার দেখেছি। ভালো লেগেছে।’
প্রলয় এবার প্রশ্ন করল, ‘আপনি বিদেশি সায়েন্স ফিকশন পড়েন?’
শীর্ষেন্দুবাবু স্মিত হেসে ঘাড় নাড়লেন, ‘এখন আর পড়ি না। অনেক সায়েন্স ফিকশনই কেমন ছেলেমানুষি মনে হয়। ক’দিন আগে আর্থার সি ক্লার্কের একটা লেখা পড়লাম। কিছু অংশ বেশ ভালো। আবার কিছু অংশ একদমই ভালো নয়। সব মিলিয়ে বড্ড তরল লেখা বলে মনে হল। তবে এককালে পড়েছি। আসিমভের লেখা বেশ লাগত। ইদানীং আর পড়া হয় না।’
সুপ্রিয় হাসল, ‘এই গ্রহান্তরের কথাগুলো শুনতে শুনতে মনে হচ্ছিল রামরাহার কথা। ‘ভুতুড়ে ঘড়ি’-তে তার দেখা প্রথম পেয়েছিলাম। সে তো ভিনগ্রহ থেকেই এসেছিল। তারপর আর ফিরে যায়নি। পরে ‘গোলমাল’ উপন্যাসে সে আবার ফিরে আসে। পৃথিবীকে বাঁচায়। সে কি আর ফিরবে না?’
মুচকি হেসে শীর্ষেন্দুবাবু জানালেন, ‘সে তো এখনও আছে। সমুদ্রের তলায়। তাকে রেখে দিয়েছি। যদি কখনও কাজে লাগানো যায়।’
তাঁর বলার ভঙ্গিতে সকলেই হেসে উঠলাম। প্রলয় বলল, ‘বাহ। তাহলে অপেক্ষায় রইলাম। যদি কোনও গল্পে আবার রামরাহা ফিরে আসে।’
একটা প্রশ্ন অনেকক্ষণ ধরেই মাথায় ঘুরছিল। এবার করেই ফেললাম, ‘আপনার বেশির ভাগ কল্পবিজ্ঞানের উপন্যাসে একটা জিনিস দেখেছি। প্লটটা সায়েন্স ফিকশন দিয়ে শুরু হলেও পরে লেখাটা মূলত অ্যাডভেঞ্চারের দিকে বাঁক নেয়। অবশ্য ‘বনি’-র কথা আলাদা। ওটা আদ্যন্ত কল্পবিজ্ঞান। কিন্তু বাদবাকি কিশোরপাঠ্য উপন্যাসেই…’
—আসলে আমি বাচ্চাদের বিজ্ঞানের বিষয়ে কৌতূহলটা একটু উসকে দিতে চাই। আবার এটাও চাই, অতিবিজ্ঞান যেন তার মস্তিষ্ককে বেশি পীড়িত না করে। তাহলেই কিন্তু সে আর লেখাটা পড়তে চাইবে না। বেশি খটমট কিছু থাকলে আর তার আগ্রহ থাকবে না। যেমন ‘পটাশগড়ের জঙ্গলে’ লিখতে গিয়ে টের পাচ্ছিলাম বেশ কঠিন হয়ে যাচ্ছে। ওই অঙ্ক-টঙ্ক কষার ব্যাপার ট্যাপার আছে না…?
দীপ বলল, ‘কিন্তু ওগুলো যখন পড়েছিলাম, তখন আমি বেশ ছোট হওয়া সত্ত্বেও দারুণ এনজয় করেছিলাম সেটা মনে আছে। আমি বরাবরই আনন্দমেলা হাতে পেলে আপনার লেখাটা জমিয়ে রেখে দিতাম। একদম লাস্টে পড়ব বলে। ওটাই ছিল প্রধান আকর্ষণ।’
দীপের কথা শুনতে মনে পড়ছিল, এটা আমিও করতাম। কে জানে হয়তো সুপ্রিয় আর প্রলয়ও তাই করত। ছোটোবেলাগুলো সব কীভাবে যেন একবিন্দুতে এসে মিলে যায়। এদিকে ঘড়ির কাঁটা এগিয়ে চলেছে। নির্ধারিত সময় পেরিয়ে গিয়েছে প্রায়। যদিও শীর্ষেন্দুবাবুকে দেখে সেটা মনে হচ্ছে না। তিনি আড্ডায় বেশ জমে গেছেন।
বললাম, ‘আপনার লেখার কথা যখন উঠল, তখন ভূত নিয়ে একটু কথা না হলে ভালো দেখায় না।’
উনি হেসে বললেন, ‘আমি ভূতে বিশ্বাস করি, সেটা তো জানোই। ভূতুড়ে ঘটনার প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা থেকেই সেই বিশ্বাস এসেছে। কিন্তু আমার লেখায় ভূতকে আমি অন্যভাবে এনেছি। আমার লেখায় ভূত হল ভয় ভাঙানো ভূত, ভয় দেখানো ভূত নয়। তাদের দিয়ে আমি মজার সৃষ্টি করি। আমাকে একবার একটি বাচ্চা মেয়ে চিঠি দিয়ে জানিয়েছিল, আমি আগে খুব ভয়-টয় পেতাম, কিন্তু এখন আর পাই না। আপনার লেখা পড়ে আমার ভূতের ভয় কেটে গেছে। (হাসি)
এদিকে সত্যি ভূতের গল্পের খোঁজ পেয়ে দীপের কৌতূহল চরমে, ‘আপনার নিজের যে অভিজ্ঞতা সেটা একটু বলুন না।’
—সে অনেকবার বলেছি। আর বলতে চাই না। বহু জায়গায় বেরিয়েছে।
কিন্তু শীর্ষেন্দুবাবু না বলতে চাইলেও আমরা নাছোড়বান্দা। অন্তত একটা সত্যি ভূতের গল্প শুনতে মরিয়া হয়ে উঠতে তিনি বললেন এক মেমসাহেবের কথা, যে ছোটবেলায় প্রায় পাঁচ-ছ’বছর ধরে তাঁকে নাজেহাল করেছিল। বাড়ি বদলেও তার হাত থেকে নিস্তার পাওয়া যায়নি।
—আমি ছাড়া আর কেউ তার পায়ের শব্দ পেত না। আমিই তার টার্গেট ছিলাম। তবে রোজ নয়, মাঝে মাঝে সে আসত। আমি বরাবরই ঘুমকাতুরে। একবার ঘুমোলে খুব গাঢ় ঘুম হয়। কিন্তু যেদিনই সে আসত আমার ঘুম ভেঙে যেত আচমকা। ঘুম ভাঙার পরই শুনতে পেতাম তার হাই হিলের আওয়াজ। যেন সে আমার ঘুম ভাঙার অপেক্ষা করত। প্রথম প্রথম ন্যাচারালি খুব চিৎকার করতাম। কিন্তু পরে আস্তে আস্তে অভ্যেস হয়ে গেল। সে এক আশ্চর্য ব্যাপার। ওই অভিজ্ঞতা থেকেই আমি বুঝে গেছিলাম ভূত আছে। নিশ্চয়ই আছে।
শীর্ষেন্দুবাবুর বলার ভঙ্গিতে ভর দুপুরেও কেমন রোমাঞ্চ হল। কথা ঘোরাতেই হয়তো দীপ আবার ফিরে গেল সায়েন্স ফিকশনে, ‘আপনার সায়েন্স ফিকশন লেখাগুলোয় একটা মজার অ্যাম্বিয়েন্স থাকে…’
—সেটা ছোটদের লেখায়। বড়দের লেখায় না। ‘বনবিবি ও পাঁচটি পায়রা’ পড়েছ আশা করি। ওখানে কিন্তু…
—অবশ্যই পড়েছি। কিন্তু আমি ছোটদের লেখার কথাই বলছি। ছোটবেলায় যেগুলো পরে কেবল মজাই পেয়েছি, একটু বড় বয়সে সে লেখা পড়তে গিয়ে মনে হয়েছে তাতে যেন একটা প্রচ্ছন্ন ব্যঙ্গ আছে। বলা যায় বিজ্ঞানের প্রতিই যেন… যেন বিজ্ঞান সবটা ধরতে পারছে না। এটা কি ইচ্ছে করেই…
—একদম ইচ্ছাকৃতভাবে এটা করা। বিজ্ঞান অনেক কিছু পারছে। তার সাহায্যে অনেক উন্নতি হচ্ছে মানব সভ্যতার। আবার অনেক কিছু তার নাগালের বাইরেও থেকে যাচ্ছে…
সামান্য নীরবতা। পরপর শুনে যাওয়া কথাগুলো মাথার মধ্যে ঘুরপাক খাচ্ছিল। কী সব প্রশ্ন লিখে এনেছিলাম বটে, কিন্তু এখন সব গুলিয়ে গেছে। আচমকাই তার মধ্যে একটা মনে পড়ে গেল। সেটার সঙ্গে অবশ্য শেষ কথাটার একটা সংযোগ আছে। বললাম, ‘অমরত্ব পাওয়ার জায়গাটাকে আপনি কীভাবে দেখেন? মানুষ কি সেটা কোনওদিন আয়ত্ত করতে পারবে, বিজ্ঞানের সাহায্যে?’
—এটা আমি লিখেছি ‘বনবিবি…’তে। ওখানে আছে অমরত্ব ক্রয় করার ব্যাপারটা। যদিও সেটা ঠিক অমরত্ব নয়। দীর্ঘ দীর্ঘ জীবন। এখন কথা হচ্ছে, এই যে বিরাট একটা সময় ধরে বেঁচে থাকা, এটাই কি মানুষের প্রার্থিত? এ প্রশ্নের উল্লেখ ‘পার্থিব’-তেও করেছি। ধরো, একটা সম্পর্ক পঁয়তাল্লিশ বছর কী সুন্দর টিকে থাকতে পারে। কিন্তু সেটা যদি পঁয়তাল্লিশ হাজার বছর হয়? সম্ভব কি অতদিন ধরে একটা সম্পর্ককে বাঁচিয়ে রাখা? ব্যাপারটা কি একঘেয়ে হয়ে যাবে না? কাজেই অত আয়ু নিয়ে কী হবে? (হাসি) এ প্রসঙ্গে একটা কথা বলি। এই যে সময়… এটাই বা কী? সময় বলে তো আসলে কিচ্ছু নেই। আমরা সেটাকে কল্পনা করে নিচ্ছি গতির পরিপ্রেক্ষিতে। সবকিছু যদি স্থির হয়ে যায়, সময়ও থাকবে না।
আমাদের চারপাশে অবশ্য সবই সচল, তাই সকালটা আস্তে আস্তে দুপুরের দিকে গড়িয়ে যাচ্ছে সেটা টের পাচ্ছিলাম। এবার উঠতে হবে। ওঠার আগে জানতে চাইলাম, ‘নতুন আর কোন বিষয় নিয়ে সায়েন্স ফিকশন লিখবেন ভাবছেন?’
—আমি ওইভাবে ভেবে লিখি না। লিখতে বসে মাথায় আইডিয়া আসে। আমার সব লেখার একই পদ্ধতি। প্রথম লাইনটা যদি আমার পছন্দ হয়ে যায়, লেখা সেখান থেকে শুরু হয়ে যায়। ছোটগল্প থেকে বড় উপন্যাস… এভাবেই লিখেছি। লিখে চলেছি।
এবার ফেরার পালা। দরজা পর্যন্ত এগিয়ে দিলেন। আসার আগে অটোগ্রাফ চাইলাম। গোটা গোটা অক্ষরে খাতায় লিখে দিলেন—শুভেচ্ছা শীর্ষেন্দু।
স্বপ্নপূরণের ঘোর নিয়ে বাইরে বেরিয়ে এলাম আমরা ক’জন।
Tags: দেবজ্যোতি ভট্টাচার্য (চিত্রচোর), প্রথম বর্ষ চতুর্থ সংখ্যা, বিশ্বদীপ দে, সাক্ষাৎকার