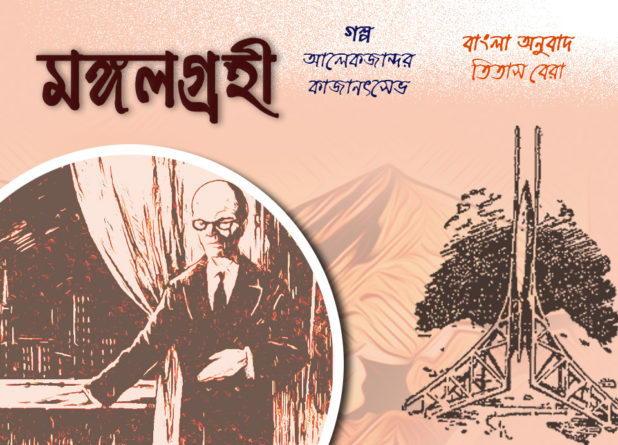মঙ্গলগ্রহী- আলেকজান্ডার কাজানসেভ
লেখক: লেখক - আলেকজান্ডার কাজানসেভ, বাংলা অনুবাদ - তিতাস বেরা
শিল্পী: দেবজ্যোতি ভট্টাচার্য্য (চিত্রচোর)
জিওর্জি সিদভের ফ্রন্টডেকের কেবিনে আলোচনা তখন প্রায় থিতিয়ে এসেছে। আসলে, কেউই সে রাতে ‘মার্সিয়ান ক্যাটাস্ট্রফি’ নিয়ে বিশেষ কথা বলতে চাইছিল না। জাহাজী নাবিক ও মাল্লারা, আর্কটিকের অভিযাত্রী অথবা উত্তর মেরুর আশেপাশে তেলের খোঁজে ঘুরে বেড়ানো মানুষজনকেও যেন একপ্রকার সন্ত্রস্তই দেখিয়েছে। ক্যাপ্টেনেরও একই মত ছিল – উল্কাপাতের পর উত্তর সাইবেরিয়া তার সমস্ত রহস্যময়তা সমেত অতলে তলিয়েছে।
— ‘কিন্তু এবার তোমাকে কিছু একটা করতেই হচ্ছে পেত্রভিচ। আলেকজান্ডার পেত্রভিচই তো, তাই না?’ হাসছিল ক্যাপ্টেন— ‘দেখা যাক আমাদের সায়েন্স ফিকশন রাইটার এ ব্যাপারে চমকদার কিছু বক্তব্য রাখতে পারে কিনা! সবাই হা পিত্যেশ করে বসে আছে দেখতেই পাচ্ছ, মহাজাগতিক আগন্তুক ইত্যাদি বৃত্তান্ত… মজার বটে, এমন কিছু তুমি বলতেই পারো’।
— ‘ইয়া ইয়া!’ জিওর্জি সিদভের ফ্রন্টডেকের কেবিন যেন একটু সরগরম —‘কই হে, আষাঢ়ে গপ্প কিছু ছাড়ো তো’।
তা, আলেকজান্ডার পেত্রভিচ হিসেবে এ ধরণের ঠাট্টা আমি গায়েই মাখিনি। উল্টে যেন তামাশাই করেছি — ‘কতটা আষাঢ়ে চাইছ? তৈগার উপরে গ্রহান্তরের মহাকাশযানের মত? লোকে এসব বিশ্বাস করে?’
—‘ইয়াঙ্কিরা কি বলে জান?’ ক্যাপ্টেন তখনও হাসছিল—‘ঈশ্বর এবং টাকা ছাড়া আমরা আর কোনো কিছুতেই বিশ্বাস রাখিনা। প্রথম ব্যাপারটা ঠিক জানি না, কিন্তু দ্বিতীয়টা নিয়ে তো কোনো সন্দেহই নেই।
— ‘ঠিকই, অস্বীকার করা যায় না’ বলে উঠল পাইলট। আমি লক্ষ্য করলাম ওর কুকুরের চামড়ার জুতো আর ওভারকোটে কুচি কুচি বরফ। জিওর্জি সিডভের এই আর্কটিক অভিযানে ওর ঘাড়ে বিশেষ দায়িত্ব চেপেছে। আর কেউ না জানলেও আমি জানি যে ওর কাজ হ’ল সেই সমস্ত দ্বীপ খুঁজে বার করা যেখানে বিমানবাহিনীর চাহিদা মতন রানওয়ে তৈরী করা যাবে।
কেবিনের এক কোণে বসে নেতায়েভ এতক্ষণ সব শুনছিল। ছোকরা গম্ভীরমুখে বলে উঠল, —‘উঁহু, এসব থাক, একটা গল্প শোনাও আমাদের। যা একদমই বিশ্বাসযোগ্য হবে না, নিঁখুত নিটোল গল্প।’
— ‘তুমি বিশ্বাস করো এসব?’ গল্পটা বলার আগে যেন একপ্রকার মেপে নিতেই চেয়েছি। উত্তর অক্ষাংশের এই প্রান্তে নানান আজগুবি ঘটনার কথা হামেশাই শোনা যায়। বিচিত্র প্রাণী ও ভুতুড়ে কান্ড। আসলে আমিই বোধহয় কৌতুহল চেপে রাখতে পারছিলাম না। ঠোঁটের কোণে হাসিটুকু ঝুলিয়ে রাখতেও ভুলিনি যেমন সমস্ত রোমাঞ্চকর গল্পের প্রতিটি পাতা উল্টোনোর সময় পাঠকদের যেরকম অবস্থা হয়।
অবশ্য এ গল্পের শুরু আজকে নয়। মস্কোর কাছাকাছি ত্যুশিন্যিয়ে শহরের চাকলভ সেন্ট্রাল এরো ক্লাবের টেবিল থেকেই এ গল্পের শুরু বলা যেতে পারে। সাক্ষী হিসেবে আরো বলা যেতে পারে এরো ক্লাবের সাদামাটা ছাতাপড়া সিলিং এবং টেবিলক্লথের কালো কালির দাগ।
যদ্দুর মনে করতে পারছি, সেদিন আমার ফ্লাইং ক্লাবে ডিউটি ছিল। না, আমি পাইলট নই, এবং এতে অবাক হওয়ারও কিছু নেই। ফ্লাইং ক্লাবের ব্যাপারটা সম্পর্কে বলতে পারি যে, মাত্র কয়েক বছর আগেই এটা চালু করা হয়। কসমোনটিক্সে উৎসাহী কিছু মানুষজন এক জায়গায় জড়ো হলে যা হয় আর কি! উদ্দেশ্য বলতে বিভিন্ন গ্রহে পাড়ি দেওয়ার ব্যাপারটা প্রমোট করা। এই কিছুদিন আগে অবধি লোকজন যেন এসব নিয়ে হাসাহাসিই করেছে একপ্রকার। আমাদের লুনাটিকস বলাও শুরু হয়েছিল, যেহেতু চাঁদে পাড়ি দেওয়ার ব্যাপারটাও আমাদের ভাবিয়েছে। কিন্তু আমরা ধীরে ধীরে আমাদের শক্তি বাড়িয়েছি, কসমোনটিক্স নিয়ে প্রচার চলেছে, প্রচুর প্যামফ্লেট। মহাকাশযাত্রার ব্যাপারে যারা উৎসাহী তাদের মধ্যে চিঠিপত্র বিলি ও যোগাযোগ রাখা। সংগঠন বাড়তে থাকায় বেশ কিছু কমিটিও তৈরী করে ফেলা হয়েছে যেমন, কসমোনেভিগেশন, রকেট সায়েন্স, জ্যোতির্বিজ্ঞান, কসমোবায়োলজি, রেডিও কন্ট্রোল ইত্যাদি। এখন আর হাসাহাসির জায়গায় ব্যাপারটা নেই। বিজ্ঞানী, ইঞ্জিনিয়ার, পাইলট, থেকে শুরু করে ছাত্র, লেখক, তরুণ যুবক-যুবতী, বয়স্ক লোকজন, মানে মোটমাটু যারা স্বপ্ন দেখতে পারে, অনেকেই নাম লিখিয়েছে। পাল্লা দিয়ে বেড়েছে সংগঠনের কাজ।
অন্যতম সংগঠক হিসেবে সেই দিন আমার ফ্লাইং ক্লাবে ডিউটি ছিল। সেটা স্পুটনিক যাত্রার বছর। জডরেল ব্যাঙ্ক রেডিও টেলিস্কোপে ধরা পড়েছে সেই সিগন্যাল। যদ্দুর মনে পড়ছে সেদিন আমি জনাদুয়েক ছেলেমেয়ের সঙ্গে এই নিয়ে কথাবার্তা চালাচ্ছিলাম। মঙ্গলগ্রহে অভিযান নিয়েও কথাবার্তা হয়। এ বাদে গ্রহান্তরে অভিযান সংক্রান্ত কিছু সাপ্তাহিক চিঠিপত্রও আমি পড়ছিলাম।
যেমন একজন লিখেছে— আঠারোয় পা দিয়েছি, সদ্য ইশকুল পর্ব মিটেছে। এখনও অবধি কিছুই ভেবে উঠতে পারিনি, কিন্তু সায়েন্সের জন্য মনে হয় অনেক কিছুই করে উঠতে পারব। শুনছি নাকি একটি কুকুরকে উপগ্রহ মারফত মহাকাশে পাঠানোর তোড়জোর হচ্ছে। আমি দাবী করছি যে, কুকুরের বদলে আমিই চলে যেতে পারি। পরীক্ষা নিরীক্ষার জন্য নিজেকে প্রস্তুত বলেই মনে হয়, রেডিও ব্রডকাস্টে উপর থেকে যা যা ঘটছে সবই বলতে পারব, গোটা পৃথিবীকে একঝলকে দেখাও হবে।
একজন মহিলা চিঠি পাঠিয়েছেন— “আমার বয়স ছেচল্লিশ। ঘরদোরের কাজ ছাড়া কিছুই পারি না। আমার মনে হয় আমিই উপযুক্ত। মহাকাশযাত্রা মানব দেহের উপরে কি কি প্রভাব ফেলছে, সেই ব্যাপারে… তাছাড়া ফিরে আসার কথা এখনই ভাবছি না, সমস্ত রকেটই যে ফিরে আসবে তাও তো আর সম্ভব নয়…”
ট্রান্স বৈকাল রেলওয়ের এক এঞ্জিনিয়ার লিখেছে— “এঞ্জিনিয়ারিং ভালবাসি, কলকব্জাও। শেখার ইচ্ছেও এ বয়সে পুরোদস্তুর। আমার মনে হয় মহাকাশযানে আমার মতই কাউকে দরকার…”
এরকম প্রচুর চিঠিপত্র প্রতিদিন আমরা পাচ্ছিলাম। বোঝাই যাচ্ছে যে, অ্যাদ্দিন ধরে প্রচারের ফলে মহাকাশযাত্রা ব্যাপারটা উৎসাহীদের মধ্যে ভালোই সাড়া ফেলেছে। অবশ্য হবে নাই বা কেন? অজানাকে জানার ইচ্ছেটা তো আর নতুন নয়। তুষারঝড়, হিমবাহ, আনচার্টেড ম্যাপ এবং নিত্যনতুন অজানা বিপদকে তুচ্ছ করে মেরু অভিযান, নিরক্ষীয় স্রোত এবং সামুদ্রিক ঝড় পেরিয়ে নতুন দেশ খুঁজে বার করার নেশা, কঠিন বিপদসঙ্কুল বরফের চড়াই উতরাই পেরিয়ে, পাহাড়চুড়োর অশান্ত বাতাসে ভর করে, চোখ ধাঁধিয়ে দেওয়া ঔজ্জ্বল্যের আকাশ ছুঁয়ে থাকা, এই অতিক্রমণের উদ্দেশ্যই বা কি! মে বি বিকজ ইট ইজ দেয়ার কিংবা কোনো একটা অদম্য শক্তির টানই হয়তো আছে অথবা শুধুমাত্র নতুনত্বের খোঁজেই বলা যেতে পারে একপ্রকার – চিঠিপত্র গুলোও সেরকমই বলছে যেন। অন্ততঃ ছাতাপড়া সিলিং এবং টেবিলক্লথের কালো দাগের দিকে তাকিয়ে এসবই আমি ভেবে চলেছিলাম।
কিন্তু এরপরই চিন্তায় ব্যাঘাত ঘটে কারণ ফ্লাইং ক্লাবের সামনের সবুজ ঘাসজমি পেরিয়ে একজনকে হেঁটে আসতে দেখা যায়। ত্যুশিনিয়ের চাকলভ ফ্লাইং ক্লাবের ডিউটিপ্রাপ্ত অফিসার হিসেবে আমি, এবং আগন্তুকের মাঝে ছিল একটি কাঁচের জানালা যে জানলার ক্যানভাসে ওর অদ্ভুতভাবে হেঁটে চলা ধরা পড়ছিল। মস্তিষ্কের সিগন্যাল অনুযায়ী আমি যেন জানতামই যে ও আমার কাছেই আসছে।
ফলে ফ্লাইং ক্লাবের দরজা ঠেলে ও যখন ঢুকল সেটা তখন আমাকে খুব একটা বিস্মিত করেনি। কিন্তু আলেকজান্ডার পেত্রভিচ হিসেবে আমি বুঝতে পারছিলাম যে কোথাও একটা আসোয়াস্তি ঘটছে। ওর দেহের তুলনায় অসমঞ্জস হাত পা, বেশ বড়ো মাপের টাক মাথা, বেঁটেখাটো চেহারা, কিন্তু এসব ছাপিয়ে ওর বুদ্ধিমত্ত চোখ, প্রচন্ড হাইপাওয়ারফুল চশমা, এবং সে চোখে সামান্য হতাশার ছোঁয়াই যেন সবচেয়ে আগে আমার কাছে ধরা পড়ল।
যদ্দুর মনে পড়ছে, ও ওর ঐ অদ্ভুত চশমার ভেতর দিয়ে আমাকে দেখছিল, এবং স্বীকার করতেই হবে যে আমি কিছুটা ইম্প্রেসড হয়েই যেন চেয়ারটা এগিয়ে দিয়েছি, —‘বাজোস্থা পেরিসিয়াচ। দয়া করে বসুন।’
টেবিলের উপর একটা মোটা পান্ডুলিপি রেখে সে আমার দিকে তাকিয়ে হাসল। হয়তো ভাবছিল যে এরকম পান্ডুলিপি প্রতিদিনই শয়ে শয়ে পেতে আমি অভ্যস্ত।
— ‘না, না, সাহিত্যসংক্রান্ত কোনো আলোচনার জন্য আমি আসিনি। এ পান্ডুলিপিও জানবেন ছাপাবার জন্য নয়!’ আমি ওকে দেখে চলেছিলাম। এর উদ্দেশ্য নিশ্চয়ই গ্রহান্তরে পাড়ি জমানো। আমি ভাবছিলাম আন্দাজমতন ও’র যা বয়েস সেই অনুযায়ী নতুন কিছু ওকে শিখতে বলার মানে হয় না অবশ্যই।
ও যেন পড়েই ফেলতে পেরেছিল আমার দ্বিধাটা। যদিও কিভাবে এটা ঘটল তা আমার কাছে পরিষ্কার নয় কিন্তু সে যেন এরপর বিনীত ভাবেই জানিয়েছে যে সে কোনো কসমোনাট নয়, ভূতত্ববিদও নয়, ডাক্তার কিংবা ইঞ্জিনিয়ারও নয়। যদিও চাইলেই সে এর মধ্যে যে কোনো একটা কিছু সে হতে পারত। তার যোগ্যতা প্রশ্নাতীত, তার শুধুমাত্র ইচ্ছা, প্রথম যে মহাকাশযান গ্রহান্তরের যাত্রীদের নিয়ে মঙ্গলে পাড়ি দেবে, সেখানে যেন তার জন্য একটি আসন বরাদ্দ থাকে, কারণ সে অ্যাডভেঞ্চার নয়, আদতে ফিরে যেতে চায়।
ফিরে যেতে চায়!
আমার আসোয়াস্তি বাড়ছিল। মনে পড়ল ১৯৪০ নাগাদ ওরা এরকমই আরেকজনের কথা চিঠিতে জানিয়েছিল। স্ভেরদোভস্কের কাছাকাছি একট ডিপার্টমেন্টাল স্টোরের ম্যানেজার চিঠি দিয়ে কর্তৃপক্ষকে জানিয়েছিলেন যে তাঁকে যেন মঙ্গলে ফেরত পাঠানো হয়। ওরা বলেছিল ভদ্রলোকের আচরণ অন্যান্য সব অর্থেই স্বাভাবিক বলে মনে হয়েছিল।
আগন্তুক একটু হাসল। আমি ওর চশমার কাঁচ মারফত বুঝতে পারছিলাম যে ও ফের আমার মনের কথা জেনে ফেলেছ। ভদব্লিন! হয়তো মঙ্গলের পাতলা বায়ুমন্ডল শব্দ তরঙ্গ পরিবহণের উপযোগী নয় বলে ওরা টেলিপ্যাথিই আবিষ্কার করে ফেলেছে! অবশ্য নিজেকে বোঝালাম যে, শুধু ওই একমাত্র তো নয় আমিও বোধহয় একপ্রকার ওর মনের কথা বুঝতে পারছি…তো এরচেয়ে ওকে পাগল ভাবাই নিরাপদ।
—‘ইয়া! খুব স্বাভাবিক যে আমাকে প্রথমে পাগলা গারদেই পাঠানো হয়েছিল, তবে পরে বুঝতে পেরেছি যে লোকজনকে ব্যাপারটা বোঝাতে যাওয়া একপ্রকার পন্ডশ্রমই বটে’।
আলেকজান্ডার পেত্রভিচ হিসেবে আমি তখনো ভেবে চলেছিলাম যে এর কথাই হয়তো যুদ্ধের আগে ওরা লিখেছিল। যদিও আগন্তুক সেটাকে পাত্তা না দিয়ে বলে চলল— ‘আমি রাশিয়ান, ইংলিশ, ফ্রেঞ্চ কিংবা ডাচ, জার্মান, চাইনিজ কিংবা জাপানীজ, যেকোনো ভাষাতেই এই পান্ডুলিপিটা লিখতে পারতাম।’
সৌজন্যের খাতিরে এরপর যেন পান্ডুলিপির প্রথম পাতাটা উল্টোতেই হয়েছে। নানারকম সাংকেতিক সব চিহ্ন পাতায় পাতায়। এমন চিহ্ন আমি কখনো দেখিনি। এগুলো কি? আশ্চর্য! মনোবিকার নাকি!
—‘বুঝতেই পারছেন যে, বাস্তবিক যেকোনো অনুভূতিসম্পন্ন কারোর পক্ষেই এটা লেখা একটা অসম্ভব ব্যাপার’, আগন্তুক বলে চলেছে— এরকম একটা ভাষা আবিষ্কার করা, যা কিনা এত নমনীয়, এত অনন্য ভাবে যা বিবিধ বোধকে প্রকাশ করে এবং অন্যকে বোঝাতে পারে এইরকম কোনো কিছু স্রেফ একজনের পক্ষে আবিষ্কার করা একপ্রকার অসম্ভবই বলা যায়। ধরা যেতেই পারে এই পান্ডুলিপির ভাষা শুধুমাত্র সেই জনজাতির প্রতিনিধিদের পক্ষেই লেখা সম্ভব যা দূরের কোনো জগতে কোনো একসময় হয়তো ছিল।
—‘কিন্তু এটা পড়ব কিভাবে’, আমার পক্ষে আর কৌতুহল চেপে রাখা সম্ভব হচ্ছিল না।
বলা মাত্রই দেখলাম ওর চোখে কৌতুক খেলে গেল। চশমার কাঁচের ভেদ করে আমি, অর্থাৎ আলেকজান্ডার পেত্রভিচ এটুকুই অনুধাবন করতে পারছিলাম।
—‘আপনি নিশ্চয়ই একমত হবেন যে গত এক শতাব্দীতে আপনাদের পৃথিবীতে সামাজিক অদলবদল ঘটেছে চূড়ান্তভাবে। প্রায় বিস্ফোরণই ঘটে গেছে বলা যায়। শক্তির নিত্যতা সূত্রের সেইসব দিন থেকে বর্তমানের পারমাণবিক শক্তির প্রয়োগ, আদিম পেগানিজম থেকে ক্রমে সেই সমস্ত মেশিনের আবিষ্কার যা কিনা হিউম্যান ব্রেনকেও ছাপিয়ে যাচ্ছে কোথাও না কোথাও। এটা ভেবে হয়তো আনন্দই পাচ্ছি যে আমি এই সময়ে রয়েছি। এমন সবুজ সময়ে, আশার কথা এটাই যে এত বিস্তর যুদ্ধবিগ্রহের পরও পৃথিবীর বায়ুমন্ডল কিংবা জলীয়স্তরের খুব বিশেষতঃ কিছু হেরফের হয়নি, আর হবেও না মনে হয়’।
—‘তোমার মনে হয় যে ইলেক্টট্রনিক কম্পিউটার তোমার পান্ডুলিপি পড়তে পারবে’?
—‘হয়তো পারবে। হয়তো এটাও বুঝতে পারবে যে একমাত্র কে এটা লিখে থাকতে পারে’।
আমি বোঝার জন্য তৈরী ছিলাম। যেন আমি বুঝেও গেছিলাম যে কে এটা লিখে থাকতে পারে। গোটা ব্যাপারটার অস্বাভবিকতায় আমি এতটাই অপ্রস্তুত ছিলাম যে আমার হাত একপ্রকার কাঁপছিলই বলা যায়। আমি ভাবছিলাম যে কে এই পান্ডুলিপি পড়তে চাইবে, সারা দুনিয়া নাকি শুধুমাত্র কিছু উন্মাদ বিশেষজ্ঞ?
চশমার পিছন থেকে ওর উজ্জ্বল চোখ আমাকে দেখছিল। আমি স্পষ্ট বুঝতে পারছিলাম যে হয়তো ও কোনোভাবে আমার মনে কি চলছে সেটা পড়ে ফেলতে পারছে।
এরপর ও চলে যায়। যাওয়ার আগে কথা দিয়ে যায় যে ছ মাস পরে এই সেন্ট্রাল এরো ক্লাবেই আমাদের মধ্যে ফের দেখা হবে। আমি আলেকজান্ডার পেত্রভিচ…
—‘দাঁড়াও দাঁড়াও’! নেতায়েভ উত্তেজিত—‘ম্যানুস্ক্রিপ্টটার কি হল’?
জিওর্জি সিদভের ফ্রন্টডেকের কেবিনরুম হঠাৎই সরগরম। যদিও এতক্ষণ সকলে চুপ করে আমার কথাই শুনছিল।
—‘যাহোক, বেড়ে গল্পটা বানিয়েছে বলতে হবে’। কেউ একজন কৌতুক করে বলে উঠল। নেতায়েভ বিরক্ত।
—‘আমার মনে হয় ঘটনাটা এখানেই শেষ হচ্ছে না’, ক্যাপ্টেন খুব আশাভরা দৃষ্টিতে আমার দিকে তাকালেন।
—‘হ্যাঁ, ব্যাপারটার এখানেই শেষ হচ্ছে না, তাছাড়া ওর সঙ্গে ফের দেখাও তো হবে’।
—‘ম্যানুসক্রিপ্টটা তোমার কাছে আছে? একবার দেখতে পারি’? নেতায়েভ বলে উঠল।
—‘না ম্যানুস্ক্রিপ্ট আমার কাছে নেই। ওটা তো আর আমার নয়। তবে ঘটনার আরো কিছু বাকি আছে’, আমি বলে চললাম। সেই আগন্তুক চলে যাওয়ার বেশ কিছুদিন পর একজন মস্তবড় বিজ্ঞানী আমাদের রাইটার্স ইউনিয়নে এসেছিলেন। ভদ্রলোকের ম্যাথমেটিশিয়ান হিসেবে খ্যাতি আছে। খুব ইন্টারেস্টিং লোক বলতে পারো। টেনিস খেলেন, অ্যাথলেটিক্সও, দুর্দান্ত চেস প্লেয়ার, লিটারেচর ব্যাপারটা খুব ভালো বোঝেন কারণ এই বিষয়ে আমাদের মধ্যে প্রায়শই আলোচনা হয়। ষোলো বছর বয়সে ইউনিভার্সিটিতে যান, এরপর কুড়ি বছর বয়স অবধি ওখানেই পড়াশোনা, আঠাশ বছর বয়সেই একজন ইলেক্টেড অ্যাকাডেমিশিয়ান। খ্যাতনামা অধ্যাপক।
—‘আমি বুঝেছি কার কথা বলা হচ্ছে’। নেতায়েভ বলে উঠল।
আমি হাসলাম। চিনতে পারাটা স্বাভাবিক। এই বিজ্ঞানী আমাদের জানিয়েছিলেন ইলেকট্রনিক কম্পিউটারের কথা। হ্যাঁ, সেই সব সাইবারনেটিক মেশিনের কথাই বলছি, যা কিনা সবচেয়ে জটিল অঙ্কও নিমেষে কষতে পারে। আলেকজান্ডার পেত্রভিচ হিসেবে আমি বলতে পারি এধরণের অঙ্ক কয়েক জেনারেশনেও কেউ করে উঠতে পারবে না। এই কম্পিউটর যুক্তিনির্ভর সমস্যাও সলভ করতে পারে। ইলেকট্রনিক মেমরির দৌলতে এক ভাষা থেকে অন্য ভাষায় অনুবাদও করতে পারে। বুঝতেই পারছ এসবই বিজ্ঞানী আমাকে জানিয়েছিলেন। ও হ্যাঁ, সেদিন আসলে গাড়িতে আমরা একই সঙ্গে ফিরছিলাম।
অবশ্য ওঁর আরেকটি অভিজ্ঞতার কথাও জানিয়েছিলেন। অ্যাকাডেমি অব সায়েন্সের সুপার কম্পিউটারের কথা। সেটি চেস খেলতে পারে। এটাও বলতে পারি, এটি নাটকের কুশীলবদের চরিত্র গুলো জেনেই একটা নাটকের প্লট আন্দাজ করতে পারে। বেশ মজার বলতে পারো। যখন নাটকের প্লট আপাত দৃষ্টিতে সহজ সরল, কে ভালো আর কে খারাপ, কোন চরিত্র কাকে ধোঁকা দিচ্ছে, মেশিন কিন্তু প্রত্যেকবারই ঠিক ঠিক আন্দাজ করেছে।
কিন্তু অধ্যাপক আমাকে এটাও জানান যে, মেশিনটার আরো একটা সাংঘাতিক ক্ষমতা আছে। যেহেতু সে লক্ষ লক্ষ ক্যালকুলেশন চোখের নিমেষে সেরে ফেলতে পারে, তাই যেকোনো এনক্রিপটেড সংকেতকেও সে পড়ে ফেলতে সক্ষম। বিজ্ঞানী লক্ষ্য করেছিলেন, এনসিয়েন্ট হায়ারো গ্লিফিক্সকেও এই মেশিন পড়ে ফেলছে এক নিমেষে যা কিনা আগের শতাব্দীর বিজ্ঞানীদের পক্ষে ধরা ছোঁয়ার বাইরে ছিল।
—‘বুঝতেই পারছ যে আমি এর অপেক্ষাতেই ছিলাম’।
আমি ধীরেসুস্থে ওঁকে সেই আশ্চর্য আগন্তুকের কথা জানিয়েছি। তার পান্ডুলিপির কথাও। অধ্যাপক সব শুনে হো হো করে হেসেছেন, কিন্তু বিদায় নেওয়ার আগে বলেছেন, কিছুটা কৌতুক করেই বোধহয়, বেশ তো পেত্রভিচ, আজ রাতে আমাদের কোনো কাজ সম্ভবতঃ নেই। তুমি যদি আমার আকাডেমি অব সায়েন্সের লোকজনকে বোঝাতে পারো, বুঝতেই পারছ, কাজপাগল ছেলেপুলে সব, হয়ত তুমি ম্যানুস্ক্রিপ্টের প্রথম কিছু পাতা ডিসাইফার করতে পারলে –
—‘এবং শেষ পাতা গুলোও’।
ফের হো হো হাসির আওয়াজ— চেষ্টা করে দেখতেই পারো পেত্রভিচ, কিছু উদ্ধার করতে পারো কিনা।
এরপর খুব স্বাভাবিক ভাবেই ত্যুশিন্যিয়ের চাকলভ সেন্ট্রাল এরো ক্লাবের ডিউটি অফিসার, এই আমি, অর্থাৎ আলেকজান্ডার পেত্রভিচ ম্যানুস্ক্রপিটটি নিয়ে অ্যাকাডেমি অব সায়েন্সে হাজির হই। সেই রাতেই। ওখানে যাওয়ার পরই বুঝতে পারি ওরা সবাই যেন অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করে আছে। এটা আমি বুঝতে পেরেছিলাম কারণ পান্ডুলিপি হাতে পাওয়ার পরই সক্কলে মিলে দ্রুত হাতে ওটার পাতা ওল্টাতে শুরু করে। এবং সেই সঙ্গে তুমুল আলোচনা, ডিক্রিপশন প্রোগ্র্যাম হিসেবে কি কি সেট করা যায়। ওফ, এই ডিক্রিপশন প্রোগ্র্যাম! না জানি কতবার বদলাতে হয়েছে।
—‘সেকী! পান্ডুলিপির সংকেত উদ্ধার হয় নি’! নেতায়েভ উত্তেজিত।
—‘প্রথমে কিসুই বোঝা যায় নি। অ্যাকাডেমি অব সায়েন্সের সেই উজ্জ্বল তরুণেরাও হতোদ্যম হয়ে পড়ছিল যেন। সেই অধ্যাপক হাসাহাসি করছিলেন। যেন এটা কোনো ল্যাঙ্গুয়েজই নয়, যদিও নতুনতর ডিক্রিপশন প্রোগ্র্যাম ব্যবহারে উনি বাধা দেন নি। এদিকে দিনের পর দিন চলে যাচ্ছে, ক্রমশঃ ব্যাপারটা হয়তো পন্ডশ্রমের দিকেই গড়াচ্ছে মনে হল’।
অধ্যাপক বলছিলেন শহরের রাতের আলোর মধ্যেও কবিতা খুঁজে পাওয়া সম্ভব এই মেশিনের সাহায্যে, কিন্তু পান্ডুলিপির পাঠোদ্ধার আর কিছুতেই হয় না। এদিকে বুঝতেই পারছ লোকজন আড়ালে বিবিধ মন্তব্য করছে। এমনটাও শোনা যাচ্ছিল যে, আমরা হয়তো বাজে কাজে সময় নষ্ট করছি। আরো গুরুত্বপূর্ণ কাজ যেমন নদীবাঁধের জল পরিশ্রুতকরণের হিসেবের কাজে মেশিনটাকে ব্যবহার করলে হয়তো ভালো হত। ফলে কিছুটা দেরীই হয়েই যায় একপ্রকার, কিন্তু বুঝলে, তারপরেই একদিন হঠাৎ করেই যন্ত্রটা ডিক্রিপ্ট করতে থাকে পান্ডুলিপি।
—‘তুমি পড়েছ’? নেতায়েভ যেন শ্বাসরুদ্ধ।
—‘হ্যাঁ পড়েছি। প্রথম কয়েকটি পাতা’।
—‘কি! কি লেখা ছিল তাতে’?
—‘তা দেখো, আলেকজান্ডার পেত্রভিচ হিসেবে আমি বলতে পারি, এই ইলেকট্রনিক কম্পিউটার যা কিনা হিউম্যান ব্রেনের থেকেও কয়েক গুণ বেশী ক্ষমতা ধরে, সে যখন এই ডায়েরীর মানে উদ্ধার করল, দেখা গেল, এই মার্সিয়ান, যার স্পেসশিপ কিনা এক দুর্ঘটনায় আছড়ে পড়ে তৈগার টুঙ্গুস্কায়, ১৯০৮ সালে – সেসবেরই বিবরণ’।
আমার অবস্থাটা আন্দাজ করতে পারো নিশ্চয়ই। আমি যেন পড়ছি সেই বিবরণ। শুধু পড়ছিই না, যেন এক পরিত্যক্ত অন্য গ্রহের প্রাণীর চোখ দিয়ে আমাদের জগতকে দেখছি। অন্য জগতের গাছপালা, তাদের অদ্ভুত হতচকিত করে দেওয়া সৌন্দর্য— সেইসবের বিবরণ। তারপর একসময় সে হয়ত দেখেছিল বিভিন্ন প্রাণীদের, যার প্রত্যেকটিই নিজগুণে সুন্দর, এবং তারপরই হয়তো সে মানুষদের সাক্ষাৎ পায়। কতটা অবাকই না তাকে হতে হয়েছে! এই মানুষরা যেন তার জগতের মতই। বাস্তবিক বোধসম্পন্ন। এরা নিজেদের মধ্যে কথাবার্তা চালায়, শব্দতরঙ্গের মাধ্যমে চিন্তাভাবনার আদানপ্রদান করে। আন্দাজ করতে পারি যে মানুষের কথা বলার ভাষাকে নকল করে হয়তো কথা বলার চেষ্টাও করেছে। চেষ্টা করেছে যে সে কে তা জানানোর, হয়তো বলেওছে। সাইবেরিয়ার ওদিককার লোকজন এবং কোনো সার্জেন্ট হয়ত তাকে উটকো বিদেশী বলে ঠাউরেছে এবং সোজা পাগলাগারদে চালান দিয়েছে। সিবস্কি মানুষজন তাকে বুঝতে পারেনি। তাদের পারার কথাও নয়।
প্রায় অর্ধশতাব্দী ধরে গ্রহান্তরের আগন্তুক আমাদের মধ্যেই থেকেছে। প্রতিদিন ডায়েরীতে লিখে রেখেছে তার অভিজ্ঞতা। আমরা এখনো পুরোটা ডিসাইফার করে উঠতে পারিনি, কিন্তু আমি আলেকজান্ডার পেত্রভিচ হিসেবে কথা দিচ্ছি যে, আমি পুরোটাই অনুবাদ করে বিস্তারিত লিখে জানাব। এটা পড়ে জানা যাবে একজন মার্সিয়ানের চোখে পৃথিবীর মানুষের কথা, যারা হাজার হাজার বছর আগে সভ্যতার চূড়ান্ত সীমায় পৌঁছেছিল।
আমরা মার্সিয়ানের চোখে দেখতে পাব আমাদের মিথ্যে মারামারি ক্লেদ ঘৃণার বাস্তব। তার চোখ দিয়ে দেখব দু দুটো বিশ্বযুদ্ধ। সে অবশ্যই দেখেছে রক্তের মাধ্যমে মীমাংসার ব্যাপারটা। বুঝতেই পারছ, বিবিধ অত্যাচারের খতিয়ান। মার্শিয়ানের ডায়েরী পড়লে পৃথিবীকে ওর দৃষ্টিতে দেখতে পাওয়া যায়।
—‘আর শেষ পাতাগুলো’?
—হ্যাঁ, ডায়েরীর শেষ পাতা গুলোর দিকেও নজর রাখা যেতে পারে। আলেকজান্ডার পেত্রভিচ হিসেবে এটুকু বলতে পারি যে শেষের দিকে সে লিখেছে কিভাবে তার নিজের ইচ্ছের শহর সে গড়তে চেয়েছিল। আমরা জানতে পেরেছি, তার মতামত আমাদের সঙ্গে থেকে বদলাতে শুরু করে। একসময় সে বুঝতে পারে যা অর্জন করতে মার্শিয়ানদের লক্ষ লক্ষ বছর লেগেছে, সেটা আমরা এই সোভিয়েতে এক শতাব্দীতেই অর্জন করে ফেলতে পেরেছি। সে এই কথা তার মার্শিয়ান বন্ধুদের জানাতে চায়। সে জানাতে চায়, কারণ সে বিশ্বাস করছে যে এইভাবে মার্শিয়ানদের আরো বহুদিন বাঁচিয়ে রাখা যাবে। আমরা ওর ডায়েরী পড়তেই পারি আর ভাবতেই পারি যে সে কিরকম মানুষ, থুড়ি মার্শিয়ান ছিল, তাই না?
অবশ্য ওর সঙ্গে ভবিষ্যতের সাক্ষাতের ব্যাপারে আমি চিন্তিত। এটা আশা করি তোমরা বুঝবে। তোমরাও কি অস্বস্তিতে পড়বে না এমন কারো সঙ্গে আলাপ করার ব্যাপারে যেখানে সেই লোকটি আদতে যেন আমাদের ভবিষ্যত থেকেই একপ্রকার এসে পড়েছে। তোমাকে বিচার করছে এক আদর্শ জগতের নৈতিকতা দিয়ে। আমি ওর সমালোচনা কোন ভাবেই চাই না।
আমি বক্তব্য শেষ করলাম। জিওর্জি সিদভের ফ্রন্টডেকের কেবিনরুম এখন শান্ত।
—‘হ্যাঁ’, ক্যাপ্টেন অবশেষে মুখ খুলল—‘এরকম কোনো মার্শিয়ানের কথা চিন্তা করা যেতেই পারে। যেকোনো সময়ই ভাবা যায়। কিই বলা যেতে পারে একে, এক সুপিরিয়র নৈতিকতার মাপ, কিংবা নিতান্ত এক মার্শিয়ান অথবা আমাদের কমিউনিস্ট মূল্যবোধ’।
—‘একদমই তাই’। পাইলট বলে উঠল।
নেতায়েভ বলল, ‘আমি পুরো ডায়েরীটাই পড়তে চাই। আমি কথা দিতে পারি তোমাকে। অথচ, আশ্চর্য! আমরা কিনা কথা ভেবেছিলাম যে তুমি যা বলবে তার এক কণাও বিশ্বাস করবো না’।
নেতায়েভ ওর ঝাঁকড়া চুলে হাত বোলাচ্ছিল, কেবিনরুমের ভেতর বেশ আলোড়ন। সবাই হুড়োহুড়ি ফেলে দিয়েছে আমার কাছে মার্শিয়ানের অ্যাপয়েন্টমেন্ট পাওয়ার জন্য। ক্যাপ্টেন জানালেন, যদি সেদিন দক্ষিণের ফেরী না ধরি তাহলে তোমাদের ফ্লাইং ক্লাবে যেতে পারি ওর সঙ্গে দেখা করার জন্য।
আমি বললাম, ‘বেশ এই ব্যাপারটা একটা নভেলে লেখা যেতেই পারে’। এতে অবশ্য কেউ কেউ রেগে গেল, গল্প কেন? আসল কথাই লেখো না হয়।
আমি কেবিনরুম থেকে বেরিয়ে এলাম। জিওর্জি সিডভ আর্কটিক সমুদ্র ভেঙে ছুটে চলেছে। রেলিং ধরে দাঁড়িয়ে রইলাম কিছুক্ষণ। উত্তর আকাশে ধ্রুবতারা জ্বলজ্বল করছে। এই অল্প আলোয় মনে হচ্ছে যেন সেটা আরো কাছে চলে এসেছে।
জাহাজের ফ্রন্টডেকে নেতায়েভ। সে আমার জন্য অপেক্ষা করছে। আকাশে মঙ্গলগ্রহের দিকে তাকিয়ে সে শুধুমাত্র বলতে পেরেছিল, এরকম কাউকে পাওয়া গেলে, পেত্রভিচ, আমি তোমাকে বলতে পারি যে সেটা সত্যিই লজ্জার ব্যাপার হত।
আমি কিছু বলতে পারি নি। আমরা এরপর অনেকক্ষণ চুপ করে ছিলাম। তারপর একসময় আমি ওকে শুভরাত্রি ও বিদায় জানাই।
যদিও আরেকজনের জন্য আমি অপেক্ষা করছিলাম। পাইলট। সে আমার সঙ্গে ব্যক্তিগত ভাবে দেখা করার জন্য অনুরোধ করেছিল, যতই হোক আমি যখন তার গোপনীয়তা একসময় প্রকাশ করেই দেব।
আমি ওর কথা শুনলাম এবং হাত ঝাঁকালাম। প্রথম গ্রহান্তরের মহাকাশযানে ওর মতো প্রাণীরাই নেতৃত্ব দেবে। শুধুমাত্র এটুকুই আমি, আলেকজান্ডার পেত্রভিচ হিসেবে বলে উঠতে পেরেছিলাম। জাহাজের কেবিনরুমের কেউই সেকথা জানতে পারেনি।
শুধু জিওর্জি সিডভ রাতের সিবস্কি আকাশে ধ্রুবতারা আলোয় উত্তর সমুদ্রের পথ খুঁজে গেছে।
অনুবাদ প্রসঙ্গেঃ

আলেকজান্দর পেত্রোভিচ কাজানৎসেভ (Алекса́ндр Петро́вич Каза́нцев) (Alexander Petrovich Kazantsev) জন্ম ২ সেপ্টেম্বর ১৯০৬, মৃত্যু: ১৩ সেপ্টেম্বর ২০০২, টমস্ক পলিটেকনিক ইউনিভার্সিটির স্নাতক, ১৯৩০-এ বেলোরেটস্ক মেটালার্জিকাল প্লান্ট এর চিফ মেকানিক, ১৯৩৯-এ ওয়ার্ল্ড এগজিবিশন-এ সোভিয়েত প্যাভিলিয়নের চিফ ইঞ্জিনিয়ার, ১৯৪১ এ জার্মানী যুদ্ধে কর্নেল এবং বরেণ্য তথা বিতর্কিত কল্পবিজ্ঞান লেখক ও ইউ-এফ-ও-লজিস্ট। ১৯৪৬-এ টুঙ্গুস্কা উল্কাকে মঙ্গলের মহাকাশযান বলে তিনি তুমুল বিতর্কের সূত্রপাত করেন, সেখানে অভিযাত্রী হিসেবেও তিনি যান। ‘বিস্ফোরণ’, ‘গ্রহান্তরের আগন্তুক’ প্রভৃতি গল্পের সিরিজ, ‘জ্বলন্ত দ্বীপ’, ‘উত্তরের জেটি’, ‘উত্তরমেরুর সাঁকো’ ইত্যাদি গ্রন্থ তার গুরুত্বপূর্ণ সৃষ্টি। জিওর্জি সিদভ নামক আইসব্রেকারটিতে ও বেশ কিছু পোলার স্টেশনে তিনি নিজে গেছিলেন। ইয়েফ্রেমভের ‘অ্যান্ড্রোমিডা নীহারিকা’ প্রকাশের পর সোভিয়েত কল্পবিজ্ঞান রচনায় যে পরিবর্তন আসে তার প্রতি বিরূপতায় তিনি নিজেকে আরো গোঁড়া আদর্শবাদী রচনায় সীমাবদ্ধ করে ফেলেন, তবে সোভিয়েত কল্পবিজ্ঞানের গড়ে ওঠার দিনগুলিতে তাঁর রচনাগুলি আজও মাইলফলক হিসেবে গণ্য করা হয়।
বর্তমান গল্পটি তাঁর জিওর্জি সিদভ সিরিজের গল্পমালার অন্তর্ভূক্ত, ১৯৫৮ সালে লেখা। প্রথম ‘গ্রহান্তরের আগন্তুক’ (Гость из Космоса) গ্রন্থভূক্ত হয় ইউ. মাকারোভ এর অলংকরণ সহ। ভায়োলেট এল দত্ত প্রথম এটির ইংরেজি অনুবাদ করেন মস্কোর Foreign Languages Publishing House থেকে প্রকাশিত A Visitor from Outer Space গ্রন্থে। পরে Collier Books এই বইটিকে Soviet Science Fiction নামে ১৯৬২ তে পূণঃপ্রকাশ করে। সিরিজের গল্প বলে পারিপার্শ্বিকে কিছু পূর্বানুবৃত্তির ছায়া রয়েইছে, তবে কাজানৎসেভ-এর আদর্শ, নৈতিকতা ও নান্দনিকতার পরিচয় এতে পাওয়া যায়। বাংলা অনুবাদের সময় কোনো ছাপা ইংরেজি সংস্করণের টেকস্ট পাওয়া যায় নি।
অনুবাদক তিতাস বেরা-র লেখালেখি মূলতঃ বিবিধ ব্লগস্ফিয়ারে। খামখেয়ালী অলস নিঝুম বিকেলবেলার মতো, লেখাপত্রে প্রভূত অস্থায়ী ছাপ। বর্তমানে নানইয়াং টেকনোলজিক্যাল ইউনিভার্সিটিতে রিসার্চ ফেলো হিসেবে কর্মরত। ছবি আঁকেন ও ভালবাসেন শিঙাড়া খেতে।
কৃতজ্ঞতা: আলেকজান্দর কাজানৎসেভ
Tags: আলেকজান্ডার কাজানসেভ, তিতাস বেরা, দেবজ্যোতি ভট্টাচার্য্য, মঙ্গলগ্রহী, রাশিয়ান অনুবাদ গল্প