মাথা
লেখক: ত্রিদিবেন্দ্র নারায়ণ চট্টোপাধ্যায়
শিল্পী: দেবজ্যোতি ভট্টাচার্য্য (চিত্রচোর)
(ঘনাদা-ভক্তদের কাছে করজোড়ে মার্জনা ভিক্ষান্তে)
–“মূর্খ! সব মূর্খ! গ্যাস ধরাতে না শিখে, গেছো বিরিয়ানি রান্না করতে? কলে পড়া ইঁদুর মারতে শিখে, ভাবছ রয়েল বেঙ্গল টাইগারের মোকাবিলা করবে? অ-আ-ক-খ না পড়ে গেছ চর্যাচর্য বিনিশ্চয় করতে? গরুর গাড়ি নিয়ে সুপারসনিক জেটের সঙ্গে রেস লাগাতে চাও?”
হ্যাঁ, ঠিক ধরেছেন! এ সংলাপ ৭২ নম্বর বনমালী নস্কর লেনের দোতলার আড্ডাঘর ছাড়া আর কোন দেশেই বা শোনা যাবে? আর বক্তাও আমাদের একম-অদ্বিতীয়ম ঘনাদা ছাড়া আর কেই বা হবে?
উত্তেজনার আধিক্যে শিশিরের সিগারেটের প্যাকেটটা হাতে নিয়ে বুঝি টঙের ঘরের উদ্দেশ্যেই যাত্রা করছিলেন ঘনাদা। কিন্তু ঠিক সময় বুঝে বনোয়ারির বড় বড় বেশ কখানা প্লেটের সম্ভার নিয়ে ঘরে প্রবেশের ফলেই বোধকরি ঘনাদার সংকল্প বিঘ্নিত হল। আর প্লেটের ঢাকনা সরানোর পর যখন ভুরভুরে সুগন্ধের সাথে আত্মপ্রকাশ করল কলকাতার সেরা রসুইখানার সেরার থেকেও সেরা, প্লেট থেকে মুখে আনতে ভেঙ্গে যাওয়া, তুলতুলে আর ঝুরঝুরে কাকোরি কাবাব; সঙ্গে সঙ্গত করছে মুড়মুড়ে লাচ্ছাদার পরোটা, তখন তো মুনিদেরও মতিভ্রম হত, ঘনাদা কোন ছার।
রুদ্ধশ্বাসে পর পর গোটা চারেক পরোটা সহযোগে গোটা দশেক কাকোরিকে যথাস্থানে পাঠিয়ে শিশিরের প্যাকেটের ২২,৩৬৩ নম্বর সিগারেটটি ধরিয়ে একেবারে ব্রহ্মরন্ধ্র থেকে ধোঁয়া ছেড়ে আরামকেদারায় কাত হলেন ঘনাদা। মেজাজ বুঝে গৌর বলল “কম্পিউটারে আর মানুষের মাথায় কি সত্যিই গরুর গাড়ি আর সুপারসনিক প্লেনের মত অতটাই ফারাক ঘনাদা?” ঘনাদা কড়িকাঠের দিকে তাকিয়ে একটা বিরাট দীর্ঘশ্বাসের সাথে সিগারেটের ধোঁয়া মিশিয়ে ঘরের আধখানা ঝাপসা করে দিয়ে বললেন “তার থেকেও অনেক বেশী। আর তা না হলে কাবুলে তালিবানি ধাঁধায় খেই হারানো প্রখর প্রতিভাবান সেই প্রকোনস্কিকে একটু পথ দেখাতেই সে একবারে আমার ভক্ত হয়ে পড়ে? না স্নায়ুর জট ছাড়ানোর গবেষণায় কোটিপতি দালাল হের বাল্কেনব্রুখের খপ্পরে পড়ে তার নিজের সিদ্ধিলাভের সঙ্গে দুনিয়ার অর্থনীতির সর্বনাশ সমার্থক হয়ে দাঁড়ায়? কী ভাগ্যিস প্রকোনস্কি তার তেলেভাজার নেশায় বাগবাজারের ফেমাস অয়েল ফ্রায়েড শপে এসেছিল, না হলে আজ বিশ্ব-শুদ্ধ সবার ব্যাঙ্কের টাকা সন্ত্রাসবাদী আবু আল জাফলির হাতে গিয়ে পড়ত।”
সবার মাথায় চক্কর লাগার আগেই এই সব মাথায় পাক দেয়া কাণ্ডের কার্য-পরম্পরা গুলির সলতে একটু পাকিয়ে নিই।
হ্যাঁ ঘনাদাকে একটু শিক্ষা দেবার বাসনাটা আমাদের চারজনার মাথাতেই এসেছিল বটে। একটা তুচ্ছ ব্যাপারকে অতখানি বাড়িয়ে তোলার বাড়াবাড়ির একটা দাওয়াই আমাদের মাথায় আসা কিছু অন্যায্য কথা নয়। শিবু একটা ফেসবুকের অ্যাকাউন্ট করে তাতে সারাদিন মজে আছে। আমরা বিরক্ত হচ্ছি, তাতে তার থোড়াই কেয়ার। কিন্তু সেদিন নিচের আড্ডাখানায় বাজারে নতুন ওঠা পালং শাকের কথায় ঘনাদার টিপ্পনী না শুনে হুঁহুঁ করে ওঠাটা তার বেয়াদবির চরম হয়েছিল, একথা আমরা সবাই স্বীকার করেছি। শিবু আমাদের সবার কাছে প্রচুর গালমন্দও খেয়েছিল। তাই বলে দিনের পর দিন আমাদের সমবেত ক্ষমা প্রার্থনা অগ্রাহ্যি করে ঘনাদার মুখ বুজে থাকাটাও অসহ্য।
মতলবটা দেয় শিশির। ওর কে এক মাসতুতো পিসির জামাইয়ের সইয়ের বকুল ফুলের ভাইপো না ভাগ্নে, কম্পিউটার হার্ডওয়্যারে নাকি মহা ধনুর্ধর। দেশ বিদেশের যত কম্পিউটার আর ইলেক্ট্রনিক ডিভাইসের যে আসল প্রসেসর তারই কেউকেটা। বিদেশেই বেশীরভাগ সময় থাকে, অবসর মত দেশে ঘুরে যায়।
খবর পেয়ে আর পায়ের নিচে ঘাস গজাতে দিই নি। অনেক কষ্টে নেমন্তন্ন করে এই বাহাত্তর নম্বরে এনে ফেলা গেছে। কিন্তু ঘনাদাকে ভড়কে দেবার মত গ্রাম্ভারি আলোচনা চালাতে গেলে তো সে ধনুর্ধরের কয়েকটা কথা অন্তত বুঝতে হয়। শেষমেশ ভাষা বোঝার আশায় জলাঞ্জলি দিয়ে খালি কটা বুকনিই শিখে মুখস্থ করলাম। ভালই করেছিলাম কারণ অচিরেই ঘনাদা সান্ধ্য সরোবর ভ্রমণ থেকে ফেরার সময়েই শুনতে পেলেন আমাদের উচ্চাঙ্গ আলোচনা।
-“আঠারো ন্যানোমিটারেরও কম? বল কী হে!” শিশিরের আর্তনাদ একতলার গেট পর্যন্ত পৌঁছে গেছে।
শিবুর গলা আরো চড়ল -“ও তো মান্ধাতার আমলের খবর হে। ন্যানো-ইলেক্ট্রনিক্স কবেই আঠারো ন্যানোমিটারের বাঁধ ভেঙ্গে এখন চোদ্দ ন্যানোমিটারের আশপাশে ঘোরাঘুরি করছে।”
গৌর কম যাবে কেন? দস্তুরমত মুরুব্বির ভাব মুখে ফুটিয়ে বলল “চোদ্দ ন্যানোমিটারও পুরোনো খবর। বিজ্ঞানীরা আকছার সাত এমনকি পাঁচ ন্যানোমিটারের কথাও ভাবছেন!”
ঘনাদাকে ঘরে ঢুকতে দেখে আমিও চালিয়াতের মত ছাড়লুম -“এসব পুরনো টেকনোলজির কথা আলোচনা করে কী যে আনন্দ পাও তোমরা? হ্যাঁ! হত দু এক ন্যানোমিটার……”
আমার কথায় বাধা দিয়ে হতভাগা ভাগ্নে না ভাইপো বলে উঠল “না না সাত, পাঁচ ন্যানোমিটার গেট লেংথের উপরে কিছু এক্সপেরিমেন্ট চললেও দুই এক ন্যানোমিটার গেট লেংথ এখনো স্বপ্ন।”
মেজাজটা যাচ্ছেতাই খিঁচড়ে গেল। ওনারা সব দিব্যি আঠারো থেকে পাঁচে নেমে এলেন, আর আমার বেলাতেই যত আপত্তি! কিন্তু ঘনাদাকে গম্ভীর মুখে আরামকেদারায় আসন নিতে দেখে মনে আশা চাগাড় দিয়ে উঠল। বোমার সলতেয় কি আগুন ধরবে?
গৌর ইতিমধ্যে আমার সম্বন্ধে একটা অপমানজনক মন্তব্য করে ফেলেছে “সুধীরটা চিরদিনের চালবাজ! কিন্তু আসল কথা হল এক স্কোয়ার সেন্টিমিটারে তাহলে কতগুলো গেট ধরছে?”
ভাগ্নে না ভাইপো উত্তর দিল “তা সাত ন্যানোমিটারে নামলে একশো বিলিয়ন তো বটেই।”
-“হুররে! মানুষের মাথার একশো বিলিয়ন নার্ভ ছুঁয়ে ফেলল তাহলে!” শিশিরের উল্লাস দেখি আর বাঁধ মানে না!
-“তা বটে” সেই ভাগ্নে না ভাইপোর সুচিন্তিত অভিমত “এ দশকে না হলেও কুড়ি বা ত্রিশের দশকের শেষে প্রসেসরের ক্ষমতা মানুষের মাথাকে ছাড়িয়ে যাবে বলেই মনে হচ্ছে।”
ঘনাদা এতক্ষণ বজ্রাহত শমিবৃক্ষের মত চাপা আক্রোশে ধোঁয়াচ্ছিলেন যেন। কখন যে সলতেয় আগুন লেগে গেছে খেয়াল করি নি। সম্বিৎ ফিরল ঐ বোমা ফাটা -“মূর্খ! সব মূর্খ! গ্যাস ধরাতে না শিখে, গেছো বিরিয়ানি রান্না করতে? কলে পড়া……………..।” ইত্যাদির সিংহ গর্জনে। তারপর কী হল সে তো প্রথমেই বলেছি।
আমাদের মাথায় কাবুল থেকে শ্যামবাজার ঘুরিয়ে স্নায়ুতে, ব্যাঙ্কে, তেলেভাজায়, সন্ত্রাসবাদে চর্কি পাক লাগিয়ে দিয়ে ঘনাদা শান্তস্বরে শুরু করলেন,
-“ও আঠারো, চোদ্দ, সাত, পাঁচ যাইই বলো, আসল খেলাটা তো অন্য মাঠে হচ্ছে। আধুনিক কম্পিউটারের কলজে যে প্রসেসর, তার এক একটি ইট হল এক একটি সি-মস গেট। যত বড় প্রসেসর তার তত বেশী গেট দরকার। ওদিকে প্রসেসরের চেহারা তো একুনে ওই এক বর্গ সেন্টিমিটার। কাজেই ক্রমশঃ গেটের সাইজ ছোট করা ছাড়া আর উপায় কী? এক ন্যানোমিটার হল এক মিটারের একশো কোটি ভাগের এক ভাগ। কিন্তু গেট ছোট হতে হতে এখন প্রায় পাঁচ ছশো অণুর আকারের কাছাকাছি চলে এসেছে। আর সেখান থেকেই বাঁধল গণ্ডগোল! কী তাই না?” ঘনাদার কটাক্ষ সরাসরি সেই ভাগ্নে না ভাইপোর দিকে।
-“আজ্ঞে, ঠিকই বলেছেন।” ভাগ্নে না ভাইপোর গলার যুদ্ধং দেহী ভাবটা এখন যেন ঠিক মিয়নো মুড়ি। “প্রচলিত সেমি কণ্ডাকাক্টার ইলেকট্রনিকসের নিয়ম আর ছোট সেই সব গেট মানতে চাইছে না। তাদের জন্য কোয়ান্টাম ওয়্যার আর কোয়ান্টাম ডটের থিওরি লাগছে। সেই সব থিওরির উপযুক্ত টেকনোলজি গড়া যায় নি বলেই এখনো কমার্শিয়ালি আমরা কুড়ি ন্যানোমিটারের ধার পাশ ছেড়ে নামতে পারছি না বটে কিন্তু……”
“এক ন্যানোমিটারে নামলেও কি মানুষের মাথা কে ছুঁতে পারবে মনে হয়?” ঘনাদার গলায় স্পষ্ট টিটকারির সুর। “ও যে অন্য নিয়মে খেলে! তোমাদের ওই ডিজিটাল শূন্য একের নিশ্চয়তার জগতের বাইরে অভিজ্ঞতার আলো আঁধারিতে তার চলন। আর ওই অ্যালান টুরিঙ্গের “এক এক বারে এক একটি মাত্র কাজের’ ধরাবাঁধায় মানুষের মাথা আটকে নেই। একই সঙ্গে সবকটা নিউরন আলাদা আলাদা সঙ্কেত পাঠায়। তাও তো মানুষ নিজের মাথার হাজার ভাগের এক ভাগকে কাজে লাগায় মাত্র। তাতেও তোমাদের সব কম্পিউটার অনেক অনেক পিছনে পড়ে আছে। আসলে ঐ হিসেব নিকেশের বাঁধা কাজেই ও কলের যা দৌড়। বুদ্ধির জগতে তোমাদের কল এখনো শিশু। প্রকোনস্কি কে তাই তো বলেছিলাম; কিন্তু থাকগে সেসব কথা।”
-“না না থাকবে কেন?” আমাদের আগে আগ বাড়িয়ে সেই ভাগ্নে না ভাইপোই বলে বসে। -“প্রকোনস্কি লোকটাই বা কে?”
সিগারেটে শেষ সুখ-টানটা দিয়ে ঘনাদা বললেন -“তাহলে তো যেতে হয় ১৯৮০ সালের কাবুলে। সেখানে তখন সদ্য জনগণের সরকার গড়ে উঠেছে। কিন্তু সে বিপ্লবকে পণ্ড করার জন্য, অক্টোপাসের আট নয়, বরং হাজার হাত বাড়িয়ে, ধর্মান্ধ মৌলবাদীদের এগিয়ে দিয়ে, সচেষ্ট হয়েছে পশ্চিমের রাষ্ট্রনায়কেরা। পাছে মধ্যপ্রাচ্যে তাদের দাঁড়াবার আসন টলে যায়। কাবুলের প্রেসিডেন্ট বারবাক কারমাল তাই বাধ্য হয়েছেন সোভিয়েত ফৌজ ডেকে এনে তাই দিয়ে মৌলবাদী তালিবানদের আটকানোর চেষ্টা করতে।
আমি তখন কাবুলে। দৃশ্যতঃ শীতবস্ত্র পুস্তিনের ব্যবসা করে তলে তলে তালিবানদের শয়তানির দৌড় মাপছি। কাবুলে তখন সদ্য শীত পড়তে চলেছে। ওদিকে প্রচুর লোকের শীতের কাপড় নেই। শহরের চক বাজার আর আরও কটা জায়গা থেকে সোভিয়েত ফৌজ পুরোন গরম কোট বিলি করছিল। আমি কাছে এক কাবুলি নান রুটির দোকানের মালিকের সাথে গল্প করছিলাম। এমন সময়ে কে যেন আমার কাঁধে হাত দিল। -“কি কমরেড ডস? এখানেও এসে জুটেছো?” তাকিয়ে দেখি কিংকঙের মাসতুতো ভাই হাসিহাসি মুখে আমার হাত পাকড়ে ফেলেছে। ‘চেরভ কাসভোভিচ’ লালফৌজের খুবই উঁচু র্যাঙ্কের অফিসার। তবে কিনা পশ্চিম দেশের আর্মিগুলোর অফিসারদের দাম্ভিক আচরণের তুলনায় লালফৌজের অফিসারদের অমায়িক ব্যবহারে তাদের র্যাঙ্ক বোঝার কোন উপায় থাকে না।
হাতটা চেরভের দানবীয় থাবা থেকে সরাতে সরাতে বললাম-“তা জুটে গেছি বটে। কিন্তু এই জামাকাপড় বিলনোর আসরে তোমার মত অফিসার কী করছে?”
চেরভের হাঁড়ির মত মুখে হাসি যেন আর ধরে না। বলে -“তোমার খোঁজ-ই করছিলাম। একটু দরকার আছে, এসো না! ভালো ক্যাভিয়ার আছে।”
ক্যাভিয়ারে লোভে ততটা নয়, কিন্তু চেরভের মত উঁচু পোষ্টের মিলিটারি ইন্টেলিজেন্সের অফিসার কাবুলে কী করছে সেটা জানার আগ্রহেই চেরভের সঙ্গ ধরলাম। তবে কি তালিবানদের পিছনে স্যাম চাচাও আছেন? সেক্ষেত্রে হয়ত বিরাট যুদ্ধই লাগতে চলেছে।
সোভিয়েত লালফৌজের নাবেরেজ্নিয়ে ট্রাকে চড়ে অল্পসময় পরেই ওদের যোগাযোগ বিভাগে গিয়ে পৌঁছলাম, আর সেখানেই দেখা পেলাম প্রকোনস্কি আলেক্সিয়েভিচের।”
একটা না একটা অঘটন ঘটাতে না পারলে শিবুর ভাত হজম হয় না। ঠিক গল্প যেখানে মাটি ছেড়ে উঠছে সেখানেই তার বাগড়া দেয়া চাই, এই মুহূর্তেই তার বেয়াড়া জ্ঞানতৃষ্ণা জেগে উঠল। ঘনাদাকে বাধা দেবার মত দুঃসাহস দেখিয়ে হঠাৎ বলে উঠল “আচ্ছা ঘনাদা অনেক দিন ধরেই জিজ্ঞাসা করব ভাবছিলাম। রাশিয়ানদের নাম না টাইটেল? কোনটা ধরে ডাকা হয়?”
গল্পে বাধা পড়া সত্ত্বেও ঘনাদা এতটুকু ব্যাজার হলেন না বললেন “রাশিয়ান নামে কোন পদবির উল্লেখ থাকে না। বিপ্লবের আগে ওদের নাম হত তিন ভাগে। নাম, খৃষ্টান নাম আর বাবার নামের সাথে ভিচ বা ভনা জোড়া। বিপ্লবের পরে ওরা খৃষ্টান নামটা বাদ দিয়ে দুটি শব্দে নাম নামিয়ে এনেছে। যেমন প্রকোনস্কি আলেক্সিয়েভিচ অর্থাৎ আলেক্সির পুত্র প্রকোনস্কি। বুঝলে এবারে?”
-“প্রকোনস্কির চেহারা একেবারেই রাশিয়ানদের মত নয়। আমারই মতন চিমড়ে, সাড়ে পাঁচ ফুট হয় কি না হয়। কাটা কাটা তীক্ষ্ণ মুখ চোখ, নাকের ডগায় চশমা। মাথায় একরাশ সোনালী চুল আর ফ্যাকাসে গায়ের রঙ না থাকলে বাঙালী বলে ভুল হতে পারত। একটা বড় ডেস্কের সামনে একরাশ অগোছালো কাগজ, ফাইল আর একটা কম্পিউটার নিয়ে বসে আছে। চোখে আনমনা গবেষকের দৃষ্টি। চেরভ পরিচয় করিয়ে দিয়ে বলল “কিয়েল ইউনিভার্সিটির রত্ন। ইলেক্ট্রনিক কম্পিউটিং বিভাগের গোল্ড মেডেলিস্ট। এখানে এসেছে দু বছরের বাধ্যতামূলক মিলিটারি সার্ভিসে। আমি ওকে দিয়ে কোড ভাঙার কাজ করাচ্ছি।”
ঠিকই আন্দাজ করেছিলাম। ও পক্ষে প্রচুর বেতার বার্তা চালাচালি হচ্ছে। সবই অবশ্য দুর্বোধ্য কোডে। এসব কোড ভেঙ্গে আদত বার্তার সন্ধান পাওয়া আর ভগবানের সন্ধান পাওয়া একই কথা। তাছাড়া একবার কোড ভাঙতে পারলে অপরপক্ষ না জানতে পারা পর্যন্ত তাদের সব মতলব জানতে পারার মওকা খুবই লোভনীয়।
-“ওকে একটু সাহায্য করো না ডস!”
চেরভের কথা শুনে আমি আর প্রকোনস্কি দুজনেই চমকে উঠেছি। বলি -“রাশিয়ান ভাষায় ভালুক দিয়ে রাই চাষ করানোর যে প্রবাদটা আছে, তোমার কথা শুনে সেটাই মনে পড়ছে।”
চেরভ মুচকি হাসে, বলে -” ওসব বিনয় অন্য কাউকে দেখিও কমরেড ডস। গোটা রাশিয়ার সবকটা কোড ভাঙা যন্ত্রের থেকেও তোমার কাণ্ডজ্ঞানের উপর আমি বেশী ভরসা রাখি।”
কাশির আওয়াজটা আর সামলানো গেল না। ছোঁয়াচে এ কাশি আমাদের চারজনের মধ্যেই ছড়িয়ে পড়ায় প্রমাদ গুনছিলাম, কিন্তু বানচাল নৌকো বাঁচিয়ে দিল সেই ভাগ্নে না ভাইপো ভয়ংকর খিঁচিয়ে উঠে -“একবারে হাসপাতাল বানিয়ে ছাড়লে ঘরটাকে। এত কেশো রুগী এক জায়গায় হল কী করে?”
ঘনাদা নাকের ভিতর থেকে একটা ছোট্ট ঘুঁৎ আওয়াজ করে আবার গল্পে ফিরে গেলেন।
-“প্রকোনস্কির দিকে তাকিয়ে চেরভ বলল -“দুনিয়ার সেরা যন্ত্র দিয়ে গেলাম প্রকোনস্কি। দেখ যেন মান থাকে।” এই বলে চেরভ গাত্রোত্থান করল।
প্রকোনস্কি ফ্যালফ্যাল করে আমার দিকে তাকিয়ে আছে। বেচারির বিড়ম্বনাটা যে বুঝতে পারছি না এমন নয়। বড় কর্তার কথায় আপত্তিই বা করে কিভাবে? কিন্তু বাংলা সাহিত্যের গোল্ড মেডেলিস্টের সামনে যদি একটা ভোজপুরি দারোয়ান কে বসিয়ে দিয়ে বলা হয় ‘এর কাছে গীতাঞ্জলীটা একটু বুঝে নাও’ তো তার অবস্থা তখন প্রকোনস্কির মতই হবে। ওকে একটু সমঝে দেবার জন্যই কড়া গলায় বলি -“সংকেতগুলি কি আলাদা করতে পেরেছ?” এই এক কথাতেই প্রকোনস্কির জড়তা কেটে গেল। বলল -“হ্যাঁ পেরেছি বলেই তো মনে হচ্ছে। কিন্তু তারপরে বেস ভাষাটাই বুঝতে পারছি না। যা পেয়েছি তার চেহারা ওদের পশতু ভাষা বা সীমান্ত পারের উর্দু ভাষার মত তো নয়ই এমন কি ইংরেজির মতনও মনে হচ্ছে না।”
রেডিও সংকেতে যে সব চিহ্ন ভেসে আসে তাদের আলাদা করে চিনতে পারাটাই সবচেয়ে বড় কাজ। চিহ্ন গুলি আলাদা করে চেনার পর, সব চেয়ে বেশী যে চিহ্নটা আসবে সেটা হল শব্দে শব্দে ফারাক করার চিহ্ন যাকে আমরা স্পেস চিহ্ন বলি। এতে শব্দ গুলি আলাদা করে তারপর শুরু হয় কোন চিহ্ন কোন অক্ষরকে বোঝায় সেটা নির্ধারণের কাজ। আমি চিহ্ন লেখা কাগজগুলির দিকে খানিকক্ষণ তাকিয়ে রইলাম। প্রকোনস্কি আমার মুখের দিকে তাকিয়ে আছে।
একটুখানি মুচকি হেসে বললাম “আমাদের বাংলা ভাষায় একটা প্রবাদ আছে, প্রদীপের নীচে অন্ধকার। সব দেশের ভাষার খবর রাখো শুধু রুশ ভাষাটাই চেষ্টা করলে না?”
-“রুশ ভাষায় তালিবান দের কে সঙ্কেত পাঠাবে? আর রুশ ভাষার কথা আপনার মনে হল কেন?”
-“পাঠাবে কারণ ওটার কথা তোমরা, রুশরা সবার শেষে ভাববে বলে। আর রুশ ভাষার কথা মনে হল দুটো একাক্ষর শব্দের বাড়াবাড়ি দেখে। একটা হল রুশ ঈ আর ভ। আর কোন ভাষায় এত বেশী একাক্ষর শব্দ নেই।”
প্রকোনস্কি ততক্ষণে ঝাঁপিয়ে পড়েছে কিবোর্ডের উপর। তাকে আর বিরক্ত না করে, শান্তিতে কাজ করতে দিয়ে চলে এলাম নিজের ডেরায়। কিন্তু শান্তিতে থাকার জো আছে। মাঝরাতে সেই প্রকোনস্কির ডাকেই ঘুম ভেঙ্গে উঠতে হল। দোরগোড়া থেকেই সে আমার হাত দুটো পাকড়ে ধরে একনাগাড়ে বলে যাচ্ছে “ভোলশেভনিক, জাদুকর! কিন্তু কী করে তুমি পারলে? একটা ভাষার প্যাটার্ন বুঝতে সেরার সেরা হেঁয়ালির জট ছাড়ানো ডিক্রিপ্টিক মেশিনেরও মাস খানেকের কম সময় লাগে না, সেখানে মুহূর্তের মধ্যে তুমি রুশ ভাষা কি করে চিনে নিলে? উজিভিতেলনেই! আশ্চর্য!” ওকে একটু শান্ত করে বললাম “হয়ত আমি মেশিন নয় বলেই পেরেছি। মানুষের বুদ্ধি একেবারে অন্য জাতের জিনিস। যদি সত্যই নতুন কিছু করতে চাও তাহলে কম্পিউটারকে মানুষের মত করে ভাবানোর চেষ্টা কর। ওই হ্যাঁ-না জগত থেকে বার করে তাকে অভিজ্ঞতার জগতে নিয়ে যাও।”
ঘনাদা একটু থামলেন। আমাদের মাথা ভর্তি না বোঝা কথা। কিন্তু কোনটা আগে বলব তাই ভাবতে ভাবতেই সেই ভাগ্নে না ভাইপো প্রশ্ন করে বসল “তাহলে প্রকোনস্কি তালিবানদের উদ্দেশ্যে আসা সব কোডগুলো ধরে ফেলেছিল? তারপর আর তার সঙ্গে দেখা হয় নি?”
ঘনাদা গম্ভীর গলায় বললেন “হয়েছিল বৈ কি। কিন্তু সে বড় বেয়াড়া সময়। তখন আমি রোমে। টাইবার নদীর ধারে সান্ধ্যকালীন পায়চারি করছি, এমন সময় একটি মাঝবয়সী সাহেব এসে প্রায় জড়িয়ে ধরল। “চিনতে পারলে কমরেড দাস?” ভাল করে দেখে চিনলাম, এ সেই প্রকোনস্কি। কিন্তু এ কী ছন্নছাড়া চেহারা হয়েছে তার? রোগা চেহারা আরও কঙ্কালসার হয়ে গেছে। মাথায় সোনালি চুল উঠে প্রায় টাক পড়ে গেছে। পরনের ময়লা সুটটা বগলের কাছে ছেঁড়া বলেই মনে হল। খালি চোখের দৃষ্টি আর মুখের হাসি দিয়ে চিনতে পারলাম। বেশী কথা বলার আগেই তাকে নিয়ে একটা মাঝারি দামের কাফেতে নিয়ে বসালাম। বোঝাই যাচ্ছে অনেকদিন পেট ভরে খায়নি। গোগ্রাসে গিলতে গিলতে প্রকোনস্কিও সেই কথাই বলল। ভাজাভাজি খাবার দিকে ওর আকর্ষণ তখনই লক্ষ করি।
নিজের কথা যা বলল তা শুনতে খারাপ লাগলেও ঐরকমটাই হবার কথা ছিল। সোভিয়েত রাশিয়া ভেঙে যাবার পর মাফিয়া আর কালোবাজারিদের পোয়াবারো হলেও সবচেয়ে খারাপ অবস্থা হয়েছে বিজ্ঞানীদের। নতুন রাশিয়ার তখন ছত্রভঙ্গ অবস্থা, ছোটবড় ইউনিভার্সিটিই বন্ধ হয়ে যাচ্ছে তো একগাদা টাকার যোগান দিয়ে সরকারি গবেষণাগারকে কোন গৌরি সেন পুষবে? বাধ্য হয়ে চাকরি হারা বিজ্ঞানীরা দেশে বিদেশে ছড়িয়ে পড়েছেন। নানা জায়গায় নানা অপমানজনক শর্তে এই সব প্রতিভাবান বিজ্ঞানীদের কাজে লাগতে হচ্ছে। এরকম কাজ প্রকোনস্কিও যে পায়নি তা নয় কিন্তু আত্ম-মর্যাদাবোধ একটু বেশী টনটনে হবার দরুন সেভাবে কোথাও টিকতে পারছে না। আধপেটা খেয়ে, ছেঁড়া ফাটা পোশাক পরতে বাধ্য হয়েও সে দমেনি। তার দুঃখ হল সাফল্যের দোরগোড়ায় এসেও তাকে রিসার্চ ছেড়ে দিতে হল। কিসের সাধনা তার, জিজ্ঞাসা করতে প্রকোনস্কির অকপট জবাব -“কেন কমরেড ডস। তুমিই তো আমাকে বলছিলে কম্পিউটারকে মানুষের মত করে ভাবতে শেখাতে, আট বছর ধরে সেই সাধনাই তো করলাম?”
আমি তাজ্জব হয়ে বললাম -“আমার মুখের একটা কথায় তুমি এত-বড় একটা অসম্ভবের সাধনায় ঝাঁপিয়ে পড়লে? তুমি তো বদ্ধ পাগল হে। আবার কী সব হাবিজাবি সিদ্ধিলাভের কথা বলছ!”
আত্মবিশ্বাসে প্রকোনস্কির চোখ জ্বলজ্বল করে ওঠে বলে -“আমি মানুষের মাথার নিউরনের কায়দায় ইলেকট্রনিক গেটদের জট পাকানোর কায়দা বার করেছি। আর এই সব গেট ডিজিটাল হ্যাঁ-না লজিকের বদলে অনিশ্চিত ফাজি লজিকে চলবে।”
-“মানে তুমি স্বপ্নের অতীত নিউরো কম্পিউটেশান কে বাস্তবে এনেছ?” আমার বিস্ময় বাধা মানে না।
-“থিওরিটিক্যাল ডস, সব থিওরিটিক্যাল। নীল নকশা সবই তৈরি, কিন্তু হাতে কলমে কাজ শুরু করতে গেলে, ওই সব মাইক্রোচিপ ডিজাইন করার মত ল্যাবরেটরি কে আমায় এখন দেবে? আর চিপ বানানোর ফাউন্ড্রিই বা কোথায় পাবো!” প্রকোনস্কি দীর্ঘশ্বাস ফেলে “আর দুটো বছর যদি সময় পেতাম! এই ডামাডোলটা যদি কেবল দুটো বছর পরে হত ডস! যাক এ সব ভেবে আর হবে কী? সবই আমার পোড়া কপালের দোষ।”
মনটা খারাপ হয়ে গেল। দুনিয়ায় ঠিক এইই হয়। প্রকৃত প্রতিভাবানের ভাত জোটে না, ওদিকে যত অপদার্থের সু-নামে পৃথিবী গমগম করে! কিন্তু আমি কী করতে পারি? পরদিন দেখা করার প্রতিশ্রুতি দিয়ে নিজের হোটেলে ফিরে এলাম।
পরদিন কিন্তু টাইবারের ধারে প্রকোনস্কির দেখা পেলাম না। ভাবলাম খেয়ালী লোক, নিজের খেয়ালে কোথায় গেছে কে জানে! কিন্তু দিন দশেক পরে হঠাৎ এক অভিজাত রেস্তোরাঁয় প্রকোনস্কির দেখা পেলাম। সঙ্গে এক, লম্বায় যা হোক চওড়ায় চারগুণ দানব। প্রকোনস্কি আলাপ করিয়ে দিল। ইনি জার্মান কোটিপতি হের বাল্কেনব্রুখ। এঁর নিজস্ব মাইক্রোচিপ তৈরির ল্যাব আর ফাউন্ড্রি দুইই আছে। প্রকোনস্কি কে নাকি ইনি যথেষ্ট সরেস মাইনেয় নিজের ল্যাবে একেবারে ফ্রি হ্যান্ড দিয়ে কাজ করার অফার দিয়েছেন।
প্রকোনস্কির বর্তমান অবস্থায় এ হেন চাকরির মওকা প্রত্যাখ্যান করা নেহাতই আহাম্মকি হবে, কিন্তু এই জার্মান কোটিপতিটিকে আমার একেবারেই সুবিধার লাগলো না। এত অতিরিক্ত বিনয় আর তেলতেলে হাসি কেবল পাকা শয়তানদেরই হয়, এ আমার অনেকদিনের অভিজ্ঞতা। দিন দুয়েকের মধ্যেই মিউনিখে গিয়ে চাকরিতে যোগ দেবে এই কড়ারে প্রকোনস্কিকে একটা অসম্ভব বেশী পরিমাণ টাকার দাদন ধরিয়ে হের বাল্কেনব্রুখ প্রস্থান করলেন।
প্রকোনস্কির সনির্বন্ধ নিমন্ত্রণে রোমের সবচেয়ে অভিজাত হোটেলগুলোর একটায় ডিনার খেতে খেতে আমি এই জার্মানটার মতিগতি সম্বন্ধে সাবধান করলাম। প্রকোনস্কি তখন আবার গবেষণা শুরু করতে পারার আনন্দে স্বপ্নের জগতে চলে গেছে। মনের আনন্দে ইটালিয়ান ভাজা রুটি ফ্রিতেল্লে খাবার ফাঁকে বললাম যদি কখনো কোন বিপদে পড় তো লন্ডন টাইমসে বক্স নম্বর দিয়ে একটা বিজ্ঞাপন দিও। আর ছোটখাটো খবর দিতে হলে দিল্লির রাশিয়ান এমব্যাসির ঠিকানায় চিঠি লিখো।
এ আজ থেকে বছর পঁচিশ আগের কথা। এর মধ্যে বছর পনেরো আগে লেখা একটাই চিঠিতে তার খবর পেয়েছি। বলা বাহুল্য প্রকোনস্কির কথা শুনে উদ্বেগ আমার অনেকগুণ বেড়ে গেছে। যে নিউরো কম্পিউটার তৈরি তার স্বপ্ন ছিল তা বছর কয়েকের মধ্যেই সে তৈরি করে ফেলেছে, কিন্তু সেই কম্পিউটারের ব্যবহারের যে ক্ষেত্র প্রকোনস্কি বেছে নিয়েছে তা যেমন চ্যালেঞ্জিং তেমনই সর্বনাশা। ব্যাঙ্কের টাকাপয়সা লেনদেনের যে আন্তর্জাতিক যোগাযোগ ব্যবস্থা, তারই রক্ষাব্যবস্থার মর্মমূলে আঘাত হানতে চলেছে প্রকোনস্কির এই নিউরো কম্পিউটার। সমাজতান্ত্রিক ভাবধারায় বেড়ে ওঠা এই সহজ সরল মানুষটির মনে পুঁজিবাদের প্রতি যে ঘৃণা জমে আছে, যে পুঁজিবাদকে সে নিজের ও মানবজাতির সর্বনাশের কারণ বলে জানে, তাকে এইভাবে ব্যাংকিং ব্যবস্থার বিরুদ্ধে লড়িয়ে দিতে শয়তান বাল্কেনব্রুখের কোনই অসুবিধা হয় নি। চিঠির ছত্রে ছত্রে সেই যুদ্ধের আভাস। খালি এই কম্পিউটার অভিজ্ঞতার মাধ্যমে শেখে বলে বিভিন্ন কোড এবং সেই সব কোড ভাঙ্গা শিখতে নিউরো-কম্পিউটারের সময় লাগছে। শিক্ষা শেষ হলে এই ভয়ানক দানবের বিরুদ্ধে লড়তে গিয়ে পৃথিবীর অর্থব্যবস্থাই খোঁড়া হয়ে মানুষের অশেষ কষ্টের কারণ হবে, কিন্তু সে কথা আমি প্রকোনস্কিকে কীভাবে জানাব? তার তো ঠিকানাও জানি না।
দুশ্চিন্তায় দিন কেটে যাচ্ছিল। এমন সময় লন্ডন টাইমসে বিজ্ঞাপন দেখলাম “আমি কলকাতায় আসছি ডস, জরুরি দরকার”। কলকাতার মত “ছোট্ট গ্রামে” তাকে খুঁজে পাওয়ার হদিস দেবারও দরকার মনে করেনি প্রকোনস্কি, এতটাই ছেলেমানুষ! যা হোক খুঁজে তাকে ঠিকই বের করলাম বাগবাজারের ফেমাস অয়েল ফ্রায়েড শপের সামনে থেকে। কিন্তু যা সে বলল তাতে দুশ্চিন্তা আমার বাড়ল বই কমলো না।
বাল্কেনব্রুখ নিজে যদিও কোটিপতি কিন্তু তার আসল ব্যবসা অন্তর্জাতিক সন্ত্রাসবাদীদের দালালি করা। প্রকোনস্কির নিউরো-কম্পিউটার দিয়ে তারা আসলে চায় ব্যাঙ্কে বিভিন্ন অ্যাকাউন্ট হ্যাক করে টাকা চুরি করে নিজেদের সংগঠনের তহবিল ভারি করতে। এটা বুঝতে সহজ সরল প্রকোনস্কির সময় লেগেছে ঠিকই, কিন্তু বুঝতে পারার পর আর একটুও দেরি না করে আমার নামে বিজ্ঞাপনটি ছেড়ে ঢাকায় সেমিনারে যোগ দেবার অছিলায় বাংলাদেশে এসে বেআইনি ভাবে বর্ডার পেরিয়ে কলকাতায় ঢুকে পড়েছে সে। শুধু এটা বুঝতে পারে নি কলকাতার মত মানুষের জঙ্গলে দাস নামের এক অজ্ঞাত ব্যক্তিকে সে কিভাবে খুঁজে পাবে। কিন্তু দাসের উপর তার অগাধ ভরসা। -“এই তো তুমি আমায় খুঁজে পেয়েও গেছো। কিন্তু কি করে পেলে বলতো?”
-“যেভাবে আমরাও তোর খবর পেলাম রে সাদা আরশোলা। তোর ভাজা খাবার নোলা দেখে। তেলেভাজার টোপ দিয়ে কেমন আরশোলা ধরলাম বল!” যমের মতন তিনটে ভাড়াটে গুণ্ডার সঙ্গে বাল্কেনব্রুখকেও দেখলাম। মোটা হতে হতে সে হাতিকেও ছাড়িয়েছে এখন। “সঙ্গে তোর ওই কেলে নেংটিটাকেও এই গঙ্গার জলেই বিসর্জন দিয়ে যাব ভাবছি। বাঁচতে চাইলে সব ডেটা ভরা মাইক্রো চিপটা শুধু কোথায় রেখেছিস বলবি।”
প্রকোনস্কির মুখ ভরা হাসি -“মাইক্রোচিপটা পেলেই বা তোমার কি লাভ হবে হের বাল্কেনব্রুখ? শেষ একমাস ধরে আমার নিউরো-কম্পিউটারকে তো আমি উল্টো শিক্ষা দিয়ে এসেছি। ঠিক-ভুল দুই শিক্ষা মিলে তার মাথায় এখন এমন জট পাকিয়েছে যা খোলা শিবেরও অসাধ্য। আমার চিপটায় তো শুধু নিউরো-কম্পিউটার বানানোর কায়দা ভরা আছে। কিন্তু নিউরো কম্পিউটারের আসল কথা তো হল শিক্ষা। শিক্ষা ছাড়া এ কল সদ্যোজাত শিশুর মত অসহায়!”
বাল্কেনব্রুখ জার্মান ভাষায় চিৎকার করে ওঠে “ডু বিশ টট্।” মানে ইউ আর ডেড। কিন্তু প্রকোনস্কির মুখে তখনো হাসি। বলে ওঠে -“আমি বাঁচলাম কি মরলাম সেটা বড় কথা নয়। তোমার শয়তানি মতলবের হাত থেকে দুনিয়া বাঁচল এটাই বড় কথা”।
নিশ্চিত মৃত্যুর মুখে দাঁড়িয়ে এতটা হিম্মৎ দেখানো যার তার কম্ম নয়। কিন্তু বাল্কেনব্রুখের গলায় বিষ ঝরে পড়ছে। -“আরশোলার যা নিয়তি সেই টিকটিকির বদলে ড্রাগনের খাদ্য হতে যাচ্ছিস এই আনন্দ নিয়েই তুই মর। তোর মত দশ ইউরোর বিজ্ঞানী আমি অনেক পাবো।” আর বিশেষ কথা না বলেই ওরা চারটে দানব আমাদের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ল।
প্যান্টের ধারে লেগে থাকা সুক্ষ্ম কাদার দাগ পরিষ্কার করতে করতে দেখলাম তিনটে ভাড়াটে গুণ্ডার একটা ভাঙা হাতের যন্ত্রণায় ছটফট করছে। বাকি দুটো বধ হওয়া ঘটোৎকচের মত অজ্ঞান হয়ে পড়ে আছে।
বাল্কেনব্রুখের জামার ভাঁজ ঠিক-ঠাক করে দিতে দিতেই ওকে ময়লার ভ্যাটের মধ্যে থেকে তুলে আনলাম। বললাম “তোমার বাইরেটা যথেষ্ট ময়লা হলেও ভিতরটার তুলনায় এখনো সদ্য ঝরা শিউলি ফুল। কষ্ট করে একটু অপেক্ষা কর। যতক্ষণ না তোমাকে ইন্টারপোলের জিম্মা করে দিই ততক্ষণ মেহেরবানি করে একটু দুর্গন্ধ বরদাস্ত করো!”
বাল্কেনব্রুখ চোখ কপালে তুলে বলল “একটা গুণ্ডার হাতে মার খাওয়া ছাড়া আমার অপরাধটা কি? ইন্টারপোল কি এতই সস্তা নাকি?”
বললাম -“কাল বিকেল থেকে সন্ত্রাসবাদীদের সাহায্য করার অপরাধে তোমার নামে রেড কর্নার জারি হয়ে গেছে। সে ব্যবস্থা না করেই কি এখানে এসেছি?” আশ্চর্য কাণ্ড হল এতটা মার খেয়েও যে দিব্যি কথা বলছিল সেই বাল্কেনব্রুখ হঠাৎই মূর্ছা গেল।”
ঘনাদা যেন ভুল করে শিশিরের সিগারেটের প্যাকেটটা নিয়ে টঙের ঘরের দিকে রওনা দিলেন।
আমরা সেই ভাগ্নে না ভাইপো কে ছেঁকে ধরলাম -“ছি, ছি!! আপনার সামনে ঘনাদা এতগুলো গুল মেরে বেরিয়ে গেলেন আর আপনি হাবার মত চুপ করে বসে রইলেন?”
-“না না আপনারা বুঝবেন না। উনি যা যা বলে গেলেন অক্ষরে অক্ষরে সত্যি। আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্সে রাশিয়ানরা আশির দশকেই বহুদূর এগিয়েছিল। তখন তো আর বাইরের দেশের বিজ্ঞানীরা সেসব জানতে পারত না, এখন একটু একটু করে জানা যাচ্ছে। কী করে যে তাদের এত অগ্রগতি হয়েছিল সে তো এখন বুঝলাম! উফফ আমার গায়ে কাঁটা দিচ্ছে!”
গায়ে কাঁটাওয়ালা সজারু হয়েই ভাইপো না ভাগ্নে বিদায় নিলো।
Tags: ঘনাদা, ত্রিদিবেন্দ্র নারায়ণ চট্টোপাধ্যায়, দেবজ্যোতি ভট্টাচার্য্য, দ্বিতীয় বর্ষ চতুর্থ সংখ্যা, মাথা
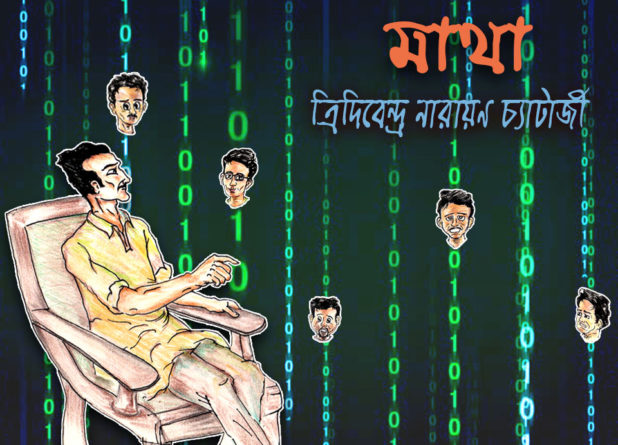

দুর্দান্ত! সেই পুরোনো আমেজ, সেই একশন, সেই তথ্যনিষ্ঠ অথচ রসসিক্ত ব্যাপারটা দারুণভাবে ফিরে পেলাম এই কাহিনিতে। অভিনন্দন।
গায়ে কাঁটা দিয়ে উঠল। সেই একই ম্যাজিক যা অর্দ্ধ-শতাব্দী পেরিয়ে এখনও অটুট আর অমলিন। ভূগোল – অ্যাডভেঞ্চারের আলোতে ঝলসে উঠেছে কৈশোরের সেই অমলিন স্বাদ। প্রেমেন বাবুর ঘোস্ট রাইটিং বলে বিভ্রম হয়েছে মাঝে মাঝেই, এতটা অথেন্টিক !!
অসামান্য! প্রেমেন মিত্তির যদি আজ ঘনাদা লিখতেন তাহলে কেমন হত সেটা জানা হয়ে গেল। ভবিষ্যতে আরও ঘনাদার কাহিনী চাই আপনার কলমে।
স্বচ্ছন্দে অপ্রকাশিত ঘনাদা-কাহিনী বলে চালিয়ে দেওয়া যায়। তবে প্রেমেনবাবুর ব্যবহৃত মুড়কিগুলো খুব বেশী লাগিয়েছেন। তাতে মূল লেখকের রচনা শৈলী এসেছে বটে, কিন্তু যাদের ঘনাদার গল্প বহুপঠিত, তারা কিছু নতুনত্বের দাবী করতেই পারে। চালিয়ে যান।
সাধু সাধু, বেশ লাগলো। 😀আদি অকৃত্রিম ডস কে খুঁজে পাওয়া গেল আপনার লেখায়।
প্রণাম নেবেন।
আর কিছুই বলার নেই!
অনেকদিন পর আমার সবচেয়ে প্রিয় ঘনাদাকে নতুন করে পেলাম। আরও এ রকম গল্প চাই – ‘নতুন ঘনাদা’ বেরোক।
ক্লাসিক একদম।
তবে ধরে আনা ক্যারেক্টারগুলো আরেকটু ঝামেলা পাকানোর চেষ্টা করে 🙂
একদম ঠিক বলেছেন। কিন্তু আমার দৌড় এই পর্যন্তই। অলরেডি যথেষ্ট দু:সাহস করে ফেলেছি। মুল গল্পের বাইরে আর খেলতে সাহস হল না। আপনাদের প্রশ্রয় লাভে অভিভূত।
বাঃ ভালো লাগল অনেকদিন বাদে, একদম ঘনাদার ফ্লেবার! এইরকম আরো অনেক চাই কিন্তু! এক্কেবারে প্রেমেন্দ্র মিত্র না হলেই বা কি … ধনবাদ এই গল্পের জন্য!
দারুন হয়েছে। শুধু মাঝখানে আরেক রাউন্ড কুলফি বা রসমালাই নিয়ে বনওয়ারীর প্রবেশ থাকলে জমে ক্ষীর হয়ে যেত।
অরিজিনাল ঘনাদায় কি কখনো সেকেন্ডবার বনোয়ারীর প্রবেশ ছিল?
পড়তে পড়তে লিঙ্ক চলে গিয়েছিল। আর খুঁজে পাচ্ছিলাম না। তারপর কাজের চাপে খেয়াল ছিল না। হঠাৎই গল্পটার কথা মনে পড়ায়, একদম অন্যমনস্কভাবে ঘনাদা সমগ্র ঘাঁটতে শুরু করেছিলাম। কিছুতেই পাই না। তারপর মনে পড়ল এটা তোর লেখা। শেষ অবধি পড়ে ফেললাম। আশা করি গল্পের গুণমান নিয়ে আর কিছু বলার নেই।
নাঃ! একবার শুরু করলে শেষ না করা অব্দি স্বস্তি নেই – বলায় অবিকল কিন্তু বিষয়ে অতুলনীয়! তুলনা নয়, প্রবীরেন্দ্র চ্যাটার্জি’র লেখা শরদিন্দু-ফ্যান ফিকশন ‘গরল তমসা’র কথা মনে পড়ে গেলো|
আপনি মশাই গুরুদেব মানুষ| প্রনাম নেবেন|
Bhalo laglo.aro likhun.
শুধু চমৎকার বললে কম বলা হয়ে যাবে. বহুদিন পর যেন সেই পুরানো ঘনাদার স্বাদ পেলাম. অনেক অনেক ভালোবাসা রইল লেখকের প্রতি
দারুন লাগলো। তবে ঘনাদার মান ভাঙানোর গল্পটা আরেকটু বাড়াতে পারলে হতো। এরকম আরো চাই।
asadharan! satyi aprakashito Ghana da mone hochchhe!durdanto! aro porar apekshay thaklam……….
eto bhalo fan fiction kakhano porini,osamayno hoeche.
prosenjit
Dada. Ei opurbo goppo porte giye kakori kabab er naam soonlam.
E bostuti kothay pabo sir?
দারুন… সেই পুরনো আমেজ যেন আবার ফিরে পেলাম… আরো লিখুন দাদা…
Very Nice