সভ্যতার সূচনা – রোমেন ইয়ারোভ
লেখক: রোমেন ইয়ারোভ, বাংলা অনুবাদ – পিউ ফাদিকার
শিল্পী: দেবজ্যোতি ভট্টাচার্য্য (চিত্রচোর)
দীর্ঘ প্রতীক্ষার অবসান। অবশেষে টাইম মেশিনের দৌড় অন্যান্য প্রযুক্তিগত প্রতিযোগিতার অন্তর্ভুক্ত করা হল। অনুরাগীদের দীর্ঘ নিরলস প্রয়াসে এই সাফল্য। স্বাভাবিকভাবেই তারা ভীষণ গর্বিত। তাদের গর্ব করার যথেষ্ট কারনও আছে। এমনিতেই বহুদিন আগে, প্রথম পরীক্ষামূলকভাবে টাইম মেশিনের মডেল তৈরির বিজ্ঞপ্তি বেরোনোর সঙ্গে সঙ্গে ‘নবীনদের বিজ্ঞান চেতনা’, ‘বিজ্ঞানই শক্তি’, ‘প্রযুক্তি ও জীবন’ প্রভৃতি বিখ্যাত বিজ্ঞান পত্রিকাগুলির দপ্তরে পাঠকদের পাঠানো চিঠির সংখ্যা চারগুণ বেড়ে গেছিল। প্রথমে চুপচাপ থাকলেও পরে সবকটি পত্রিকা তাদের সাপ্লিমেন্টারি পাতায় একসাথে রঙিন নকশা সহ ভ্রমণমূলক, অবসরকালীন ও প্রতিযোগিতামূলক – তিন ধরণের টাইম মেশিনেরই বর্ণনা প্রকাশ করে। শিগগিরিই অতীতচারীদের জন্য তৈরি করা হয় একটি ক্রীড়াসংস্থা। তার সাম্মানিক সভাপতির পদে বেছে নেওয়া হয় একশ সাতচল্লিশ বছর বয়স্ক এক বৃদ্ধকে। সংস্থার পক্ষ থেকে বেশ কিছু ছোটোখাটো দীর্ঘ দূরত্বের প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হয়, যদিও কোনো প্রতিযোগীইই ষোড়শ শতাব্দীর থেকে বেশি পিছনে যেতে পারেনি।
অবশ্য তখনই আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন দৌড়বীররা প্রথম শতাব্দী অবধি পাড়ি দিচ্ছিলেন। সুইডেন থেকে আসা একটি অপ্রত্যাশিত খবর সমগ্র ক্রীড়াজগতে আলোড়ন তুলে দিল। উনিশ বছরের এক খেলোয়াড় জর্জেন জর্জেনসন মাত্র তিনঘন্টা আঠারো মিনিট আটচল্লিশ পূর্ণ তিনের দশ সেকেন্ডে চব্বিশ শতক সময় অতিক্রম করেছে। তারপরই ক্রিড়া সংবাদপত্রে বড় বড় হরফে একটি প্রতিবেদন প্রকাশিত হয়, যার শিরোনাম ছিল ‘আসুন, আমাদের অতীতের হৃতগৌরব ফিরিয়ে আনি।’ সেই প্রতিবেদনে সেই সমস্ত কলকারখানার সমালোচনা করা হয়েছিল যারা খেলোয়াড়দের প্রয়োজনের কথা ভুলে শুধুমাত্র বিজ্ঞানের প্রয়োজনে টাইম মেশিন তৈরি করছিল। এই সমালোচনার প্রভাব হল সুদুরপ্রসারী। বেশ কয়েকটি প্রযুক্তিগত ক্রিড়া-উপযোগী টাইম মেশিনের মডেল তৈরি করা হল ও সেগুলি সফলভাবে পরীক্ষাও করা হল। তারপরই টাইম মেশিনের সময়-দৌড়, প্রযুক্তিগত প্রতিযোগিতা ‘স্পার্টাকাস গেমস’-এ স্থান পায়।
দর্শকেরা ভূগর্ভস্থ পথ দিয়ে ধীরে ধীরে ক্রীড়াঙ্গণের দিকে এগোচ্ছিল। গোল পাকানো ক্রীড়াসূচি যারা বিলি করছিল তাদের হাতে ওগুলো পতঙ্গের ডানার মতো ফড়্ফড়্ করছিল।
– “খেলার অন্তিম পর্যায়! দূরত্ব প্রতিযোগিতা! প্রধান প্রতিযোগীরা হলেন, ভাসিলি ফেডোসেইভ, কনস্তান্তিন প্যারামোনভ!”
আকাশে সূর্য ঝলমল করছে। সঙ্গীতের সুর গমগম করছে। অসংখ্য মানুষের পদচারণা, শিশুরা ছটফট করছে। সকলে প্রাণচঞ্চল এবং নিজেদের মধ্যে তর্কবিতর্ক জুড়ে দিয়েছে।
– “প্যারামোনভের মধ্যে সহিষ্ণুতা আছে, দায়িত্ববোধ আছে। বলি, ফেডোসেইভের আছেটা কি শুনি?”
– “কিন্তু সুখুমির অনুশীলনে …”
– “থামো তো! প্যারামোনভ আর প্যারামোনভ! কই, কোথায় ছিল তোমার প্যারামোনভ যখন ফেডোসেইভ …”
– “থাক, আর তোমার ফেডোসেইভের গুণকীর্তন শোনাতে এসো না!”
অনুরাগীদের তথ্যানুসন্ধান সত্যিই অবাক করার মতো। তাদের ভবিষ্যৎবাণী, পরীক্ষা, পর্যবেক্ষণ, তাদের নির্ভুল অকাট্য যুক্তি, সমস্যাকে সুবিন্যস্ত করে নানাভাবে বিচার বিবেচনা করে দেখা – এ যেন স্বয়ং একটি বিজ্ঞান, ভূগর্ভস্থ পথের মধ্যে দিয়ে ক্রীড়াঙ্গণ অবধি যেতে যেতেই যার বিকাশ। ক্রীড়াঙ্গণের মাঝখানে রাখা পোস্টারে নীল রঙ-এ গৌরবের শিখরস্পর্শী দৌড়বীরদের ছবি। তাদের সর্পিল ভাবে ঘিরে রয়েছে এথেন্স, স্পার্টা, রোম, কার্থেজ, বাইজান্টিয়াম, চিঙ্গিজ খান ও নেপোলিয়ান। শিল্পীর দৃষ্টিভঙ্গীতে এই সর্পিল পথ সমগ্র মানব ইতিহাসের দ্যোতক। দৌড়বীররা অবশ্য অতীতে গিয়েও ইতিহাসের সেই সমস্ত ঘটনার সাক্ষী হতে পারবেনা। প্রতিযোগিতার নিয়ম অনুসারে তারা কোনো দূর সময়-স্থানে থামতে পারবে না।
প্রতিযোগীরা ট্র্যাকের উপর দৌড় শুরু করার সংকেতের জন্য অপেক্ষা করছে। তারা সকলে এক সরলরেখায় দাঁড়িয়ে নেই বরং সকলে নিজেদের প্রয়োজন মতো স্থান বেছে নিয়েছে। সকলকেই শুরু করতে হবে একই সময়ে, কিন্তু কোন স্থান থেকে তারা যাত্রা শুরু করছে তা গুরুত্বপূর্ণ নয়। ফেডোসেইভের প্রশিক্ষক টাইমমেশিনগুলোর পরীক্ষামূলক উড়ানের একজন প্রবীণ এবং অভিজ্ঞ চালক। হাত দিয়ে মেশিনের চেসিসের একটা বোল্ট দেখতে দেখতে তিনি তার ছাত্রের কানে কানে শেষ মুহূর্তের উপদেশ দিচ্ছিলেন – “সবচেয়ে জরুরি ব্যপার হল গতিতে আসা। আমি জানি তুমি পারবে। তুমি যোগ্য, কিন্তু প্রথমদিকে তাড়াহুড়ো না করে নিজের ছন্দে আসা অবধি অপেক্ষা কর। সর্বোচ্চ বেগে পৌঁছনোর পর সমস্ত শক্তি দিয়ে সেই একই গতিবেগ শেষ পর্যন্ত ধরে রাখ। মনে রেখো, প্যারামোনভ এই সর্বোচ্চ গতিবেগ লাভ করার দিকে একটু দূর্বল। প্লাজমা আকর্ষণের বিষয়টিও মনে রেখো।”
নিজের ছককাটা কোটটি ক্লাবের ছোকরা সদস্যদের হাতে ছুঁড়ে দিয়ে, খেলোয়াড়ের পোশাকে প্রশিক্ষক তাঁর বলিষ্ট বাহু রাখলেন ফেডোসেইভের কাঁধে।
ট্র্যাকের দিক থেকে ছুটে এল চশমা পরা এক তরুণ। ছেলেটি স্নাতকস্তরের ছাত্র, ইতিহাসবিদ ও সময়-দৌড়ের পথ বিশেষজ্ঞ। বিশ্ববিদ্যালয়ের গণ্ডী পেরিয়ে সে খেলাধুলো নিয়ে পড়াশোনা করছে। সে সমস্ত প্রতিযোগীদের সাথে করমর্দন করলো এবং তাদের জড়িয়ে ধরে বলল – “এগিয়ে যাও। কোন অবস্থাতেই থেমে যেওনা।” সে আরও বলল, “অতীতে প্রবেশ করে অহেতুক সময় নষ্ট কোরোনা।”
খেলা যারা পরিচালনা করবে তারা ইতিমধ্যেই সময়-পথে বেরিয়ে পড়েছে।
একটা চলন্ত টাইম মেশিনকে সুনির্দিষ্ট সময়ের গণ্ডীর মধ্যে থামানো খুব কষ্টসাধ্য কাজ। অন্তত পাঁচ দশ সেকেণ্ড এদিক-ওদিক হয়ই। তাই তাদের অবয়ব মেঘের মধ্যে দাঁড়িয়ে থাকা প্রেতাত্মার মতো দেখায়। সমগ্র মানবসভ্যতার ইতিহাসের সময়পথ জুড়ে যেন তারা ভাসমান। মানুষ তাদের সর্বত্র দেখতে পায়, ফলে অশুভ লক্ষণ বা প্রাকৃতিক ঘটনা বলেই মনে করে। কিন্তু আধুনিক দার্শনিকরা তাদের কুসংস্কার নিয়ে হাসি-ঠাট্টা করেন। তাঁদের মতে এসব মহাকাশের আলোর খেলা ছাড়া আর কিছুই নয়। দু-শতাব্দী পিছনে গেলে দেখা যায় তারা ডাইনি আর ধর্মের বিরুদ্ধাচারণকারীদের শায়েস্তা করছে। আরো কিছুটা পিছিয়ে গেলে দেখা যায় যাযাবরদের দলপতি তাদের দিকে তাকিয়ে উল্লাস প্রকাশ করছে কারণ ঘোড়ার পিঠে চড়ে সফল ডাকাতি আর লুঠতরাজের মাল এসে পৌঁছেছে। সময়পথের প্রায় শেষে, যার আগে টাইম মেশিনগুলোর প্রযুক্তিগত বৈশিষ্ট্য আর কাউকে যেতে দেয় না, সেখানে তাদের দেখায় যেন – ধর্মগুরু, কঙ্কালসার হাত আকাশের দিকে তুলে দাঁড়ানো, দাড়ি বাতাসে থরথর করে কাঁপছে, যেন সারা বিশ্বের সমস্ত অন্যায়ের স্বরূপ তারা উদ্ঘাটন করছে।
দর্শকের কাছে টাইম মেশিনের এই গতি প্রতিযোগিতা অদৃশ্যই থাকে। প্রতিযোগিতার শুরুর সংকেত পাওয়া মাত্র প্রতিযোগীরা অদৃশ্য হয়ে যায়। ম্যারাথনের মতোই সকলের অলক্ষে বহু দূরে সেই গতির যুদ্ধে প্রতিযোগীরা একে অপরকে অতিক্রম করতে থাকে। মাঠে অন্যান্য প্রতিযোগিতা চলতে থাকে এবং প্রশিক্ষকরা ছাড়া প্রায় সবাই দৃষ্টির বাইরে বহুদূর কোনো শতাব্দীর মধ্যে দিয়ে চলতে থাকা দৌড়বীরদের কথা ভাবা বন্ধ করে দেয়।
যেখান থেকে অদৃশ্য হয়েছিল, সহসা ঠিক সেই জায়গায় সে উদয় হল। যে কম্পনের জন্য তাকে দেখতে অসুবিধে হচ্ছিল তা থেমে গেলে প্রতিযোগীটির অবয়ব ক্রমশ স্পষ্ট হতে থাকল। অবশেষে বোঝা গেল, সে কনস্তান্তিন প্যারানোমভ।
তার প্রশিক্ষক প্যারানোমভের দিকে ছুটে গিয়ে আনন্দে তাকে জড়িয়ে ধরলেন, হেলমেট ও পোশাক খুলতে সাহায্য করলেন, তারপর দুজনে টাইম মেশিনটি একধারে সরিয়ে নিয়ে অন্যদের জন্যে অপেক্ষা করতে লাগলেন। বিজয়ীর নাম ভেসে উঠল আলোকিত অক্ষরে। ঘোষক সংযত উচ্ছ্বাসের সাথে ঘোষণা করলেন, “সত্যি যথাযথ ফলাফল।” আশেপাশে গুঞ্জন শুরু হয়ে গেল। ফেডোসেইভের সমর্থকদের ভ্রুকুঞ্চিত হয়ে উঠল।
অন্যান্য প্রতিযোগীরা একে একে ফিরে এলো। এমনকি সবচেয়ে দূর্বল প্রতিযোগীরাও এসে উপস্থিত হল, কিন্তু ফেডোসেইভকে দেখা গেল না।
দর্শকাসনে অস্থিরতা দেখা যাচ্ছে, শোরগোল শুরু হয়েছে। বিচারকমণ্ডলী সময়পথব্যাপী প্রতিযোগিতা পরিচালকদের সাথে যোগাযোগ করছেন। কিচ্ছু বোঝা যাচ্ছিল না। ফেডোসেইভের প্রশিক্ষক ততক্ষণে আবার তাঁর কোট পরে নিয়েছেন। তিনি দাবী করলেন, নথিতে প্রতিযোগিতার এই চূড়ান্ত অব্যবস্থার উল্লেখ রাখতে হবে। ইতিহাসবিদ উদ্বিগ্ন হয়ে হৈ চৈ শুরু করে দিলেন। শেষে যখন একটা বিশাল আপৎকালীন পরিষেবার টাইম মেশিন স্টেডিয়ামের গেট অবধি নিয়ে আসা হল তখনই ফেডোসেইভ দৃশ্যমান হল। তাকে বিবর্ণ ও ক্লান্ত দেখাচ্ছে। নীল চোখ দুটো নিষ্প্রভ হয়ে পড়েছে। মাথার চুল ধুলিধূসরিত, ছোট্ট দাড়িটাও একদিকে হেলে পড়েছে। হাসিখুশি মুখটাকে দেখাচ্ছে অন্যমনস্ক। তার প্রশিক্ষক তৎক্ষণাৎ তার কাছে ছুটে গেলেন, জানতে চাইলেন “কি হয়েছে তোমার? কোথায় আটকে পড়েছিলে?”
ফেডোসেইভ ক্লান্তভাবে বলল – “দুর্ঘটনা।”
আশঙ্কিত ইতিহাসবিদ প্রশ্ন করল – “তুমি কি কোথাও থেমে গিয়েছিলে?”
– “বেশিক্ষণের জন্য নয়।”
– “কোথায়? কোন শতাব্দীতে?”
– “যন্ত্রের প্যানেলে দেখুন!”
সকলে প্যানেলের দিকে তাকিয়ে দেখলেন সূচক তেত্রিশশ খৃষ্টপূর্বাব্দে থেমে আছে।
– “এমন একটি রেকর্ড নষ্ট হল!” প্রশিক্ষক নিজের হাত নাড়িয়ে বললেন, “ইসস্!” তারপরে পিছন ফিরে তিনি চলে গেলেন।
সময়-দৌড় চলাকালীন থেমে যাওয়ার জন্য ফেডোসেইভকে কয়েক মাসের জন্য প্রতিযোগিতা থেকে বহিষ্কার করা হল। কিন্তু সে তার জীবন খেলা ছাড়া ভাবতে পারে না বলে আগের মতোই অনুশীলনে যেতে লাগল। মন দিয়ে তার প্রশিক্ষকের উপদেশ শুনত, ইতিহাসবিদের বক্তৃতা শুনতো। প্রশিক্ষক তার কাজের সময় থেকে কিছুটা সময় বাঁচিয়ে একটা বই লেখায় মনোনিবেশ করেছিলেন – “নবীন সময়-যাত্রীদের সঙ্গী”। কিন্তু ইতিহাসবিদ সর্বান্তঃকরণে চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছিলেন। এমনকি পরিচিত এক বলবিদ্যা ও গণিতের স্নাতককেও তিনি বক্তৃতা দিতে নিয়ে এলেন, যিনি খেলোয়াড়দের ঋনাত্মক সম্ভাবনা ও অন্তর্বর্তী স্থানের দৃষ্টিতে সময়ের মধ্যে অগ্রসর হওয়ার তত্ত্ব ব্যাখ্যা করলেন।
ইতিহাসবিদ খেলোয়াড়দের গোটা দলটাকে একটা মিউজিয়ামে নিয়ে গেলেন, যাতে তারা সময়-পথের বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ স্থান সম্পর্কে ওয়াকিবহাল হতে পারে। ছোট্ট কুড়ুল, শবাধার, শকট … এক একটি চমকপ্রদ কক্ষের মধ্যে দিয়ে তাদের যাওয়ার অভিজ্ঞতা টাইম মেশিনে চড়ে শতাব্দী পাড়ি দেওয়ার চেয়ে কিছু কম ছিল না। হঠাৎ আপাততুচ্ছ একটা বস্তুর সামনে ফেডোসেইভ থমকে গেল। সবাই চলে গেলেও সে নড়তে পারছিল না। যেন তার পা মাটিতে গেঁথে গেছে। ইতিহাসবিদ ফিরে তার দিকে এগিয়ে এলেন। মনের গভীরে কোথাও তিনি ফেডোসেইভের সমব্যথী ছিলেন। তাঁর নিজেরও স্বপ্ন ছিল এ ধররণের অত্যাশ্চর্য অভিযাত্রার, কিন্তু তা আর হয়ে ওঠেনি। কারণ সূর্যকে দিগন্তরেখার সাথে মেলানোর কৌশল তিনি রপ্ত করতে পারেন নি।
– “এটার দিকে তাকিয়ে কি দেখছো?” অমায়িকভাবে ফেডোসেইভের কনুইয়ে হাত রেখে তিনি বললেন, “এটা নিওলিথিক যুগের পরের সময়ের একটা সাধারণ উপাসনার উপকরণ। মহান তিয়েন-ৎলিটস্ সাম্রাজ্যের রাজধানীর প্রত্নতাত্ত্বিক খননের সময় একটা উপাসনাগার থেকে এটি পাওয়া যায়। সবই নিচে লেখা আছে।”
– “না” ফেডোসেইভ বলল, “ওটা আমার সিগারেট জ্বালানোর লাইটার।”
– “কি?” ইতিহাসবিদের চোখ বিস্ফারিত হয়ে উঠল, যেন তিনি সামনে জ্যান্ত ফ্যারাও কে দেখছেন।
– “হ্যাঁ, তাই তো বলছি!”
– “তা কি করে হয়?”
– “আপনার মনে আছে আমার শেষ প্রতিযোগিতা, যার পর আমি বহিষ্কৃত হই? আমি সময়-পথ ধরে বহু দূরে চলে গেছিলাম। ফোটন মন্দায়ক-এর তারটার ঝামেলায় না পড়লে আমিই জিততাম। পুরস্কারটা চোখে না দেখে প্যারানোমভকে ওটার কথা কেবল শুনেই সন্তুষ্ট থাকতে হত। আমি আমার মেশিন চালানোর অনেক চেষ্টা করেছিলাম। তারটা টেনেছিলাম, কিন্তু ওটা বাজেনি। আবার টানলাম, তাও বাজলোনা। গতি তখন ভয়ঙ্কর। আপনি নিজেই বুঝতে পারছেন, নিয়ন্ত্রণহারা ওই মেশিনে থাকলে একটা মানুষের স্রেফ দুটুকরো হয়ে যাবার কথা। আমাকে থামতেই হতো। আমার সাথে যন্ত্রপাতি সারানোর সরঞ্জাম সর্বদা থাকে, তাই ঢাকনা খুললাম। দেখি, তারটা কেটে গিয়ে একটি সুতো দিয়ে ঝুলছে। সেটার মেরামতিতে লাগলাম। কারিগর বোল্টটা অতিরিক্ত জোরে এঁটে দিয়েছিল আর আমি সারাক্ষণ সেটা নিয়ে টানাটানি করে যাচ্ছিলাম। যাই হোক, তবু তো ওটা ফার্স্ট গিয়ারে চলছিল। কী করব ভেবে না পেয়ে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে মাথা চুলকাচ্ছিলাম। একবার মনে হল – না থামলেই হত। এই জুড়ে থাকা সুতোর সাহায্যেই ফিরে যাওয়া উচিত ছিল। হয়তো সময়ের মধ্যে মিলিয়ে যেতাম, কিন্তু জন্মের তিনশো শতাব্দী আগে বসে থেকে সময় নষ্ট করার চেয়ে সেটা বরং ভালো হত।
আমি চারদিকটা খেয়াল করিনি, তার সময়ও ছিল না। হঠাৎই দেখতে পেলাম কাছেই প্রায় দশ ফুট দূরে একটা জঙ্গল থেকে লাফিয়ে কজন বেঁটে খাটো মানুষ বেরিয়ে এল। ওরা চেঁচিয়ে কিছু বলল। তারপর সবাই ছুটে এসে হাঁটু গেঁড়ে বসল। আমি জিজ্ঞেস করলাম – “ওরকম করছ কেন?”
ওরা বিড়বিড় করতে লাগল। খালি পা, প্রায় নগ্ন, পরণে শুধু কোমর থেকে ঝোলানো বুনো জন্তুর ছাল। পানীয় চাইতে ওরা পশুর চামড়ায় করে কিছুটা জল এনে দিল। চামড়াটা খুব অপরিষ্কার ছিল। বললাম,
– “প্রশিক্ষক আমায় কাঁচা জল খেতে নিষেধ করেছেন। ফোটানো জল নেই?”
ওরা কিছুই বুঝল না। তখন মাথায় এলো যে, ওরা এখনো আগুন-এর ব্যবহার জানেনা। একটা বাটির মতো আকৃতির পাথর খুঁজে বের করলাম। তার মধ্যে জলটা ঢেলে কিছু খড়কুটো জোগাড় করে আগুন জ্বেলে জলটা ফুটিয়ে খেয়ে নিলাম। ওদের ছেঁড়া তারটা দেখাতে কিছুক্ষণ চিন্তা করল। তারপর গাছের বাকলের কিছু আঁশ টেনে নিয়ে এল। সেটা নিয়ে কাজে লেগে গেলাম। খারাপ দাঁড়াল না। তারটা ধরে রাখা যাবে। বললাম,
– “ধন্যবাদ বন্ধুরা! আমার লাইটার টা স্মারক হিসেবে রাখো। এটার সাহায্যে ঝলসানো মাংস আর ফোটানো জল খেতে পারবে। কখনোই অবিশুদ্ধ জল খেও না। ওতে লক্ষ লক্ষ জীবাণু রয়েছে। তোমরা শান্তিতে থেকো, ভালো থেকো বন্ধুরা।”
এই বলে, সেখান থেকে টাইম মেশিনে করে উড়ে চলে এলাম। দেখতেই পাচ্ছ, আমি ওদের সাথে দশ মিনিট মতো কাটিয়েছিলাম। কিন্তু এখানে ততক্ষণে প্রায় তিন ঘন্টা কেটে গেছে … দাঁড়াও, আরে কী করছ?”
ইতিহাসবিদ ফেডোসেইভের হাত ধরে টানতে টানতে মিউজিয়াম থেকে বেরোবার পথের দিকে নিয়ে যেতে লাগলেন। তারা মসৃণ মেঝের উপর দিয়ে রীতিমতো ছুটছিল আর স্নাতক ছাত্রটি দাঁতে দাঁত চেপে বার বার বলছিল, “আমার সাথে সাথে এসো।”
বাড়ি পৌঁছে ইতিহাসবিদ হতচকিত ফেডোসেইভকে একটা আরামকেদারায় ঠেলে দিয়ে বইয়ের তাক থেকে একটা ছোট বেগুনী রঙ-এর বই টেনে প্রয়োজনীয় পাতাটা খুঁজে বের করলেন।
– “তোমার মুখে তখন দাড়ি ছিল, তাইনা?”
– “হ্যাঁ,” ফেডোসেইভ কিছুটা লজ্জিতভাবেই বলল, “ছিল কিছুটা। ওরা অবশ্য কেটে ফেলতেই বলেছিল, কারণ অন্যরকম দেখতে লাগছিল।”
– “শোনো তাহলে”, এই বলে ইতিহাসবিদ বইটা কিছুটা দূরে ধরে স্ত্রোত্রগীতের ভঙ্গীতে পড়তে শুরু করলেন,
– “তিনি স্বর্গ থেকে আমাদের কাছে এসেছিলেন। তাঁর ছিল লাল রঙ-এর দাড়ি । তিনি ছিলেন মহান এবং জ্ঞানী। আমাদের শিখিয়েছিলেন আগুন জ্বালাতে। তা নেভানোর উপায়ও দেখিয়েছিলেন। তিনি আমাদের দান করলেন একটি আত্মা যে আগুনকে জ্বলার নির্দেশ দেয়। তারপর তিনি তাঁর স্বর্গে ফিরে গেলেন। তিনি ছিলেন সূর্যের পুত্র ও চন্দ্রের ভ্রাতা! … ”
“এই প্রাচীন স্ত্রোত্রগুলো ওখানেই খননকাজের সময় পাওয়া গেছে। বুঝলে কিছু?”
ফেডোসেইভ কাঁধ ঝাঁকালো।
“সেই ব্যক্তি ছিলে তুমি! তুমি স্বর্গ থেকে ওদের কাছে গিয়েছিলে এবং ওদের সেই জিনিসটা দিয়েছিলে যা দিয়ে আগুন জ্বালানো যায়। এভাবেই ওরা তোমার লাইটার সম্পর্কে বলেছে। তুমিই সভ্যতার সূত্রপাত ঘটিয়েছিলে। তুমি মহান!”
“ভাব একবার!”, ফেডোসেইভ বলে উঠলো, “ওরা ভুলে যায়নি! সূর্যের পুত্র, চন্দ্রের ভ্রাতা!”
–“হ্যাঁ! শিক্ষাবিদ অর্নিথোপটেরস্কির অনুবাদে।”
ইতিহাসবিদ এই আশ্চর্য ঘটনার সম্পর্কে অনেক প্রবন্ধ লিখেছিলেন, যেমন – “একটি মহৎ কাজ”, “বিপদে সহায়তা করলেন খেলোয়াড়”, “প্রকৃত খেলোয়াড়ের মতো ব্যবহার” ইত্যাদি। ফেডোসেইভ জনপ্রিয় হয়ে উঠল। অনেক চিঠি পেতে শুরু করল সে। খেলার জগতের থেকে অনেক দূরে থাকা লোকেরাও তার সম্পর্কে জানল। তাকে আবার দলে ফিরিয়ে নেওয়া হল আর সেও আসন্ন প্রতিযোগিতার জন্যে কঠিন প্রস্তুতি শুরু করে দিল। শুধু তাইই নয়, সে নিজেকে বার বার প্রশ্ন করত আর ভাবত কেন সে সভ্যতার সূত্রপাত করার পরও বুঝতে পারল না?
এতে কিন্তু তার গুমোর হয়নি। সে বিশ্বস্তভাবে অনুশীলন চালাতে লাগল। সকলেই তাকে নিয়ে সন্তুষ্ট, শুধুমাত্র তার প্রশিক্ষক ছাড়া। তাঁর মতে, তাঁর ছাত্রটির মধ্যে যথেষ্ট পরিমানে লড়াকু মানসিকতা নেই। সভ্যতা হল গিয়ে সভ্যতা, ঠিক আছে। কিন্তু এসব সামাজিক ব্যাপার স্যাপার খেলোয়াড়ের সাফল্যের পথে বাধা হতে পারে না। প্রতিযোগিতা চলাকালীন তোমাকে যে কোনো মূল্যে জেতার চেষ্টা করতে হবে, সভ্যতার সৃষ্টি-টিষ্টি অবসর সময়ে করলেই তো হয়! প্রশিক্ষক ধরেই নিয়েছিলেন খেলোয়াড় হিসেবে ফেডোসেইভের কোন ভবিষ্যৎ নেই। কিন্তু সমাজে ফেডোসেইভের মহান কীর্তির যে প্রতিক্রিয়া হয়েছিল, তাতে প্রশিক্ষক তাঁর ধারণা আর কাউকে বলে ওঠেন নি। এমনকি দুবার তো নৈতিক বিষয় নিয়ে সংবাদপত্রে তাঁর মতামতও প্রকাশিত হয়েছিল।
অনুবাদ প্রসঙ্গেঃ

রোমেন ইয়ারোভ (Ромэн Ефремович Яров) (Romain Efremovich Yarov): জন্ম ১২ ফেব্রুয়ারি, ১৯৩৩, মস্কো, মৃত্যু : ২৯ জানুয়ারি, ২০০৫, টেক্সাস। মস্কো ইনস্টিটিউট অফ অটোমোবাইল ট্রান্সপোর্ট থেকে তিনি স্নাতক হন। বিজ্ঞানের ইতিহাস সংক্রান্ত বহু জনপ্রিয় নিবন্ধের এই লেখক বহু সাহিত্যসৃষ্টিও করেছেন। ১৯৭৭ এ তিনি USSR ছেড়ে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে থিতু হন। বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ অ্যান্থলজিতে তাঁর গল্প স্থান পেয়েছে, যেমন – ‘বিদায় মংগলগ্রহী’ গল্পটি ১৯৬৮ সালে মির পাবলিশার্স প্রকাশিত রবার্ট ম্যাজিডফ সম্পাদিত “দ্য মলিকুলার ক্যাফে’ সংকলনভূক্ত ছিল।
‘দ্য ফাউন্ডিং অফ সিভিলাইজেশন’ (The Founding of Civilization) গল্পটি ১৯৬৮ সালে নিউইয়র্ক ইন্সস্টিটিউট প্রেস প্রকাশিত ‘রাশিয়ান সায়েন্স ফিকশন’ সংকলন ও ১৯৭০ সালে র্যানডম হাউস প্রকাশিত ‘আদার ওয়ার্ল্ড আদার সী’স’ সংকলনভূক্ত ছিল।
বর্তমান অনুবাদটি গ্যালাক্সি পাবলিসিং কর্পোরেশন কর্তৃক প্রকাশিত ফ্রেডেরিক পোহল (Frederik Pohl) সম্পাদিত ‘ইন্টারন্যাশনাল সায়েন্স ফিকশন’ পত্রিকার জুন ১৯৬৮ সংখ্যায় হেলেন সালট্জ জ্যাকবসন (Jacobson, Helen Saltz) কৃত ইংরেজি অনুবাদ (The Founding of Civilization) থেকে করা হয়েছে ।
পিউ ফাদিকার: বিজ্ঞানের ছাত্রী। যদিও ছোটবেলা থেকে পাঠ্যপুস্তকের তুলনায় গল্পের বই-এর প্রতি বেশি আকর্ষণ অনুভব করতেন। সাহিত্যানুরাগী হলেও সাহিত্যচর্চার পথে এই তাঁর প্রথম পদক্ষেপ।
কৃতজ্ঞতা: রোমেন ইয়ারোভ, গ্যালাক্সি পাবলিসিং কর্পোরেশন, ফ্রেডেরিক পোহল, ‘ইন্টারন্যাশনাল সায়েন্স ফিকশন’ পত্রিকা, হেলেন সালট্জ জ্যাকবসন
Tags: দেবজ্যোতি ভট্টাচার্য্য, দ্বিতীয় বর্ষ চতুর্থ সংখ্যা, পিউ ফাদিকার, রাশিয়ান অনুবাদ গল্প, রোমেন ইয়ারোভ, সভ্যতার সূচনা
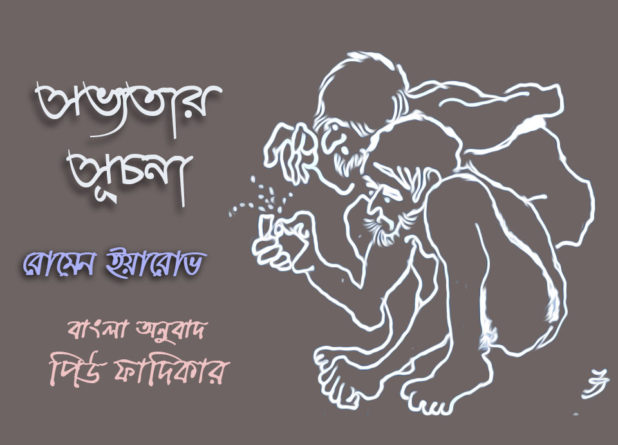

বড় ভাল গল্প। অনুবাদটাও চমৎকার।