অদ্রীশ বর্ধনঃ যেমন দেখেছি
লেখক: বিশ্বদীপ দে
শিল্পী: দেবজ্যোতি ভট্টাচার্য (চিত্রচোর)
একটা আলো–আঁধারির ল্যান্ডিংয়ে দাঁড়িয়ে ছিলাম। সামনের ক’টা ধাপ পরেই দেখা যাচ্ছে দরজা আর কলিং বেল। ওপারেই তিনি থাকেন। আজ প্রথমবার তাঁর মুখোমুখি হব।
প্রথমবার কথাটা হয়তো ঠিক নয়। বইমেলার স্টলে তো কতবার তাঁর সামনে গিয়ে দাঁড়িয়েছি। বাড়িয়ে দিয়েছি সদ্য কেনা বই। সেরা আশ্চর্য সেরা ফ্যান্টাস্টিক, সবুজ মানুষ কিংবা মিলক গ্রহে মানুষ। গম্ভীর মুখে অন্যমনস্ক ভাবে সই দিয়েছেন ব্লেজার পরিহিত গম্ভীরদর্শন এক বৃদ্ধ। শুভেচ্ছা সহ অদ্রীশ বর্ধন।
আসলে সই দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে বইয়ের বিল করা এবং টাকাপয়সার লেনদেন সেরে ফিরতি খুচরোর হিসেবে তখন তিনি বেজায় ব্যস্ত। লেখক শুধু নন, তখন তিনি প্রকাশকও। তাছাড়া সে তো নিতান্তই তাৎক্ষণিক মোলাকাত। মধ্যরাতে নির্ঘুম চোখে টানটান হয়ে বসে যাঁর লেখা পড়েছি কিংবা ছুটির দুপুরে বালিশে হেলান দিয়ে যাঁর লেখনী আমাকে মুগ্ধ করেছে দিনের পর দিন, তাঁকে নিয়ে কি অত সহজে মন ভরে?
কৈশোর পেরিয়ে তারুণ্য। পেরিয়ে গেছে বেশ অনেকগুলো বছর। আস্তে আস্তে শুরু হয়েছে যুবকবেলা। পড়তে পড়তে লেখা লেখা খেলায় মেতে উঠেছি। শুরু হয়েছে বন্ধুবান্ধবের সঙ্গে দল বেঁধে পত্রিকা করা। সেই সূত্রেই এবার তাঁর কাছে আসা। একটা সাক্ষাৎকার নিতে চাই। ফোনে খুব বেশি সময় নষ্ট করেননি। কেবল বাড়ির ঠিকানা আর কোন সময়ে আসতে হবে সেইটুকু বলে দিয়েছেন।
সেইমতো এসে পড়া। ৪, রামনারায়ণ মতিলাল লেন। সময়টা বর্ষাকাল। কিন্তু সেদিন বৃষ্টি নেই। তবে আকাশ মেঘলা। দমচাপা একটা গরমের দিন। সবে বিকেল থেকে সন্ধে হচ্ছে। এরকমই এক সময় গুটি গুটি পায়ে পৌঁছে গেছি।
২০১০ সালের সেপ্টেম্বর মাস। সময়ের হিসেবে প্রায় সাত বছর আগের কথা। আজও স্পষ্ট মনে আছে। মগ্ন পাঠকের কাছে প্রিয় লেখক একজন ফিল্মস্টার কিংবা খেলোয়াড়ের মতো ‘লার্জার দ্যান লাইফ’ হয়ে ওঠেন। সায়েন্স ফিকশন, ফ্যান্টাসি কিংবা অলৌকিক সমস্ত উপাদানে ঠাসা যাঁর সাহিত্য, তিনি যে ব্যক্তি হিসেবেও পাঠকের মনে এক রোমাঞ্চকর ইমেজ গড়ে তুলবেন তাতে আর আশ্চর্য কী! তাই সিঁড়ি দিয়ে উঠে কলিং বেল টেপার আগের সেই মুহূর্তে এক দমচাপা ছেলেমানুষি উত্তেজনায় ফুটছিলাম আমরা সবাই।
২
সবকিছু বদলে গেছিল মুহূর্তে। শুভ্রকেশ, হাস্যমুখ যে বৃদ্ধ সেদিন আমাদের মুখোমুখি হয়েছিলেন, তাঁকে দেখে অবাক হয়েছিলাম। কোথায় সেই বইমেলার গম্ভীর মানুষটা! ইনি তো একজন সদালাপী, রসস্নিগ্ধ মানুষ! যিনি সস্নেহে তাঁর থেকে বয়সে কয়েক দশকের ছোটদের পিঠ চাপড়ে দিয়ে বলেন, ‘তোমরা অনেক ছোট। কিন্তু সমমনস্ক। তাই কথা বলতে ভালো লাগছে। নিছক পাগলামি থেকে আমি লিখতে এসেছিলাম। পত্রিকা করেছি। তোমাদের দেখে সেই শুরুর দিনের কথা মনে পড়ে যাচ্ছে। কী পাগলামিই না করেছি!’ বলতে বলতে রীতিমতো অট্টহাসি হেসে ওঠেন তিনি!
অবাক হয়ে দেখলাম, কী অনায়াসে তিনি তাঁর জীবনের নানা অধ্যায়, এমনকী খুব ব্যক্তিগত শোকের কথাও অনায়াসে বলে ফেললেন অদ্রীশ বর্ধন। বাংলা সাহিত্যের চিরকালীন ফ্রেমে অনায়াসে যাঁর জন্য একটি জায়গা নির্দিষ্ট। একথা শুনে অনেকেই ভুরু কোঁচকাবেন। আসলে স্পেকুলেটিভ ধারার লেখকদের সম্পর্কে একধরনের অবহেলা বাংলা বাজারে একেবারে প্রতিষ্ঠিত। যেন এসব লেখা নিতান্তই মনোরঞ্জনের জন্য লেখা। একেবারেই লঘু বিনোদন ছাড়া যা থেকে আর কিছুই পাওয়ার নেই। একথা অবশ্য অদ্রীশবাবু তাঁর লেখালেখির শুরু থেকেই জানতেন। স্বভাবসিদ্ধ ভঙ্গিতে আমাদের জানিয়েওছিলেন, ‘জানতাম ওই ধারার লেখা সবচেয়ে অবহেলিত। কিন্তু সেটাই আমার জেদ বাড়িয়ে দিয়েছিল। ওইটা যখন অবহেলিত, তখন ওটাই আমি লিখব।’
এটাই অদ্রীশ বর্ধনের আজীবনের স্পিরিট। বারে বারে চাকরি ছেড়েছেন। হন্যে হয়ে খুঁজে বেড়িয়েছেন নতুন কী করা যায়। সমাজের প্রচলিত প্রোটোটাইপের বিরুদ্ধে অন্য এক ভুবন গড়ে তোলার অভিপ্রায়েই তাঁর সংগ্রাম। না হলে ভেবে দেখুন, ছয়ের দশকের একেবারে শুরুর সময়ে তিনি সায়েন্স ফিকশন লেখা শুরু করলেন। জঁরটির নামের বঙ্গীকরণ করলেন ‘কল্পবিজ্ঞান’। সেই সময়ে সেটা কিন্তু একেবারেই অপ্রচলিত ধারা। যদিও প্রেমেন্দ্র মিত্র, ক্ষিতীন্দ্রনারায়ণ সহ অনেকেই তাঁদের লেখায় এই বিষয়কে নিয়েই কাজ করেছেন। কিন্তু সবকিছু ছেড়ে কেবল এই জঁরকে জনপ্রিয় করে তুলতে উঠেপড়ে লাগা… সে কাজটা নিয়তি দিয়েছিল অদ্রীশ বর্ধনকেই। স্রোতের উলটো পথে হেঁটে এক নতুন ভূখণ্ড আবিষ্কারের নেশা ছড়িয়ে গিয়েছিল তাঁর রক্তের অন্তর্লীন স্রোতে।
৩
পরবর্তী সময়ে বারবার তাঁর মুখোমুখি হওয়ার সুযোগ হয়েছে। গত কয়েক বছরে দেখেছি কীভাবে জরা গ্রাস করে ফেলছে এক কর্মচঞ্চল, ছটফটে প্রাণকে। হেয়ারিং এইড লাগিয়েও কানে সেভাবে শুনতে পান না। স্মৃতির পাতা কুড়ে কুড়ে খাচ্ছে বিস্মৃতির পোকা। এক কথাই বারবার বলে ফেলেন। কিন্তু যেটাই বলেন, সেখানে থাকে গভীর বিশ্বাসের স্পর্শ। বোঝাই যায়, ভিতরে ভিতরে যে আগুনটা জ্বলছিল, সেটা কিন্তু একই রকম আছে।
ছোটবেলা থেকেই ডানপিটে স্বভাবের অদ্রীশের মনের মধ্যে ছিল অজানার প্রতি তীব্র আকর্ষণ। তাই দশটা–পাঁচটার চাকরি করতে মন সায় দিত না। একে একে সাতটি চাকরি ছেড়ে দেওয়ার পর তিনি ঠিক করলেন এমন কাজ করবেন, যেটা কেউ করেনি। শুরু হল ‘আশ্চর্য’। বাড়িতেই বসিয়ে ফেললেন প্রেস। কম্পোজও হত ওখানেই। সম্পাদকের নাম হিসেবে ছদ্মনাম (আকাশ সেন) ব্যবহার করেছিলেন তিনি। উদ্দেশ্য, যাতে নিজের নামে অনেক লেখা লিখতে পারেন। তার জন্যও পুলিশের পাল্লায় পড়তে হয়েছিল। সবকিছুকে সামলে নিয়ে বাংলা কল্পবিজ্ঞানের আন্দোলনকে এগিয়ে নিয়ে গিয়েছিলেন তিনি।
এরপর আলাপ সত্যজিৎ রায়ের সঙ্গে। সেই অভিজ্ঞতার কথা বলতে গেলে আজও দু–চোখ চকচক করে ওঠে। ‘উনি আমাকে স্টাডি করেছিলেন প্রথমদিন। আসলে দেখে নিচ্ছিলেন ধান্দাবাজ কিনা। যখন বুঝলেন আমি তা নই, তখনই আমাকে গুরুত্ব দিলেন। সায়েন্স ফিকশন সিনে ক্লাব হোক বা আশ্চর্য, পাশে থেকেছেন। লেখা তো দিয়েছেন বটেই। সঙ্গে নতুন নতুন আইডিয়াও দিতেন।’
সেই সময়, খ্যাতির উত্তুঙ্গ উচ্চতায় থাকা সত্যজিৎ নিজের কর্মব্যস্ততার মধ্যেও অদ্রীশকে বিরাট গুরুত্ব দিয়েছেন। ধৈর্য ধরে বেছে দিয়েছেন সিনে ক্লাবে দেখানোর জন্য সায়েন্স ফিকশন ছবি। ছবি দেখানোর সময় সঙ্গে থেকেছেন। এমনকী ছবি চলার সময় সাউন্ডের কোনও গোলমাল হলে ‘সাউন্ড’ বলে চেঁচিয়ে উঠেছেন… এই সবই প্রমাণ করে দেয় তিনি কতটা ইনভলভ থাকতেন এই কর্মকাণ্ডের সঙ্গে।
আসলে নিজের অসামান্য পর্যবেক্ষণ শক্তিতে সত্যজিৎ চিনতে পেরেছিলেন অদ্রীশের ভেতরের শক্তিকে। তাই প্রয়োজনমতো উৎসাহ দিয়ে গেছেন। এমনকী জীবনের সবচেয়ে কঠিন সময়েও কাঁধে হাত রেখেছেন। অকালে পত্নী বিয়োগে অদ্রীশ তখন দিশেহারা। সেই সময় পাশে থেকেছেন তাঁর ‘মানিকদা’।
পাশে ছিলেন প্রেমেন্দ্র মিত্রও। কিংবা ‘রামধনু’ পত্রিকার সম্পাদক ও কল্পবিজ্ঞান লেখক ক্ষিতীন্দ্রনারায়ণ ভট্টাচার্য। সেই সময়ের তরুণ ও শক্তিশালী লেখকেরাও তাঁকে ভালোবেসে লেখা দিয়েছেন। সেদিনের সুনীল–শীর্ষেন্দু–সৈয়দ মুস্তাফা সিরাজরা। ‘আশ্চর্য’ হোক, বা ‘ফ্যান্টাস্টিক’… সম্পাদক অদ্রীশকে ফেরাননি তাঁরা কেউই।
ছয়ের দশক বাংলা কল্পবিজ্ঞানের এক অলোকসামান্য যুগের সূচনা করে। ‘আশ্চর্য’ পত্রিকার জন্ম। এবং চলচ্চিত্রের আঙিনায় প্রতিষ্ঠার শিখরে পৌঁছে যাওয়া সত্যজিতের লেখালেখি শুরু। প্রফেসর শঙ্কুর জন্ম। সবই খুব অল্প সময়ের মধ্যে পরপর ঘটে গিয়েছিল। শঙ্কু কাহিনি আদৌ কল্পবিজ্ঞান নাকি ফ্যান্টাসি, তা নিয়ে তর্ক এক্ষেত্রে অনাবশ্যক। আসল কথা হল, এই দুই মিলে গিয়ে একটা ‘মুড’ গড়ে ওঠা। যা সেই সময়ের বাংলা সাহিত্যের পাঠকদের উৎসাহিত করে তুলেছিল। তথাকথিত ‘মূলধারার’ লেখকরাও এই ধারায় লিখতে উৎসাহিত হয়েছিলেন।
৪
অকালে স্ত্রীকে হারিয়ে জীবনের ভরকেন্দ্র টলে গিয়েছিল মানুষটার। আর তাই বন্ধ হয়ে গিয়েছিল ‘আশ্চর্য’। কোনও সন্দেহ নেই, এই ছেদ না পড়াটাই কাম্য ছিল। কিন্তু জীবন নিজের মতোই তো চলবে। তা–ই নিয়ম। সে কারণেই ইতিহাস বারবার বাঁক বদল করে।
স্ত্রীর মৃত্যু তাঁকে নতুন করে জীবন চিনিয়েছিল। যেন শোকের আগুনে পুড়ে আরও গনগনে হয়ে উঠলেন মানুষটা। মধ্যরাতে ঘুম ভেঙে যেত। তিনি উঠে লিখতে বসতেন। লিখতে লিখতেই দেখতেন পুব আকাশের গায়ে লালচে ছোপ। ভোর হচ্ছে। পাশে শুয়ে ঘুমিয়ে কাদা শিশুপুত্র।
এই সময়েই অনুবাদ করেছেন জুল ভের্ন। লিখেছেন উপন্যাসও। জীবনের সেই কঠিন সময়টাকে অক্ষরে অক্ষরে বেঁধেছেন। সেই উপন্যাস আজ আর পাওয়া যায় না। কিন্তু ওই লেখা তাঁকে শান্ত করেছিল। একথা বলতে বলতে তাঁর চোখ দুটো বেদনাবিধুর হয়ে উঠতে দেখেছি। ‘ওই লেখাটা লিখতে পারায় অনেক শান্তি পেয়েছিলাম। যে কথাগুলো মনের মধ্যে জমেছিল, সব ওই উপন্যাসের মধ্যে ঢেলে দিয়েছিলাম। আমার একমাত্র সামাজিক উপন্যাস। তবে এর পাশাপাশি জুল ভের্নের লেখাও অনুবাদ করেছি সেই সময়। সেটাও শান্তি দিয়েছিল।’
মৌলিক লেখার সমান্তরালে অদ্রীশ অনুবাদ করে গিয়েছেন নাগাড়ে। জুল ভের্ন। এডগার অ্যালেন পো। আর্থার কোনান ডয়েল। এবং অবশ্যই লাভক্র্যাফট। যাঁকে বাঙালির কাছে নিয়ে এসেছিলেন অদ্রীশই। আজ ইন্টারনেটের কল্যাণে লাভক্র্যাফট মোটেই দুষ্প্রাপ্য নয়। কিন্তু সেই সময় খুঁজে–পেতে তাঁর রচনা জোগাড় করে অনুবাদ করে অদ্রীশ বাঙালি পাঠককে ঋদ্ধ করেছিলেন।
অনুবাদের কথায় বারবার বলেছেন, ‘একেবারে যা আছে তার অবিকল অনুবাদ আমি করিনি। ওরকম করলে লেখা কাঠ কাঠ হয়ে যায়। ট্রান্সলেশন নয়, আমি ট্রান্সক্রিয়েশনে বিশ্বাসী। লাভক্র্যাফটের লেখা আমি হরদম এডিট করেছি। যেখানেই দেখেছি অনন্তের পিছনে ছুটতে গিয়ে লেখক জটিল হয়ে যাচ্ছে আমাকে এডিট করতে হয়েছে। আমাকে সবসময় মাথায় রাখতে হয়েছে আমার পাঠকের কথা।’
যেকোনও খ্যাতিমান মানুষকে ঘিরেই প্রশংসার পাশাপাশি ব্যাঁকা কথাও শোনা যায়। অদ্রীশ বর্ধনকে নিয়েও অনেক নেগেটিভ কথা শুনেছি। যার মধ্যে প্রধানতম হল, তাঁর লেখায় বিদেশি ছাপ রয়েছে। একথা যাঁরা বলেন, তাঁরা ভুলে যান মেরি শেলির হাত ধরে যে নতুন ধারার জন্ম হয়েছিল উনবিংশ শতকে, তার পালস কিন্তু বিদেশি রচনার মধ্যেই প্রোথিত রয়েছে। বাংলায় এই ধারার লেখা লিখতে গেলে তাই তার মধ্যে খানিকটা সেই মেজাজ এসেই যায়। অদ্রীশেরও এসেছে। হয়তো অত বেশি পরিমাণে অনুবাদের কাজ করায় তাঁর মৌলিক লেখায় সেই মেজাজ খানিক মিশেছে। কিন্তু তাঁর লেখায় বাঙালিয়ানাও কিছু কম নেই। বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই তিনি লিখছেন আপাত অসম্ভব সব বিষয় নিয়ে। অথচ তাকেই কত প্রাঞ্জল আর স্বাভাবিক ভাবে প্রকাশ করেছেন তিনি! চলতি শব্দের পাশাপাশি তৎসম শব্দের নিখুঁত ও যথোপযুক্ত ব্যবহারে অদ্রীশ পাঠককে তাঁর গদ্যে সম্মোহিত করে তোলেন সহজেই।
আজও তাঁর লেখার কাটতি, বাৎসরিক রয়্যালটির অঙ্ক চোখ কপালে তুলে দেওয়ার মতো। কলেজ স্ট্রিট পাড়ায় অদ্রীশ আজও বহুপঠিত। সে কথাটা অবশ্য যাঁরা ব্যাঁকা কথা বলেন, তাঁরাও জানেন।
দুর্ভাগ্যের বিষয়, প্রথম শ্রেণির প্রকাশকেরা তাঁকে বই বিক্রির ঠিকঠাক হিসেব দিলেও বইপাড়ার অনেক প্রকাশক মোটেই সে পথে হাঁটেননি।
৫
সাহিত্যিক অদ্রীশ। সম্পাদক অদ্রীশ। প্রকাশক অদ্রীশ। একই মানুষ নানা ভূমিকায় সাফল্যের সঙ্গে কাজ করে গেছেন। কী করে পারলেন একসঙ্গে এতকিছু করতে? উত্তরে বরাবরই স্বভাবসিদ্ধ হাসিতে জানিয়েছেন, ‘এর পাশাপাশি মা–হারা শিশুকে মানুষ করার ব্যাপারটাও ছিল। আসলে সবই করতে পেরেছি ভেতরের এক অদম্য জেদ থেকে।’
তাঁর সঙ্গে কথা বলে যেটা মনে হয়েছে, তাঁর ভিতরে একদিকে ছিল খুব হিসেবি, দক্ষ কেজো একজন মানুষ। এই সময়ের অন্যতম প্রধান কল্পবিজ্ঞান লেখক অনীশ দেব বলেছিলেন, ‘অদ্রীশদা একজন দৈত্যের মতো কাজ করেছেন। নিজে লিখেছেন, অন্যকে দিয়ে লিখিয়েছেনও।’ কিন্তু এটা একেবারেই বাইরের স্তর। মনের গভীরে তিনি একজন বালকের মতোই প্রাণচঞ্চল। কাজগুলো তাঁর কাছে খানিকটা খেলার মতো। বাইরে থেকে দেখলে সেই স্তরের পরিচয় মেলে না। কিন্তু আলাপ হলে আস্তে আস্তে বোঝা যায়। আর সেটাই তাঁর অমানুষিক পরিশ্রমের রহস্য।
তাঁকে নিয়ে গবেষণালব্ধ প্রবন্ধ লিখতে বসিনি। সে ক্ষমতাও আমার নেই। একজন সাধারণ পাঠক হিসেবে তাঁর লেখা পড়েছি। পরবর্তী সময়ে সৌভাগ্যক্রমে কাছ থেকে দু–দণ্ড দেখার ও কথা বলার সুযোগ হয়েছে। সেই সব অভিজ্ঞতা থেকে তাঁকে নিয়ে যা মনে হয়েছে তা নিয়েই দু–চার কথার আঁচড় এই লেখা।
শেষ করার আগে একটা ঘটনার কথা বলি। তাঁর একটি ছবি বাঁধিয়ে তাঁকে উপহার দিয়েছিলাম। ছবিটা পেয়ে ছেলেমানুষের মতো উৎফুল্ল হলেন। ঘরের কোণে রাখা যুবক বয়সের একটা ছবি দেখিয়ে বললেন, ‘আমার ওই বয়সের অনেক ছবি রয়েছে। কিন্তু এই বয়সের ছবি সেভাবে নেই। তুমি এটা দিলে, খুব ভালো হল।’ বলতে বলতে পুরোনো ছবিটার দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে রইলেন কিছুক্ষণ। তারপর বললেন, ‘বলো তো কতটা বদলেছি।’
কী আর বলব। হাসলাম। মনে মনে বললাম, বাইরে তো বদল আসবেই। সেটাই নিয়ম। কিন্তু আপনার ভেতরের মানুষটা আজও একই রকম তরুণ রয়ে গেছে। একটু মিশলেই যার নাগাল মেলে। ছোটবেলায় দেখা সেই গম্ভীর লেখকের অবয়ব ছিল নেহাতই এক ক্যামোফ্লেজ। যার আড়ালে থেকে বছরের পর বছর বিপুল কর্মযজ্ঞে আপনাকে সামিল করে রেখেছিল এক প্রাণশক্তিতে ভরপুর সদ্য তরুণ।
সেই তরুণ শতায়ু হোক। আপনি সুস্থ থাকুন, ভালো থাকুন প্রিয় লেখক।
Tags: দেবজ্যোতি ভট্টাচার্য (চিত্রচোর), দ্বিতীয় বর্ষ দ্বিতীয় সংখ্যা, প্রচ্ছদ কাহিনি, বিশ্বদীপ দে
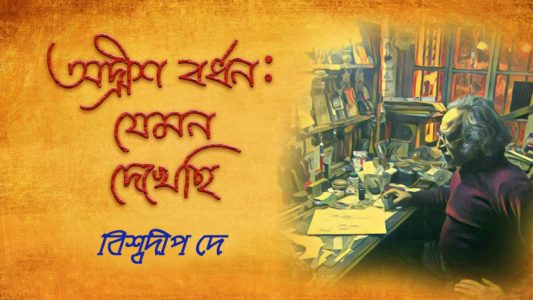

Osomvob sundor lekha Biswadip da.
যখন আমরা কোন প্রিয় লেখককে নিয়ে লিখি, উঠে আসে তাঁর সম্পর্কে জানা অজানা তথ্য, আতশ কাঁচের নিচে ফেলে চুল চেরা বিশ্লেষণ চলে কি দিলেন আর কি নিলেন প্রিয় লেখক। বিশ্বদীপের এই লেখাটা তাই এই সংখ্যার অন্য সব লেখার থেকে আলাদা, ও তথ্যের ভারে ভারাক্রান্ত করেনি লেখাটা, অদ্রীশ বাবুর কাজকে মূল্যায়ন করার গুরুদায়িত্ব ও সে নেয়নি। সে শুধু দেখেছে তাঁর ছোটবেলার স্বপ্নের যাদুকরকে। মনে পড়ে যায় শেষ জীবনের ক্যাপ্টেন নিমোর কথা মিস্টিরিয়াস আইল্যান্ডে, বৃদ্ধ নিমোকে দেখে শ্রদ্ধায় যেমন মাথা নিচু হয়ে গেছিল দ্বীপবাসীদের, ঠিক সেইভাবেই বিশ্বদীপ শ্রদ্ধা জানিয়েছে আরেক ক্যাপ্টেনকে, কল্পবিজ্ঞান ছিল যার সমুদ্র, আশ্চর্য আর ফ্যান্টাসটিক ছিল যার জাহাজের নাম। ভালো থাকুন নীমো, আমাদের মতো ভক্তদের মনের কোণে মিস্টিরিয়াস আইল্যান্ডে রাজত্ব শুধু আপনারই.
শুধু ভালো বললে এই লেখার সম্বন্ধে কিছুই বলা হয় না। অত্যন্ত সংবেদনশীল এই পোস্ট বাংলা সাহিত্যের এক উপেক্ষিত নায়কের ওপর ভালোবাসা ও শুভকামনার গোলাপ ছড়িয়ে দিয়েছে পরম যত্নে।
বিশ্বদীপ অসাধারণ একটা লেখা উপহার দিয়েছ।
খুব মন ছুঁয়ে গেল। বারে বারে অন্যমনস্ক হলুম।
অজানা অদ্রীশ বর্ধনকে আমরা যারা দুরে থাকি তাদের কাছে তুলে ধরবার জন্য বিশ্বদীপবাবুকে অসংখ্য ধন্যবাদ। ওই সাক্ষাৎকারের ছবি যেদিন সোশ্যাল নেটওয়ার্কিংয়ের পর্দায় দেখেছিলাম, সেদিন বিশ্বদীপবাবুর সাথে ঘন্টাব্যাপী চ্যাটাড্ডার কথাও মনে পড়ে যাচ্ছে।
কৃতজ্ঞ রইলাম আপনাদের প্রতি