ক্লোরোফিলিয়া
লেখক: সায়ন্তন ভট্টাচার্য
শিল্পী: সুমন দাস
এক নম্বর কাঠপুল থেকে নৈহাটি রোডের একটা সরু শাখা ডানদিকে ঢুকে হিজলি গ্রামে চলে যায়। মোড়টার সামনে একটা মরা অর্জুন গাছ, পাশে ছোট্ট চায়ের দোকান আর ঠিক মোড়ের মাথাতেই চায়ের দোকানের উল্টোদিকে জাকির কাকার বাড়ি। কাকার বাড়ির সামনে হিজলি যাওয়ার রাস্তা, রাস্তার ওপারে ধু-ধু ধানখেত দিগন্তের কাছে এসে খাটের কোনায় গোঁজা বিছানার চাদরের মতো ভ্যানিশ হয়ে গেছে। বাড়ির পেছনে বিরাট বড় খাল রাস্তাটার সাথে আড্ডা মারতে মারতে হিজলি গ্রামের ভেতরে ঢুকেছে সেই মান্ধাতার আমলে। জাকির কাকা রাজমিস্ত্রী, এখানে সেখানে পাকা বাড়ি বানানো তার পেশা, আর এভাবেই রাকেশের সাথে তার আলাপ। বয়সের ব্যবধান থাকলেও দুজনের মধ্যে অল্প সময়েই বন্ধুত্ব হয়ে গেছিল, রাকেশের তখন ক্লাস থ্রি কি ফোর, জাকির কাকা রান্নাঘরের দেওয়াল গাঁথতে গাঁথতে তাকে মাছ ধরার গল্প শোনাত—কীভাবে জাল ফেলে মাছ ধরতে হয়, বর্ষায় কাঠপুলের খালে যখন স্রোত আসে তখন মশারি দিয়ে খোলসে মাছ ধরার টেকনিক, ছিপের চার কী কী দিয়ে বানায় এসব।
“স্যার, ড. ভট্টাচার্য এসেছেন। ডাকব এখন?”
রাকেশের ঘোর কাটে, ঘড়ি বলছে সোয়া তিনটে, প্রায় দেড় ঘন্টা লেট।
“শিওর, ব্রিঙ হিম প্লিজ!”
ওমাহাতে এই সময় টেম্পারেচার মোটামুটি আরামদায়ক, অন্তত ইন্ডিয়ার অগাস্ট মাসে এমন ওয়েদার আশাও করা যায় না। প্রায় ত্রিশ বছর হতে চলল নেব্রাস্কাতে থাকেন মাল্টি মিলিওনেয়ার ফার্মাসিউটিকাল ব্যবসায়ী রাকেশ দাস। ভারতবর্ষ তাঁকে নিয়ে গর্বিত, এমনকী প্রাইমারী স্কুলের জেনারেল নলেজ বইতে এখন প্রশ্ন রয়েছে, “কোন বিখ্যাত ভারতীয়র তৈরি করা ওষুধের কোম্পানী পৃথিবীখ্যাত?” লাইফ অ্যান্ড বিয়ন্ড নামটা রাকেশেরই দেওয়া। সেই ছাব্বিশ বছর বয়সে তিনজন বন্ধু মিলে বানানো একটা সামান্য সংস্থা কত ঘাটের জল খাওয়ার পরে আজ বিশ্বজুড়ে ড্রাগসের জগত নিয়ন্ত্রণ করছে সেই নিয়ে উপন্যাস লেখা যায়। ইন ফ্যাক্ট, রাকেশের আত্মজীবনী লেখার প্রস্তাবও এসেছে বেশ কিছু গত চার-পাঁচ বছরে। রাকেশ যে বরাবরই এমন ভাগ্যবান ছিল বা সোনার চামচ মুখে নিয়ে জন্মেছিল তা কিন্তু নয়, বরং একটা বয়েস অবধি তাকে বেশ আনলাকি-ই বলা যেত! অসামান্য মেধার অধিকারী রাকেশের সমস্যা একটাই, সে ছিল শিডিউলড কাস্ট। ফলে স্কুলের গন্ডি পেরোনোর পর থেকেই প্রত্যেক পরীক্ষায় সফলভাবে উত্তীর্ণ হওয়ার পরে তাকে শুনতে হত, “এস সি বলে, জেনারেলে দেখতাম কত র্যাঙ্ক হয়!” শুধু কি তাই, ছেলেবেলা থেকেই তাকে সো কলড কদাকার বলা যায়, ফলে ইনফিরিয়রিটি একটা ছিলই। তারপর পৃথিবীর বিভিন্ন জায়গায় গিয়ে “ব্রাউন পিপল, পাকি, নামাষ্ঠে” শুনতে শুনতে তার গায়ে এতদিনে গন্ডারের চামড়ার মতো একটা পরত পড়ে গেছিল। রাকেশ জানত জীবনের সমস্ত জায়গাতেই সে আলাদা—মেধায় নয়, সাফল্যে নয়, ক্ষমতায় নয়। কাস্টে, চামড়ার রঙে, সৌন্দর্যহীনতায়…
“আআহ, বাঙালি!” ঘরে ঢুকেই একটা হোঁচট সামলাতে সামলাতে বললেন কোল্ড স্প্রিঙ হার্বার ল্যাবরেটরীজের বিখ্যাত বটানিস্ট ড. শীর্ষেন্দু ভট্টাচার্য। রাকেশ ভালো করে শীর্ষেন্দুকে আপাদমস্তক পরখ করল—চুল উশকোখুশকো, চোখদুটো গাঁজার দমে লাল হয়ে আছে, পরনের পোশাকটা প্রায় এক সপ্তাহ আগে কাচা। শীর্ষেন্দু একটা চেয়ার টেনে নিয়ে গা এলিয়ে বসে পড়ল, তারপর বলল, “তা আপনি তো দেশের গর্ব মশাই, দুনিয়ার ইকোনমি ওঠে-নামে আপনার মর্জিতে, হঠাৎ আমার এই কন্ট্রোভার্শিয়াল প্রোজেক্টের সাথে নিজেকে প্যাঁচাচ্ছেন কেন?”
(২)
“আপনার আইডিয়াটা একটু ব্রিফ করলে ভালো হত, মানে আপনার পাবলিকেশনগুলো পড়েছি, কিন্তু বিজ্ঞান আর বিজনেস তো এক নয়, বুঝতেই পারছেন আমায় জানতে হবে ইনভেস্টমেন্টটা শেষ অবধি বুনো হাঁস তাড়া করা হবে কি না।” আইডিয়া ব্রিফ করার ধারকাছ না ঘেঁষে শীর্ষেন্দু উলটে রাকেশকে প্রশ্ন করে বসল, “আচ্ছা আমরা রাগ করি কেন? বা ঝগড়া করি কেন? বা যে কোনও কাজ বলুন আপনি—চাকরি করা, ঘুরতে যাওয়া, প্রেম-ভালোবাসা যে কোনও হিউম্যান অ্যাক্টিভিটির উৎস খুঁজুন, উত্তর দেখবেন একটা যায়গায় গিয়েই ঠেকবে—খিদে। আর খিদে হল এমন একটা জিনিস যেটা কোনওদিন কমবে না। আমরা দিনের পর দিন রিপ্রোডিউস করেই যাব, ওভারপপুলেটেড প্ল্যানেটটায় আমাদের অগোচরেই আরেকটা প্যারালাল যন্ত্রের সোসাইটি তৈরি হতে থাকবে আর এই ফ্লো চলতে চলতে আর কিছু বছর পরে পৃথিবীতে খাবার তৈরি করার জন্যে এক আউন্স মাটিও খুঁজে পাওয়া যাবে না। তাহলে উপায়?”
নেশাচ্ছন্ন মানুষ কথা বলতে শুরু করলে থামে না, রাকেশ জানে, ব্যাপারটা তার মতো ব্যস্ত মানুষের কাছে অত্যন্ত বিরক্তিকর। কিন্তু এই লোকটার কাছে এমন একটা জিনিস রয়েছে যেটা গোটা পৃথিবীর চেহারা বদলে দিতে পারে। রাকেশ তাই তার সমস্ত ধৈর্য একত্রিত করে চুপচাপ শীর্ষেন্দুর ভাষণ শুনতে থাকল।
“আমাদের খাওয়ারের মুখ্য উপাদান তিনটে—কার্বোহাইড্রেট, প্রোটিন আর ফ্যাট। প্রথমটা লাগে এনার্জি খরচ করতে আর পরের দুটো মেইনলি লাগে স্ট্রাকচারাল মেইন্টেন্যান্সের জন্য। এখন আমাদের এই অ্যানিমাল কিংডমের সমান্তরালে আরও একটা প্রাণ আছে—গাছ, যারা সূর্যের আলো আর জল থেকে ফটোসিন্থেসিসের মাধ্যমে কার্বোহাইড্রেট তৈরি করতে পারে। ব্যাপারটা সেখান থেকেই প্রথম মাথায় এসেছিল—উদ্ভিদকোষে সালোকসংশ্লেষ হয় ক্লোরোপ্লাস্ট নামের অর্গানে, যেটা অ্যানিমালদের মধ্যে অনুপস্থিত। হিয়ার কামস দ্য ফান পার্ট, ল্যাবরেটরীতে আমার টিম এমন একটা থেরাপি বানিয়েছে যেখানে মানুষের কোষে ইঞ্জিনিয়ার্ড ক্লোরোপ্লাস্ট তৈরি হতে থাকবে ক্রমাগত। ইমপ্যাক্টটা বুঝতে পারছেন? পৃথিবীতে হাঙ্গার বলে আর কিছু থাকবে না! আফ্রিকাতে আর খেতে না পেয়ে মরতে হবে না হাজার হাজার বাচ্চাকে!”
“একটু বাড়াবাড়ি হয়ে যাচ্ছে না? তা ছাড়া এ তো গেল কার্বোহাইড্রেট। প্রোটিন, ফ্যাট কোত্থেকে আসবে?”
রাকেশের অনুমতির তোয়াক্কা না করেই শীর্ষেন্দু পকেট থেকে একটা সিগারেটের প্যাকেট বের করল, তারপর ধীরেসুস্থে সিগারেট জ্বালিয়ে দুটো সুখটান ছেড়ে আবার বলতে শুরু করল, “প্রোটিন আর ফ্যাট তৈরি করা একটু ট্রিকি, তবে পর্যাপ্ত সময় আর গ্রান্ট পেলে আমি পারব সেটাও তৈরি করে ফেলতে। আরে মশাই আস্ত সূর্যটা তৈরি হাইড্রোজেন আর হিলিয়াম দিয়ে, পৃথিবী তৈরি হল কয়েকটা পেতি গ্যাস কনডেন্স করে, আর মানুষ একটা সামান্য মলিকিউল তৈরি করতে পারবে না আউট অফ থিন এয়ার? আমাদের কি গাছের থেকেও বুদ্ধি কম?”
রাকেশের মুখে হাসি ফুটে উঠল। লোকটা একটু খ্যাপাটে তবে সম্ভাবনাময়, তাছাড়া এই বৈজ্ঞানিকের মার্কেট ভ্যালু তার জানা। মূল প্রতিদ্বন্দ্বী একটা জার্মান আর একটা নিউইয়র্ক বেসড কোম্পানী শীর্ষেন্দুর প্রোডাক্ট কেনার জন্যে মরিয়া হয়ে রয়েছে… টেবিলের পাশের পাতাবাহার গাছটা কেমন শুকনো লাগল, ভালো করে জল দেওয়া হচ্ছে না নিশ্চই। সেদিকে তাকিয়েই অন্যমনস্ক চোখে রাকেশ বলল, “আমি আপনার এই ইনভেনশনের পেটেন্ট কিনতে চাই, প্রোভাইডেড নেক্সট দু’বছরের মধ্যে আপনার ল্যাব এমন একটা ক্লোরোপ্লাস্ট তৈরি করবে যেখান থেকে সমস্ত ধরনের নিউট্রিশনের নিডস ফুলফিলড হয়ে যাবে মানুষের। পারবেন?”
(৩)
২৩০০ সাল। এক নম্বর প্লাটিনাম ব্রিজ থেকে রাউট নাইন্টি নাইনের একটা সরু শাখা ডানদিকে ঢুকে আদার্সল্যান্ডে চলে যায়। মোড়টার ঠিক সামনে একটা অক্সিজেন স্টেশন, পাশে জাঙ্কইয়ার্ড আর ব্রিজের তলা দিয়ে যে টক্সিক ওয়েস্টের সরু নদীটা বয়ে যাচ্ছে তার একদম তীরে একটা বাচ্চা দাঁড়িয়ে আছে। বাচ্চাটার চোখে-মুখে ভয়, বয়স মাত্র সাত বছর, পরিবারের সঙ্গে কান্ট্রিসাইডে ঘুরতে এসে পথ হারিয়ে ফেলেছে সে। বাচ্চাটা রুপোলী নদীর দিকে আরেকটু এগোতে গিয়ে থমকে গেল, দূরের জঞ্জালের স্তুপটার পেছন থেকে একটা খসখস শব্দ ভেসে আসছে। দূরের রোবট ইন্ডাস্ট্রিতে বিকেলের ভোঁ ভোঁ সাইরেন বাজার সঙ্গে সঙ্গে একটা মানুষ বাচ্চাটার দিকে এগিয়ে এল…
“আপনার আবিষ্কার আমি দশ বিলিয়ন ডলার দিয়ে কিনে নিয়েছি ড. ভট্টাচার্য, ইটস মাইন। এখন আমার প্রোডাক্ট নিয়ে আমি কিভাবে বিজনেস করব সে জ্ঞান তো আপনার থেকে শুনব না!”
“রাকেশ আপনি একটা বিশ্রী ভুল করছেন। আমি বৈজ্ঞানিক, শুধু ভালবাসা থেকে রিডলস সলভ করি, আমার ক্ষমতা রিসার্চ পাবলিকেশন অবধি। আপনার একটা ভুল স্টেপের জন্য গোটা ওয়র্ল্ড সাফার করতে পারে। কেন বুঝছেন না? কীসের এত ইগো আপনার!”
‘লাইফ অ্যান্ড বিয়ন্ড’ আর নেই। প্রায় আড়াইশো বছর আগে কন্ট্রোভার্শিয়াল হাঙ্গার পিলের ব্যবসা করতে গিয়ে বিভিন্ন মাল্টিন্যাশনাল ফুড চেন আর ফ্র্যাঞ্চাইজির সাথে লড়াইতে হেরে গেছে তারা। বিজনেস টাইকুন রাকেশ দাস বুঝতে পেরেছে, দুনিয়ার সমস্ত সিদ্ধান্ত সেই সব মানুষ নেয় যাদের খিদের চিন্তা নেই… “বুঝল না শীর্ষেন্দু, বুঝল না এরা! ব্রডার অ্যাসপেক্টটাই ধরতে পারল না, বলল চাষীদের কী হবে? তাও ভালো বলেনি আমার থেরাপি মার্কেটে এলে চাষীরা না খেতে পেয়ে মারা যাবে। শালা পয়েন্টটাই বুঝল না! খিদে না থাকলে কতটা ক্রিয়েটিভ হতে পারতাম আমরা, ভাবতে পারছেন? যুদ্ধ থাকত না, ক্রাইসিস থাকত না, কোনওরকম আর্থিক ভেদাভেদ থাকত না।”
“পারছি, কিন্তু আপনি তো গভর্নমেন্টের বিরুদ্ধে যেতে পারেন না! প্লিজ এসব পাগলামি থেকে বেরোন, লুকিয়ে ব্যবসা করতে গিয়ে শেষে আপনি নিজে মরবেন, আমাকেও মারবেন! নিজেকে ঈশ্বর ভাবা বন্ধ করুন প্লিজ!”
বাচ্চাটা মনের সুখে বার্গার চিবোতে চিবোতে টিভি দেখছিল। প্রথমে ভয় পেলেও মানুষটার সঙ্গে তার বন্ধুত্ব হয়ে গেছে। লোকটার নাম জাকির, বৌ-বাচ্চা নিয়ে আদার্সল্যান্ডে থাকে। পেশায় সে বিল্ডার, এখানে-ওখানে বিভিন্ন জায়গায় ঘর বানায় আর অবসর সময়ে নদীতে জাল ফেলে ছোটো ছোটো মাছ ধরে কাঁচের বয়ামে ভরে রাখে। এমন মাছ আগে দেখেনি সে, জাকির বলল জলের বিষের জন্যে ওরা নাকি ইভলভ করে এমন বীভৎস হয়ে গেছে।
“আর একটু পরে একটা ট্রেন ছাড়বে আদার্সল্যান্ড থেকে, তোমার শহর অবধি যাবে। একদম চিন্তা কোরো না, রাত্রের আগেই বাবা-মা’র কাছে ফিরে যাবে তুমি।”
বাচ্চাটার কিন্তু তেমন পরিবর্তন দেখা গেল না! সে মনের আনন্দে বার্গার মুখে পুরে বলল, “জাকির কাকা, তোমরা সবাই সবুজ কেন?”
জাকির এই প্রশ্নের কোনও জবাব দিল না, তারা গত পাঁচ পুরুষ ধরেই সবুজ মানুষ, পৃথিবীর এই কোনায় ওই কোনায় ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা সংখ্যালঘু কম্যুনিটির অন্যান্য সবজে সদস্যদের মতো। রোগটার নাম ক্লোরোফিলিয়া—হাঙ্গার পিলের সাইড এফেক্ট, যেখানে ক্লোরোফিলের আধিক্যে মানুষদের চামড়া গাছের পাতার মতো সবুজ হয়ে যায়। তারা সংখ্যালঘু, কারণ তারা সবুজ, তাদের আর খিদে পায় না, তাদের পৌষ্টিকতন্ত্র আমাদের অ্যাপেনডিক্সের মতো নিষ্ক্রিয়, তারা আর্থিকভাবে অসচ্ছল, তাদের পুর্বপুরুষরা কোনও একদিন দারিদ্র সহ্য করতে না পেরে ‘লাইফ অ্যান্ড বিয়ন্ডের’ পাচার করা হাঙ্গার পিল নিতে শুরু করেছিল আর সেই থেরাপির এতটাই ক্ষমতা যে পরবর্তী প্রজন্মও তার পর থেকে ক্লোরোপ্লাস্ট সঙ্গে নিয়ে বেড়েছে। জাকির সাদা চামড়ার বাচ্চাটার হাত ধরে স্টেশনের দিকে ধীরে ধীরে এগিয়ে গেল, অতি সন্তর্পনে, কারণ স্বাভাবিক নিয়মেই সে এই বাচ্চাটার থেকে আলাদা! তিনশো বছরের প্রাচীন একটা কদাকার, কালো, শিডিউলড কাস্ট ব্যবসায়ীর খামখেয়ালীপনায় জাকির আর তার মতো পরিবারেরা গোটা পৃথিবী থেকে এখন অচ্ছুত হয়ে গেছে…
Tags: কল্পবিজ্ঞান গল্প, চতুর্থ বর্ষ তৃতীয় সংখ্যা, পূজাবার্ষিকী, সায়ন্তন ভট্টাচার্য, সুমন দাস
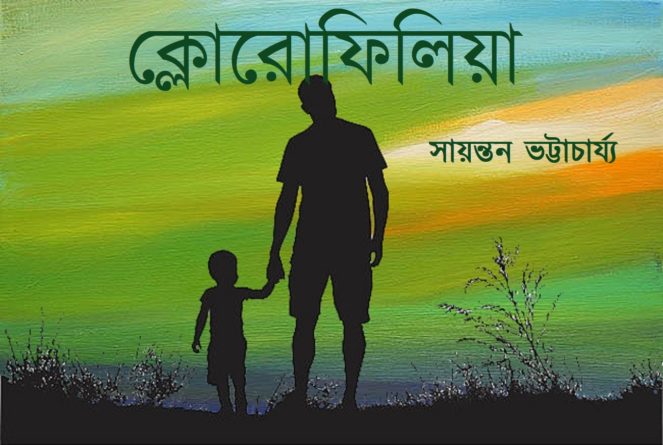

গল্পের নামটা চোখে আটকে গেল, তাই এটি দিয়েই কল্পবিশ্বের এই সংখ্যাটি পড়া শুরু করেছি। লেখার স্টাইল অসাধারণ, প্লট মোটামুটি। প্রায় কাছাকাছি প্লটের গল্প আগে বেশ কয়েকটা পড়া হয়েছে। তবে গল্প বলার ধরনটা ইউনিক। সবমিলিয়ে ভালোই বলা চলে। লেখককে অনেক শুভেচ্ছা।
golpo tay onek layer ache,onek bar porte hobe,galpo bolar style durdanto