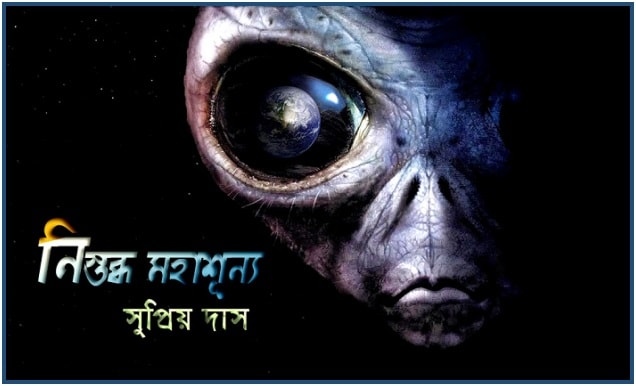নিস্তব্ধ মহাশূন্য
লেখক: সুপ্রিয় দাস
শিল্পী: অন্তর্জাল
লস আলামোস ন্যাশনাল ল্যাবরেটরি, ১৯৫০, গ্রীষ্মকালের একদিন। মধ্যাহ্নভোজনের বিরতি হয়েছে কিছুক্ষণ আগেই।এক্সপেরিমেন্ট রুম থেকে ক্যাফেটেরিয়ায় যাওয়ার করিডোরটা ল্যাবে কর্মরত বৈজ্ঞানিক, গবেষক ও টেকনিশিয়ানদের পায়ের শব্দে গমগম করে উঠল। সেই করিডরে আর সকলের অন্যদিনের মত মধ্যে সেদিনও ছিল চার সহকর্মী বৈজ্ঞানিক। কদিন ধরেই এদের মধ্যে বিরতির সময়ে আলোচনা চলছে একটি বিষয় নিয়ে। ১৯৪৭ সালে রোসওয়েলে ভেঙ্গে পড়া উড়ন্ত বস্তুটি নিয়ে সম্প্রতি খবরের কাগজগুলো আবার হুজুগে মেতে উঠেছে। একদল মানুষের এখনো বদ্ধমূল ধারনা যে ওটা একটা ভিনগ্রহী যান ছিল। তার স্বপক্ষে ও বিপক্ষে যুযুধান হুজুগের দল নানা তর্ক বিতর্ক চালিয়ে যাচ্ছে এখনো। রেডিও বা সংবাদপত্রগুলোও মওকা বুঝে এই বিষয়ে অনেক যৌক্তিক-অযৌক্তিক অনেক কিছুই প্রচার করছে। কিন্তু এই চার বৈজ্ঞানিকের আলোচনা কিন্তু ঘোর বাস্তব এবং গাণিতিক যুক্তি ও বিচারের ওপর নির্ভরশীল। এদের একজন, হার্বাট ইয়র্ক উত্তেজিত হয়ে বলছে, “বাকি ব্রহ্মাণ্ড না হয় বাদ দিলাম। কিন্তু আমাদের এই মিল্কি ওয়ে গ্যালাক্সিতেই ২০০ থেকে ৪০০ বিলিয়ন নক্ষত্র রয়েছে। মানে কম করে ২০০ বিলিয়ন পৃথিবীর মত প্রাণধারণের উপযুক্ত গ্রহ থাকার সম্ভাবনা খুবই প্রবল। যদি তার এক ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র ভগ্নাংশেও বুদ্ধিমান প্রাণীর বিকাশ হয়ে থাকে তাহলেও এই গ্যালাক্সিতেই কয়েক মিলিয়ন মানুষের চেয়ে উন্নত সভ্যতা থাকা সম্ভব যাদের বিজ্ঞান তাদের নিজেদের সৌরজগতের বাইরে অন্য সৌরজগতে নিয়ে যেতে সক্ষম। তাই আমি প্রবলভাবে বিশ্বাসী যে ভিনগ্রহী প্রাণীদের সাথে আমাদের সাক্ষাৎ হওয়া বা তাদের পৃথিবীতে আগমন নেহাতই সময়ের অপেক্ষা।” এই নিয়ে দুই বিজ্ঞানী এডওয়ার্ড টেলার ও এমিল কোনোপিনস্কি আলোচনা চালিয়ে যাচ্ছেন। চতুর্থ জন আগ্রহভরে এঁদের আলোচনা শুনছেন।
এনরিকো ফের্মি ও এডোয়ার্ড টেলার
এদের এই আলোচনার মধ্যেই এরা ক্যাফেটেরিয়াতে এসে টেবিলে বসে আহার শুরু করে দিলেন। তাতে স্বভাবতই আলোচনায় কিছুটা ভাঁটা পড়ল। সবাই আলোচনা বন্ধ করে আহারে মননিবেশ করেছেন এমন সময়ে এতক্ষণ নীরব শ্রোতা হয়ে থাকা চতুর্থ বৈজ্ঞানিকটি মুখ খুললেন। “ওরা সব কোথায়?” আচমকা এই আপাত অপ্রাসঙ্গিক ছোট্ট প্রশ্নটি সেদিনের সেই বাকি তিন বৈজ্ঞানিককেই শুধু আহার থামিয়ে মুখ তুলে ভাবনায় ডুবে যেতে বাধ্য করেনি। বরং তার পরে ছয় দশক ধরে সারা পৃথিবীর মহাকাশ বৈজ্ঞানিকদের বিস্মিত ও ভাবিত করে চলেছে। সেদিনের সেই প্রশ্নকর্তা আর কেউ নন, আধুনিক পরমাণু বিজ্ঞানের এক অন্যতম স্রষ্টা ইতালিয় বৈজ্ঞানিক এনরিকো ফের্মি। সেদিন লস আলামোস ল্যাবরেটরির ক্যাফেটেরিয়াতে বসে ফের্মি শুধুমাত্র এই প্রশ্ন করেই থেমে থাকেননি। বরং তাঁর এই আপাত নিরীহ প্রশ্নের সূত্র ধরে করেছিলেন এক আশ্চর্য সওয়াল। সেই সওয়াল পরবর্তী সময়ে সারা পৃথিবীতে “ফের্মি প্যারাডক্স” নামে পরিচিত হয়, যা আজও মহাকাশ গবেষকদের কপালে ভাঁজ ফেলে চলেছে।
ফের্মি প্যারাডক্স নিয়ে আলোচনা করতে গেলে এর সম্পর্কিত আরও বহু তত্ত্ব নিয়ে আলোচনা করা একান্ত প্রয়োজন। কিন্তু তাত্ত্বিক জটিলতা এড়িয়ে সহজভাবে বললে সেদিন ফের্মি সাহেব যে সওয়াল করেছিলেন তা এরকম:-
দৃশ্যমান মহাকাশে পর্যবেক্ষিত তারার সংখ্যা ও তাতে প্রাণের প্রবল সম্ভাবনা সম্পর্কে বৈজ্ঞানিক মহলে কোন দ্বিমত নেই। এবং সংখ্যাতত্ত্বের বিচারে মানব সভ্যতার চেয়ে কয়েক বিলিয়ন বছর পুরনো লক্ষ লক্ষ ভিনগ্রহী সভ্যতা এই গ্যালাক্সিতেই থাকা উচিৎ। এবং সময়ের নিয়মে সেই সব সভ্যতা পৃথিবীর চেয়ে অনেকগুণ উন্নতও হওয়ার কথা। সেই সভ্যতা গুলির এক সামান্য ভগ্নাংশও যদি আন্তঃসৌর যাত্রা করবার পন্থা আবিষ্কার করে থাকে তাহলেও আমাদের এই পৃথিবীতে এতদিনে ভিনগ্রহীদের পায়ের ধুলো বহুবার পড়াটাই স্বাভাবিক। নিদেনপক্ষে তাদের আগমনের কোন চিহ্ন বা মহাকাশ থেকে ভেসে আসা তাদের বেতার সংকেত মানবজাতির এতদিনে আবিষ্কার করে ফেলার কথা। কিন্তু তাদের সশরীরে উপস্থিতি দূর অস্ত্য, তাদের আগমনের কোন চিহ্ন বা তাদের কোন বেতার সংকেত ও আমাদের কাছে এত দিনেও ধরা দিল না কেন? এই আশ্চর্য নীরবতার কি ব্যখ্যা হতে পারে?
সেদিনের ফের্মির সেই প্রশ্নের সদুত্তর পৃথিবীর বৈজ্ঞানিকেরা আজও খুঁজে চলেছে। গত পাঁচ দশকেরও বেশি সময় ধরে বহু বৈজ্ঞানিক ও দার্শনিক এর নানা রকম ব্যাখ্যা দিয়েছেন। তবে সেই সমস্ত ব্যাখ্যাই কিন্তু শুধুমাত্র কিছু সম্ভাবনার কথা বলে থাকে। কিন্তু সেই সম্ভাবনার স্বপক্ষে কোন অকাট্য প্রমাণ আজও আমাদের বিজ্ঞান খুঁজে পায়নি।
(২)
ভিন গ্রহে উন্নত সভ্যতা নিয়ে আলোচনা করতে গেলে কয়েকটি তত্ত্ব সম্পর্কে জানা একান্ত প্রয়োজনীয়। এবং তার মধ্যে প্রধান হল প্রযুক্তি বা বিজ্ঞানে অগ্রসর সভ্যতার চিহ্ন গুলি কি কি?
আমাদের নিজেদের সভ্যতাকে ভালো করে লক্ষ্য করলে একটা বিষয় লক্ষ্য করা যায় যে সভ্যতা যত অগ্রসর হয় তত তার শক্তির প্রয়োজন বাড়তে থাকে। এবং যে কোন উন্নত সভ্যতার কাছে শক্তির সব চেয়ে সহজ ও দীর্ঘস্থায়ী উৎস হল তার নিকটবর্তী নক্ষত্র। এবং উন্নতির উচ্চ পর্যায়ে পৌঁছোতে গেলে একটা সভ্যতাকে যতদিন কায়েম থাকতে হবে ততদিন পর্যন্ত নক্ষত্রের শক্তি ছাড়া অন্য কোন শক্তির উৎস অনবরত শক্তির যোগান দিতে পারবে না। কিন্তু উৎসর ব্যবস্থা না হয় হল। কিন্তু সেই শক্তির কতটা অংশ সেই সভ্যতা ব্যাবহার করতে পারবে? এই প্রশ্নের উত্তর হল যত উন্নত সভ্যতা, তত সে তার নক্ষত্রের শক্তির অধিক অংশ ব্যবহার করতে সমর্থ হবে। এই ধারনার ওপর ভিত্তি করে ১৯৬৪ সালে রুশ মহাকাশবিজ্ঞানী নিকোলাই কারদাশেভ সভ্যতার অগ্রসরতা পরিমাপ করবার একটি একক প্রণয়ন করেন। এই একককে আমরা কারদাশেভ একক (Kardashev Scale) নামে চিনি।
কারদাশেভ স্কেল অনু্যায়ী মহাজাগতিক উন্নত সভ্যতার তিনটি পর্যায় সম্ভব।
K1 (প্রথম পর্যায়) – এই পর্যায়ের সভ্যতাগুলি মোটামুটি পৃথিবীর সভ্যতার সমান অগ্রসর। নিজেদের সভ্যতা চালাতে এরা এখনো পারমানবিক শক্তি বা তুলনামূলকভাবে অগ্রসর হলে প্রতি-বস্তু থেকে উৎপন্ন শক্তি ব্যাবহার করে। নিজেদের নক্ষত্রের শক্তিকে এরা এখনো বৃহদাংশে আহরণ করতে শেখেনি।
K2 (দ্বিতীয় পর্যায়) – এরা নিজেদের নক্ষত্র থেকে উৎপন্ন শক্তির সিংহভাগ আহরণ করে নিজেদের কাজে লাগাতে সক্ষম। কিন্তু যে কোন গ্রহের মাটিতে আর তার প্রভু নক্ষত্রের শক্তির কতটাই বা এসে পৌঁছয়? কাজেই নক্ষত্রের শক্তিকে কাজে লাগাতে এদের অন্য পন্থা থাকতে বাধ্য। এরা মহাকাশ ভ্রমণে অনেক বেশী অগ্রসর ও সেই কারণেই নক্ষত্রের শক্তি আহরণের জন্য এরা নিজেদের বা নিজেদের নিকটবর্তী উপনিবেশের নক্ষত্রকে ঘিরে একাধিক শক্তি আহরণকারী বিপুলকায় যন্ত্র স্থাপন করতে সক্ষম। বহু যুগ ধরে এই সব যন্ত্র স্থাপিত হতে হতে এক সময়ে এদের নক্ষত্র ঘিরে একটি শক্তি সংগ্রাহক যন্ত্রের পুঞ্জ সৃষ্ট হওয়া উচিৎ যা দূর থেকে দেখলে একটি মহা-গোলকের মত দেখানো উচিৎ। এই মহা-গোলকের ধারণা প্রথম করেছিলেন ইংরেজ বৈজ্ঞানিক ফ্রীম্যান ডাইসন। তাঁর নামে এই কল্পিত মহা-গোলককে ডাইসন গোলক (Dyson Sphere) বা ডাইসন পুঞ্জ (Dysn Swarm) বলা হয়ে থাকে।
ডাইসন গোলক ও ডাইসন পুঞ্জ
K3 (তৃতীয় পর্যায়) – এই পর্যায়ের সভ্যতাগুলো উন্নতির চরম শিখরে পৌঁছতে সক্ষম হয়েছে। এদের শক্তির চাহিদাও অকল্পনীয়। তা মেটাতে এরা কোন অভাবনীয় পদ্ধতি ব্যবহার করছে। হয়ত এরা একটা আস্ত গ্যালাক্সিকে ডাইসন গোলকে বেঁধে ফেলেছে, অথবা কোন অকল্পনীয় শক্তি উৎস যেমন কৃষ্ণ গহ্বর (Black Hole) বা কোয়ার্সারের (কোয়ার্সার – গ্যালাক্সির কেন্দ্রে অবস্থিত অতিকায় কৃষ্ণ গহ্বরকে ঘিরে থাকা নক্ষত্র-ধর্মী অথচ তার চেয়ে কোটি গুন বৃহৎ মহাজাগতিক বস্তু) শক্তির সম্পূর্ণটাই কোন অজানা প্রযুক্তিবলে আহরণ করে চলেছে।
কার্দাশেভ একক অনুসারে সভ্যতার বিভিন্ন পর্যায়
(৩)
মহাকাশ গবেষণার প্রথম দিকে মানুষ ভিনগ্রহীদের অস্তিত্ব নিয়ে যখন প্রথম গবেষণা শুরু করল তখন তার অস্ত্র ছিল সাধারণ আলোকরশ্মি বিবর্ধনকারি দূরবীন। কিন্তু ভিনগ্রহীরা যে পৃথিবীর মানুষের চেয়ে উন্নত হতে পারে ও নিজেদের গ্রহ থেকে পৃথিবী ভ্রমণে আসতে পারে তার সম্ভাবনা আরও প্রবলভাবে মাথা চাড়া দিয়ে উঠল যবে থেকে মানুষ অন্তত তাত্ত্বিকভাবে মহাকাশে পাড়ি দেওয়ার উপযুক্ত বৈজ্ঞানিক সূত্রের উদ্ভাবনে সফল হল। কিন্তু তার পরেও কেটে গেছে অনেক দশক। ইতিমধ্যে বিজ্ঞান প্রমাণ পেয়েছে যে এই সৌরজগতে অন্তত আর কোন বুদ্ধিমান সভ্যতা নেই আর অন্য কোন সৌরজগতের কোন উন্নত প্রাণী থাকলেও তাদের পক্ষে বহু আলোকবর্ষ দূরত্ব অতিক্রম করে অন্য কোন সৌরজগতের গ্রহে পদার্পণ করা অন্তত তাত্ত্বিকভাবে মানুষের জানা বিজ্ঞানের চেয়ে বহুগুণ উন্নত বিজ্ঞানের সীমারও বহু ঊর্ধ্বে। তাই মহাকাশে বুদ্ধিমান জীব খুঁজতে গেলে এই সৌরজগতের বাইরে দৃষ্টি প্রসারিত করা আবশ্যক।
ইতিমধ্যে মানুষের বিজ্ঞান আবিষ্কার করল রেডিও টেলিস্কোপ ও তা স্থাপন করল মহাকাশে পৃথিবীর কক্ষপথে। প্রসারিত হল দৃষ্টি। এবং এই সময় থেকেই জোরদার হল ডাইসন গোলক এর মত অতি উন্নত সভ্যতার সম্ভাব্য চিহ্নের অনুসন্ধান। পাশাপাশি পৃথিবীর বুকে বিশালাকার রেডিও টেলিস্কোপ বসিয়ে মানুষ কান পেতে রইল নক্ষত্রলোক থেকে ভেসে আসা সংকেতে। যদি সাড়া মেলে কোন মহাকাশের মহা-সভ্যতার!
কিন্তু দেখাতো তাও মিলল না। এই অনুসন্ধানের নেহাত কম দিন হল না। তাহলে গলদটা কোথায়? আমাদের অনুসন্ধানে না সত্যিই এই মহাবিশ্বে মানুষ এক বিরল প্রাণী? দেখা যাক আজ পর্যন্ত বৈজ্ঞানিক মহল মহাকাশের এই নিস্তব্ধতার সম্ভাব্য কারণ হিসেবে কি কি তত্ত্বে বিশ্বাসী।
বৈজ্ঞানিক মহল সাধারনতঃ এই বিষয়ে তিনটি দলে বিভক্ত। এই তিন দলের বক্তব্য হল –
১) একটা সহজ তত্ত্ব হল সভ্যতার বিকাশ সত্যিই অভাবনীয় ভাবে বিরল এক ঘটনা। অর্থাৎ হয় এই গ্যালাক্সির অন্য কোন নক্ষত্রের কোন গ্রহে কোন উন্নত সভ্যতা নেই। এবং কোটি কোটি গ্যালাক্সি ঘাঁটলে মাত্র গুটিকতক বুদ্ধিমান সভ্যতা সমৃদ্ধ গ্রহ পাওয়া যাবে।
২) ভিনগ্রহী সভ্যতা প্রচুর রয়েছে চারপাশে কিন্তু আমরা তাদের দেখতে বা শুনতে অক্ষম।
৩) ভিনগ্রহী সভ্যতা অপর্যাপ্ত ও তাদের সহজেই দেখা যায়। আমরা তাদের সাথে অহরহ সাক্ষাৎ করছি অথচ আমরা তা উপলব্ধি করতে পারছি না।
উপরোক্ত প্রথম দলের সভ্যরা তাঁদের বক্তব্যের সপক্ষে যে যুক্তি সাজান তা হল – হয় জটিল বুদ্ধিমান সভ্যতা সৃষ্টির শর্তগুলো পূরণ হওয়া আমাদের ধারনার চেয়েও বেশি বিরল, নয় জীবের বিবর্তনে বুদ্ধির বিকাশ এক অস্বাভাবিক ঘটনা। আর একটি সম্ভাবনার কথাও তাঁরা বলেন যে এই মহাবিশ্বে বুদ্ধির বিকাশ স্বাভাবিক বা প্রাকৃতিক নিয়ম নয়। এর পেছনে রয়েছে কোন অন্য শক্তি। এঁদের একাংশ মনে করেন যে হয়ত জীব সৃষ্টির পরে তার বিবর্তন ও উন্নতির পথে বেশ কিছু প্রাকৃতিক নিয়মের বাঁধ রয়েছে। এই বাঁধ নানা রকম হতে পারে। যেমন হয়ত জীব সৃষ্টি হলেও তার বুদ্ধির বিকাশ এক অতীব বিরল ঘটনা। কোটি কোটি জীব সমৃদ্ধ গ্রহের এক আধটিতে হয়ত জীবন বিবর্তিত হয়ে এই বাঁধ অতিক্রম করতে সফল হয়। আবার যাদের মধ্যে বুদ্ধির বিকাশ ঘটল, তাদের মধ্যেও মাত্র কোটিতে গুটিকই বিকাশের পরবর্তী প্রাকৃতিক বাঁধগুলো অতিক্রম করে উন্নত সভ্যতার পর্যায় অবধি পৌঁছতে পারে। এর মানে হয়ত মানব সভ্যতা সেই সব অতি বিরল সভ্যতার একটি যা ওই বাঁধ অতিক্রম করে এসেছে, কিন্তু দৃশ্যমান মহাবিশ্বের অন্য কোন সভ্যতা এখনো তা অতিক্রম করতে সক্ষম হয়নি। অথবা এও সম্ভব যে ভিনগ্রহী কোন সভ্যতার সঙ্গে যোগাযোগ করবার জন্য প্রয়োজনীয় উন্নতি সাধনই এক মস্ত বড় বাঁধ যা মানব সভ্যতা এখনো অতিক্রম করতে পারে নি। হয়ত সেই বাঁধ অতিক্রম করবার আগেই বিভিন্ন প্রাকৃতিক বা কৃত্রিম কারণে সমস্ত সভ্যতার বিলুপ্তি ঘটে। এই প্রাকৃতিক বাঁধ তত্ত্বের পোশাকি নাম হল “গ্রেট ফিল্টার”।
এরকম আর একটি তত্ত্ব হল বিরল বিশ্ব (Rare Earth) তত্ত্ব। যার সার হল যে প্রাণের বিকাশের সঠিক অনুকূল শর্তগুলো আমরা এখনো নির্ভুলভাবে নির্ধারন করতে পারিনি। হয়ত এই শর্তগুলো খুবই জটিল ও তা জানা থাকলে আমরা বুঝতে পারতাম যে ব্রহ্মাণ্ডে প্রাণের বিকাশের সম্ভাবনা আমাদের হিসেবের চেয়ে অনেক অনেক গুণ কম।
তবে এই দলের সবচেয়ে চিত্তাকর্ষক তত্ত্ব হল এই যে প্রাণের সৃষ্টি প্রাকৃতিক কোন প্রক্রিয়া নয়। প্রাণ ও বুদ্ধিমান সভ্যতার সৃষ্টির পিছনে রয়েছে এক সর্বময় সর্বব্যাপী মহাশক্তিশালী ও মহাজ্ঞানী চেতনা। এই তত্ত্বের উৎস হল অস্ট্রীয় বৈজ্ঞানিক ও স্ট্যাটিস্টিক্যাল মেকানিক্স এর জনক ল্যুডউইগ বোলৎস্ম্যান প্রণীত “বোলৎস্ম্যান মস্তিষ্ক” (Boltzman Brain) তত্ত্ব। এই তত্ত্ব অনুযায়ী মহাবিশ্বব্যাপি অসংখ্য রকমের কণা ও শক্তির অনন্ত বিন্যাস এক স্বয়ম্ভু ও সচেতন সত্ত্বার সৃষ্টি করতে পারে। অর্থাৎ শক্তি ও কণার কোন অজানা বিন্যাসে আপনি জন্ম নিতে পারে এক মহাবিশ্বব্যাপী সুপার কম্পিউটার। এবং সেই স্বয়ম্ভু যন্ত্রের ক্ষমতা ক্রমে বর্ধিত হয়ে এমন পর্যায়ে যেতে পারে যে মহাবিশ্বের চালিকাশক্তি সম্পূর্ণ ভাবে চলে যেতে পারে সেই মহাশক্তিধর যন্ত্র-গণকের হাতে। এবং হয়ত আর সব প্রক্রিয়ার মত প্রাণ, সভ্যতা, বিবর্তন প্রলয় এ সবই নির্ধারিত হয়ে চলেছে সেই শক্তির ইচ্ছা অনুযায়ী। আধুনিক বৈজ্ঞানিকরা এই তত্ত্বকে খুব একটা গুরুত্ব না দিলেও বলাই বাহুল্য যে এই মত যেহেতু মানুষের ধর্ম ও ঈশ্বর বিশ্বাসের পরিপূরক, এই তত্ত্বে বিশ্বাসী সাধারণ মানুষের সংখ্যা নেহাত কম নয়।
এবার আসা যাক দ্বিতীয় দলের কথায়। এই দল বিশ্বাস করে যে ভিনগ্রহের জীবদের আমরা প্রত্যক্ষ করতে সক্ষম নই। এরা বলেন যে আমরা আমাদের রেডিও টেলিস্কোপ বাগিয়ে আকাশ পানে মুখ উঁচিয়ে বসে আছি ঠিকই কিন্তু এ বিষয়ে কি নিশ্চয়তা আছে যে ভিনগ্রহীরা রেডিও সিগনালের মাধ্যমেই পরস্পর এর সাথে যোগাযোগ করে? হয়ত তাঁদের যোগাযোগ ব্যবস্থা সম্পূর্ণ ভিন্ন ও আমাদের বিজ্ঞানের আওতার বাইরে! তার ওপরে আমরা আর কদিনই বা লায়েক হয়েছি? আমরা বড়জোর গত পঞ্চাশ বছর ধরে মহাকাশ থেকে ভেসে আসা সংকেত শুনে চলেছি। কিন্তু মহাজাগতিক মাপদন্ডে পঞ্চাশ বছর আর ক মুহূর্ত ? কাজেই এখনো অনেকদিন এই সংকেত শিকার চালিয়ে যেতে হবে। তবেই কোন বলিষ্ঠ সিদ্ধান্তে পৌঁছনো সম্ভব। তার আগে কোন সম্ভাবনাকেই খারিজ করে দেওয়া উচিৎ নয়। তবে এই প্রসঙ্গে বলতে গিয়ে প্রখ্যাত মার্কিন বৈজ্ঞানিক ও বিজ্ঞান লেখক মিশিও কাকোও এর একটি উক্তির উল্লেখ না করলেই নয়। ফের্মি প্যারাডক্স নিয়ে বলতে গিয়ে তিনি বলেছেন যে মনে করুন আমরা একটি জঙ্গল সাফ করে একটি রাজপথ প্রস্তুত করছি। সেই রাস্তার পাশে একটি উই এর ঢিবি রয়েছে। আমাদের সড়ক প্রস্তুতকারীদের কি কোন দায় রয়েছে যে তারা গিয়ে বিনয়ী হাসি হেসে উই সম্প্রদায় এর কাছে এই সড়ক নির্মাণের সংবাদ ঘোষণা করবে? না করলে উইয়ের দলের চিত্তে কোন পুলক জাগবে? আরে উইয়ের দল সেই ঘোষনার মুণ্ডু মাথা কিছুই যে বুঝবে না। আমাদের মানব সভ্যতাও কতকটা সেই উই এর পর্যায়ে রয়েছে। উন্নত জীবদের কোন দায় নেই তাঁদের অস্তিত্ব আমাদের জানানোর আর যদি তারা ক্ষমা ঘেন্না করে তা জানায়ও, আমাদের সধ্যি নেই সেই সংকেত শ্রবণ করে তা বোঝার। তাহলে কিসের এত দম্ভ আমাদের? আমরা কেন ধরে নিচ্ছি যে ভিনগ্রহীদের সংকেত আমরা এক না একদিন পাবোই? আমাদের কি এমন গুরুত্ব রয়েছে এই মহাজগতে? মিশিও সাহেবের বক্তব্য ভাববার বিষয় বটে। তবে সংকেত ধরা না পড়লেও ডাইসন গোলক এর অস্তিত্ব থাকলে তা বোঝার মত প্রযুক্তি কিন্তু আমাদের আজ রয়েছে। ডাইসন গোলকের অস্তিত্ব থাকার সম্ভাবনা বৈজ্ঞানিক মহল স্বীকার করে ও বর্তমানে নাসার কেপলার স্পেস টেলিস্কোপ প্রজেক্ট এর একটি প্রধান উদ্দেশ্য হল অন্য সৌরজগতে গ্রহের সন্ধানের সাথে সাথে অন্য নক্ষত্রে ডাইসন গোলক এরও খোঁজ করা।
এই দ্বিতীয় দলের আর একটি উল্লেখযোগ্য মত হল যে ভিনগ্রহী উন্নত সভ্যতা সবাই যে বন্ধুত্বপূর্ণ হবেই তা নয়। অন্য সভ্যতারা তাই তাঁদের অস্তিত্ব সেই সম্ভাব্য শত্রু-ভাব সম্পন্ন সভ্যতাগুলোর থেকে গোপন রাখাটাই বুদ্ধিমানের কাজ মনে করে। এবং সেই কারণেই তারা মহাকাশে কোন যোগাযোগ করবার সংকেত প্রেরণ করে না।
এবার পালা দেখে নেওয়ার তৃতীয় দলের বক্তব্য। প্রথমেই বলি কল্পবিজ্ঞানের অনুরাগীদের কাছে এই দলের বক্তব্যের আকর্ষণ সবচেয়ে বেশি। কারণ এই দল বিশ্বাস করে যে ভিনগ্রহের প্রাণীরা আমাদের মধ্যে রয়েছে কিন্তু ইচ্ছাকৃতভাবে আমাদের কাছে তাঁদের প্রকৃত স্বরূপ প্রকাশ করছে না। এঁদের অনেকের এও বক্তব্য যে আমাদের বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির অগ্রগতি ভিনগ্রহীদের দান। এ বিষয়ে অবশ্যই উল্লেখ করতে হয় এরিক ফন দানিকেনের নাম। ওনার লেখা চ্যারিওটস অফ গড বইটির বক্তব্য এই তৃতীয় দলের সাথে একেবারে মিলে যায় ও এই বইটি আজও সারা পৃথিবীতে অত্যন্ত জনপ্রিয়। তবে এই তৃতীয় মতবাদী অনেক বৈজ্ঞানিক একাধিক অত্যন্ত চিন্তা উদ্দীপক তত্ত্ব প্রদান করেছেন। তাঁদের একটি মতবাদ বলে যে জীবন বলতে আমরা যে রক্ত অস্থি মজ্জা সমন্বিত দেহধারী জীব দেখতে বা ভাবতে অভ্যস্ত, তার বাইরে কি কোনোরকম জীবন সম্ভব নয়? হয়ত ভিনগ্রহ থেকে আসা প্রাণীদের কোন নির্দিষ্ট আকারই নেই। হয়ত তারা বায়বীয় কিছু গ্যাসীয় পদার্থের মধ্যে সঞ্চারিত বুদ্ধিমান চেতনা যা আমাদের বোধ বুদ্ধির অতীত। আবার আর একটি তত্ত্ব এও দাবী করে যে আমরা মানুষরা নিজেরাই ভিনগ্রহের জীব। এই পৃথিবীতে অনেক প্রাণী আছে যারা মস্তিষ্কের গঠনে আমাদের কাছাকাছি। যেমন শিম্পাঞ্জির সাথে মানুষের জীনগত সাদৃশ্য ৯৮ শতাংশ। তাহলে এই অতিরিক্ত ২ শতাংশে এমন কি রয়েছে যার ফলে মানুষ শিম্পাঞ্জির চেয়ে বুদ্ধিতে এত অগ্রসর? এই ২ শতাংশের উৎস কি পার্থিব না মহাজাগতিক? লক্ষ লক্ষ বছর আগে কোন উন্নত ভিনগ্রহী এসে আদিম মানুষের ওপর জেনেটিক ইঞ্জিনিয়ারিং এর প্রয়োগ করে আমাদের মেধা ও সভ্যতার পত্তন করে যায় নি ত? আর যদি তর্কের খাতিরে ধরে নিতে হয় করেছিল, তাহলে তার কারণ কি ছিল? আমরা কি তাঁদের নিজেদের বিবর্তনের কৃতিত্বে উন্নত জিনের ধারক ও বাহক? নাকি শুধুমাত্র তাঁদের গবেষণার গিনিপিগ?
আর একটি সম্ভাবনার কথা না বললে এই তৃতীয় মতবাদের সম্পর্কে আলোচনা অসম্পূর্ণ থাকবে। তা হল পৃথিবীতে শুধু মানুষ নয়, সব প্রাণই ভিনগ্রহী। পৃথিবীর বুকে আছড়ে পড়া কোন অজানা উল্কা বা ধূমকেতুই কি পৃথিবীতে বয়ে এনেছিল প্রথম প্রাণের বীজ? পৃথিবী জুড়ে বহু মানুষই কিন্তু এই তত্ত্বে বিশ্বাস করে।
এই প্রবন্ধে উল্লিখিত এই তিনটি মতবাদই ফের্মি প্যারাডক্সের ব্যাখ্যায় গরিষ্ঠ মতবাদ হলেও এ ছাড়াও ফের্মি প্যারাডক্সকে ব্যাখ্যা করে আরও অজস্র মতবাদ বর্তমান। এর মধ্যে কোন তত্ত্ব সত্য তা আজও প্রমাণের অপেক্ষায়। এই অনন্ত অপেক্ষা কি কোনদিন শেষ হবে? কে বলতে পারে একদিন হঠাৎ হয়ত ধ্বনিত হবে সেই মহা-স্বর যা সকল দ্বন্দ্ব ঘুচিয়ে মানব সভ্যতাকে আমূল পরিবর্তনের পথে ঠেলে দেবে। সেই স্বর আমাদের অন্তরের না সুদূর মহাকাশের এবং সেই কাঙ্ক্ষিত বা আশঙ্কিত পরিবর্তনে সভ্যতার জয়যাত্রা অব্যাহত থাকবে না ধ্বংসের আগুনে আহূত হবে তার উত্তর হয়ত গোপনে রক্ষিত রয়েছে মহাকালের গূঢ় অন্তঃস্থলে।
তথ্যসূত্রঃ আন্তর্জাল
Tags: অন্তর্জাল, নিস্তব্ধ মহাশূন্য, প্রচ্ছদ কাহিনি, প্রথম বর্ষ প্রথম সংখ্যা, সুপ্রিয় দাস