প্রফেসর নাটবল্টু চক্র: অমৃতের সন্ধান, না সময়-নষ্ট?
লেখক: ঋজু গাঙ্গুলি
শিল্পী: দেবজ্যোতি ভট্টাচার্য (চিত্রচোর)
প্রফেসর নাটবল্টু চক্র নামটার সঙ্গে পরিচিত নন, এমন বাঙালি পাঠক খুঁজে পাওয়া ভার।
কিন্তু তাঁকে কেন্দ্রে রেখে অদ্রীশ বর্ধন যে কাহিনিগুলো লিখেছেন, তাঁদের মধ্যে ক’টার নাম মনে করতে পারবেন এই মুহূর্তে?
নাম ছেড়ে দিন। নাটবল্টু চক্রর একটা কল্পকাহিনির কথাও মনে করতে পারছেন কি, যেটা পড়ার পরেও রেশ রেখে গেছে মনে–চিন্তায়–আত্মায়?
বাংলায় কল্পবিজ্ঞান সাহিত্যের ভগীরথদের অন্যতম, সায়েন্স–ফিকশনের বাংলা প্রতিশব্দ হিসেবে ‘কল্পবিজ্ঞান’ শব্দের প্রবক্তা, এবং অসংখ্য গল্প–উপন্যাসের রচয়িতা হওয়া সত্বেও অদ্রীশ বর্ধনের সৃষ্ট এই চরিত্রটির নাম উঠলে পাঠকদের একাংশের মধ্যে বিভ্রান্তি, এবং বাকিদের মধ্যে উন্নাসিক বিরক্তি কেন দেখা দেয়, সেটা নিয়ে ভাবতে গিয়ে নিজের মাথায় এই দুটো প্রশ্নই এল।
কিন্তু কেন?
উত্তরটা খোঁজার জন্য আনন্দ পাবলিশার্স থেকে প্রকাশিত “প্রফেসর নাটবল্টু চক্র সংগ্রহ”–র দুটো খণ্ড হাতে তুলে নিলাম। ২০০৮–এর ডিসেম্বরে প্রকাশিত ৮২৮ পৃষ্ঠার হার্ডকভার প্রথম খণ্ড, এবং এপ্রিল ২০১৩–য় প্রকাশিত ৭৩২ পৃষ্ঠার হার্ডকভার দ্বিতীয় খণ্ড মিলিয়ে পাঠকদের কাছে হাজির হয়েছে প্রনাবচ–র যথাক্রমে ৬০টি এবং ৩১টি উপন্যাসোপম থেকে অতিক্ষুদ্র কাহিনি।
ওঙ্কারনাথ ভট্টাচার্যের প্রচ্ছদ ও অলঙ্করণে সুসজ্জিত, আপাতভাবে সুমুদ্রিত শক্ত–মলাটের বইগুলোতেও কিন্তু সব সমস্যা মেটেনি।
প্রথমত, লেখাগুলো আদৌ কালানুক্রমে সাজানো হয়নি। দ্বিতীয়ত, প্রথম খণ্ডে তাতে সামিল করা লেখাগুলোর প্রথম প্রকাশের তথ্য থাকলেও দ্বিতীয় খণ্ডে সেসব কিচ্ছু থাকেনি। প্রথম খণ্ডে আবার একই গল্প দু’বার ছাপা হয়েছে। তৃতীয়ত, এই লেখাগুলোর বাইরেও যে এই চরিত্রটিকে কেন্দ্রে রেখে লেখা একাধিক গল্প–উপন্যাস রয়ে গেছে এবিষয়ে আমি নিশ্চিত।
তবু, যা পেয়েছি তাই নিয়েই পড়তে বসলাম। পড়তে গিয়ে আক্ষরিক অর্থে চক্ষু চড়কগাছ হল, কারণ প্রনাবচ–কে কেন্দ্রে রেখে অদ্রীশ বর্ধন বাংলা ভাষায় যে কত রকমের ভাব ও বিষয় এনেছেন, তা এই বইদুটো না পড়লে ধারণাও করতে পারতাম না।
কল্পবিজ্ঞানের ঠিক কী কী দিক বা টপিক নিয়ে লেখা হয়েছে এই কাহিনিগুলো?
নিচের নীরস টেবিলটা লক্ষ্যনীয়।
ক্রমাংক | বিষয় | গল্পের নাম | লেখার সংখ্যা |
১ | এলিয়েন বা নন–অ্যানথ্রপয়েড লাইফ ফর্ম, অর্থাৎ অ–মানুষিক প্রাণীদের সঙ্গে সাক্ষাৎকার তথা মোকাবিলা | “কালোছায়ার করাল কাহিনি”, “ক্রিস্টাল পুঁথির কাহিনি”, “পাইন বনের প্রহেলিকা”, “ওনারা”, “বেলুন–পাহাড়ের বিচিত্র কাহিনি”, “দাঁতালো”, “গাইয়ে গাছ”, “চাঁড়ালচন্দ্রের ফুঁ”, “বজ্রদন্তী বিভীষিকা”, “হত্যার হাতিয়ার হরমোন”, “পরগাছা”, “কঙ্কালের টংকার”, “সোনা”, “প্রাচীন আতঙ্ক”, “ম্যাটারহর্ন”, “রক্তের মধ্যে বিষ”, “লালাভিচ লাডুকং”, “মানুষ, না যক্ষ”, “মারণ মেশিন”, “চাঁদু মানে চাঁদের জীব”, “রুদ্ররোষ”, “অ্যাকুইলার আস্পর্ধা”, “গাছ”, “ঘাস”, “হলুদ পাহাড়”, “সুবর্ণ–গোলক রহস্য”, “কাঁকড়া”, “মেহগনি জঙ্গলের বিস্ময়”, “ইলেকট্রিক জীবাণু”, “পাথর”, “উড়ন্ত গোলার জ্বলন্ত কাহিনি”, “অপার্থিব ভাইরাস”, “পুষ্পক রথের দেশে”, “তুহিন–তমাল শ্বেত–প্রহেলিকা” (থুলু মিথোস), “ডলফিনের ডাক” | ৩৫ |
২ | ডার্ক ম্যাটার, তথা কসমিক এনার্জি/ম্যাটার | “টেক্কা দিলেন প্রফেসর”, “রঙিন কাচের জঙ্গল”, “ডার্ক এনার্জি”, “ভয়ংকর ভুডু”, “ডক্টর ফুঁ”, “আরব্য আতঙ্ক” | ৬ |
৩ | অ্যান্টিম্যাটার | “কালো চাকতি” | ১ |
৪ | হারানো সভ্যতার কিংবদন্তি | “আটলান্টিস–এর সন্ধানে”, “আটলান্টিক–লেমুরিয়ার রহস্য”, “প্রজাপতি, ম্যমি ও সংকেত”, “ত্রিভুজ রহস্য”, “জীবন্ত পাথর”, “আশ্চর্য রশ্মি”, | ৬ |
৫ | পৃথিবীর গভীরে থাকতে পারে এমন কিছু | “কালো থাম”, “সাগর দানব”, | ২ |
৬ | জিনগত বা শারীরিক পরিবর্তন | “মনের মেশিন”, “মলিকিউল মানুষ”, “বৈজ্ঞানিক কুমারটুলি”, “ধুরন্ধর ধরের ধড়িবাজি”, “কসমিক কুয়াশা”, “সাগর বিভীষিকা সাংকোপাঞ্জা”, “নস্যি আর ডক্টর মাথামোটা”, “অ্যানড্রয়েড আতঙ্ক”, “অণিমা–মানুষ”, “ক্রিস্টাল কটেজ”, “ডক্টর ফুটুনি”, “স্ট্রিং”, “ভূত সাম্রাজ্য”, “স্ট্রিং–ভূত”, “অদৃশ্য অবতার”, “সময়–সিন্দুক”, “নব কলেবরে নাটবল্টু”, “রাজা র্যাটের রহস্য”, “টেরা ইনকগনিটো”, “ভয়ংকরদের দ্বীপ”, “কাঁকড়া কারখানার দ্বীপে”, “কেমিক্যাল এক্স”, “মারক মৌমাছি”, “শয়তান উদ্যান” | ২৪ |
৭ | ইচ্ছাপূরণ | “ঈশ্বর আছেন”, “অমর আরক”, “ভয়ংকর কাচ”, “মকর মল্লিকের মহামন্ত্র”, “বাড়ির নাম ব্যাবিলন”, “কঙ্গোর বঙ্গোবাবা”, “তেজস্ক্রিয় মণিক”, “দজ্জাল দর্পণ”, “যদি”, “অলৌকিক ইন্টারনেট”, “টাইম–ভিশন”, “ভূত–গ্রহ”, “আশ্চর্য সংবাদপত্র” | ১৩ |
৮ | ব্ল্যাক হোল | “ব্ল্যাক হোল–এর ব্ল্যাক ম্যাজিক” | ১ |
৯ | সময় ভ্রমণ | “সোনা আর চুনির শহর”, “পুষ্পকের পরিণতি”, “সময়–গাড়ি” | ৩ |
শুধু এই টেবিল থেকে বোঝা যাবে না, কিন্তু বিজ্ঞান বা কল্পবিজ্ঞানের প্রচলিত থিমের বাইরে অজস্র কিংবদন্তি, লোকায়ত ভাবনা, এবং কঠোর পর্যবেক্ষণলব্ধ তথ্যও ঠাসা রয়েছে এদের মধ্যে।
কিন্তু, সাহিত্য হিসেবে লেখাগুলো কেমন?
বিশুদ্ধ জঁর ফিকশনের জগতেও প্রফেসর নাটবল্টু চক্রর এই অ্যাডভেঞ্চারগুলো নিয়ে উপযুক্ত আলোচনা বা চর্চা না হওয়ার জন্য তিনটে কারণ আছে বলে আমার ধারণা, আর সেগুলো হল:
(১) প্রথম খণ্ডের ভূমিকায় অদ্রীশ বর্ধন নিজেই বলেছেন, “ছোটোদের মন জয় করতে গেলে, সুগারকোটেড ট্যাবলেটের মতন তেঁতো ওষুধ খাইয়ে দিতে গেলে, হাসিঠাট্টা কৌতুক পরিহাসের মোড়কে বৈজ্ঞানিক অ্যাডভেঞ্চারের নায়ক হিসেবে খাড়া করেছিলাম শ্রীহীন এক আধবুড়ো ফোকলা এক্কেবারে বাঙালিকে – যার নামকরণ করেছিলাম এমননভাবে যাতে ছেলেমানুষেরা নাম শুনলেই বুঝতে পারে মানুষটা কী নিয়ে যত্তোসব উদ্ভট সৃষ্টিছাড়া ব্যাপারের গবেষণা করে। বাঙালি বৈজ্ঞানিক যে ফ্যালনা নয়, এইটা বোঝানোর সুড়সুড়ি ছিল মনের মধ্যে। একই সঙ্গে বাঙালি ছেলে যে কতখানি ডানপিটে গাছে–চড়া হতে পারে, সে ব্যাপারটাও তুলে ধরার জন্যে দরকার ছিল বোম্বেটে টাইপের মারকুটে দুঃসাহসী একজনকে আনা।
ফলে এসেছে প্রনাবচ আর দীনানা ওরফে প্রফেসর নাটবল্টু চক্র আর দীননাথ নাথ”।
সমস্যা হচ্ছে, এই হাসিঠাট্টা, কৌতুক, আর পরিহাসের কাঠামোর মধ্যে আটকে থাকায় হেঁশোরাম হুঁশিয়ার, তথা “বিরিঞ্চিবাবা” এবং আরো অজস্র লেখায় হাসির খোরাক হিসেবে বর্ণিত বিজ্ঞানীর সঙ্গে প্রফেসর নাটবল্টু চক্র–র তফাৎ পাঠকের দৃষ্টিগোচর হয়নি। প্লাস, লেখাগুলো পড়তে গিয়ে জটিল বৈজ্ঞানিক তথ্য, তত্ত্ব, গুরুগম্ভীর তৎসম শব্দবহুল ভাষ্যের সঙ্গে চরিত্রদের হাস্যকর নাম, এবং অত্যন্ত অসংস্কৃত ও প্রায়শ অমার্জিত ভাষার মিশেল পড়ে একথাই মনে হতে বাধ্য যে, লেখক নিজেই নিজের সৃষ্ট চরিত্রটিকে, বা তাঁর কাণ্ডকারখানাকে সিরিয়াসলি নেননি।
(২) প্রফেসর শঙ্কুর গল্পগুলোকে কল্পবিজ্ঞান না বলে সুখপাঠ্য ফ্যান্টাসি ভাবা হয়, কারণ সেগুলোতে বৈজ্ঞানিক তথ্যের তোয়াক্কা না করে অবিজ্ঞান ও অপবিজ্ঞান প্রায়ই ছোটে অশ্বমেধের ঘোড়া হয়ে। আলোচ্য গল্পগুলোতেও বিজ্ঞান প্রায়শই পিছু হটে গেছে অবিজ্ঞান, অপবিজ্ঞান, আর গাঁজাখুরি ভাবনার কাছে, যাদের প্রকৃষ্ট নিদর্শন হল “ইচ্ছাপূরণ” বর্গভুক্ত গল্পগুলো, যেখানে যা–ইচ্ছে–তাই একটা ধারণাকে কেন্দ্রে রেখে চরিত্র আর ঘটনার জাল বোনা হয়েছে তাদের চারপাশে। তাছাড়া, বেশির ভাগ লেখাই তাদের বাকসর্বস্ব মুখরতা দিয়ে এবং বদলাতে থাকা সময়ের পাঠকের বুদ্ধিমত্তা বা রুচিবোধের তোয়াক্কা না করে হয়ে উঠেছে রীতিমতো দুষ্পাঠ্য। ফলে, যা হবার তাই হয়েছে।
(৩) ষাট–সত্তর দশকে ইন্টারনেট বা অন্য কোনো মাধ্যম না থাকায় উপরোক্ত বিষয়গুলোর মধ্যে অনেকগুলোই ছিল বাংলার পাঠকদের কাছে একেবারে অজানা জগৎ। কিন্তু অ্যাডভেঞ্চার বা রহস্য কাহিনির ধাঁচে বৈজ্ঞানিক তথ্যের পরিবেশন ও তত্ত্বের উন্মোচনের যে মডেলটা দিলীপ রায়চৌধুরী, প্রেমেন্দ্র মিত্র, এবং সিরিয়াস লেখালেখির ক্ষেত্রে অদ্রীশ বর্ধন নিজেও অনুসরণ করেছেন, সেটা প্রনাবচ–র গল্প–উপন্যাসে আদৌ অনুসৃত হয়নি। বরং যেমন–তেমন ভাবে প্রনাবচ–র একটি আবিষ্কারের প্রসঙ্গ এনে বিভিন্ন চরিত্রকে জড়িয়ে তাদের নাম, চেহারা, কথাবার্তা, ভাবনাচিন্তা, ইত্যাদি নিয়ে ইয়ার্কি–ফাজলামি করাটাই এখানে মুখ্য হয়েছে। এই রসিকতাগুলো থেকে প্রনাবচ বা দীনানা নিজেরাও রেহাই পাননি। তাই আসল জায়গায় দুধ কমে চোনা বেড়ে গেছে, ডার্ক ম্যাটার আর সাইকিক এনার্জি একাকার হয়ে গেছে, রোবট–ক্লোন–অ্যান্ড্রয়েড–ভিনগ্রহী সব এক গোত্রের হয়ে গেছে। অথচ প্রাণ, সভ্যতা, তথা ক্ষমতার বিবর্তনের যে গূঢ় দিকগুলো লেখায় স্থান পেয়েছিল, সেগুলো চাপা পড়ে গেছে অলৌকিক আর অতিলৌকিকের নীচে।
একজন নির্মম সম্পাদকের ছাঁকনির মধ্য দিয়ে যেতে হলে এই লেখাগুলো যে আমূল বদলে যেত, তা আমি হলফ করে বলতে পারি। জঁর ফিকশনের অনুবাদের ক্ষেত্রে সর্বোত্তম গুণমানের পরিচয় দেওয়া এই সাধক যে চাইলে প্রনাবচ–কে কেন্দ্রে রেখে বাংলায় কল্পবিজ্ঞানের এক স্বতন্ত্র ও সিরিয়াস আকাশগঙ্গা বইয়ে দিতে পারতেন, তা জানি বলেই আক্ষেপ হয়, কেন সেই আদি যুগেই কেউ তাঁকে চেপে ধরে বললেন না, “সুগারকোটেড ক্যাপসুল নয়, আপনার কাছ থেকে বাংলা ভাষা বলিষ্ঠ, এবং সত্যিকারের বিজ্ঞানভিত্তিক কাহিনি চায়”?
কিন্তু প্রনাবচ আর দীনানা–র ভবিষ্যৎ কি তাহলে ধূলিধূসর বিস্মৃতির অতলে তলিয়ে যাওয়া?
আমার কিন্তু তা মনে হয় না। কারণ, গল্পগুলোর ধরন থেকে সরে এসে, ভাষা বদলিয়ে, পরিবেশ পালটিয়ে, হাসি–ঠাট্টা বর্জন করে ঘটনার ঘনঘটা আর কড়া বৈজ্ঞানিক ভাবনার আমদানি করেও মূল ছকটা কিন্তু পরিত্যক্ত হয়নি। বাঙালি বৈজ্ঞানিক যে ফ্যালনা নয়, আর তার সঙ্গী বাঙালিটি যে রীতিমতো ডানপিটে হতে পারে, সেই কথাটা মাথায় রেখেই আজও বাংলায় কল্পবিজ্ঞান লেখা হয়।
বর্তমানের জন্ম যে দেয়, সে তো শুধু অতীত হয়েই বুক–শেলফের এক কোণে সরে যায় না।
সে হয় ইতিহাস!
Tags: ঋজু গাঙ্গুলী, দেবজ্যোতি ভট্টাচার্য (চিত্রচোর), দ্বিতীয় বর্ষ দ্বিতীয় সংখ্যা, প্রফেসর নাটবল্টু চক্র, প্রবন্ধ
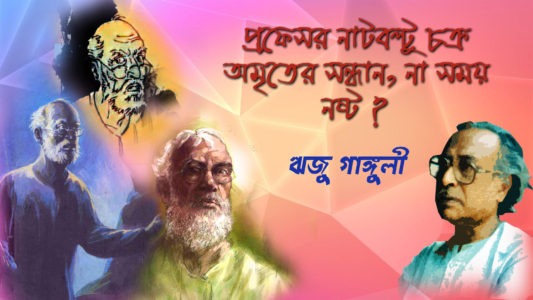

দুর্দান্ত চুলচেরা বিশ্লেষণ এবং সাথে ভগবান কি হতে পারতেন, অথচ কি হলেন সেটিকে যুক্তির অতস-কাঁচ দিয়ে খুব সুন্দর ভাবে তুলে ধরা, লাজবাব!
হীরালালের গল্পটা পড়লে, ইচ্ছে করলে কোন স্তরে যেতে পারত এ সিরিজের গল্পেরা তার একটা হালকা আভাস মেলে। তাহলে কেন প্রতিটি গল্পতে তা নয়? কেন অবহেলার চিহ্ন গায়ে নিয়ে জন্মাল এই জনপ্রিয় সাইফি রূপকথার দল? সম্ভবত, সাহিত্যে সায়েন্টিফিক রিগার, তুলনায় অগভীর বাংলাপাঠকের কাছে কখনই গ্রহনযোগ্য হয় না। সেখানে সামান্যতম গুরুমস্তিষ্কের প্রয়োগ বা স্কুলবুকের বাইরের পড়াশোনার দাবি থাকলে সঙ্গেসঙ্গেই সে লেখাকে “কঠিন”তার তকমা দিয়ে বনবাসে পাঠানোটাই চিরকেলে দস্তুর। হাসি, প্রেম, রাজনীতি ও টি’শপ-সমাজচেতনার বাইরে সাহিত্যকে অন্য গভীরতায় নিয়ে যেতে চাইলে তাকে কঠিনতার তকমা লাগিয়ে তাকে তুলে রাখার ইনস্টিংকট তার মননের গভীরে গাঁথা। এজন্যেই রবীন্দ্রনাথের বহু সিরিয়াস কাজ কম পড়া হয়। ত্রৈলোক্যনাথ বা পরশুরামের হাস্যরসকে নিয়ে (তাত্ত্বিক কিছু কাজ হলেও) জনমানসে সেই হুল্লোড় তৈরি হয় না যা হয় ফেসবুকের একটা হালকা হাসির ওয়েফার জোকে, কিংবা দীর্ঘকাল ধরে সেই জনপ্রিয়তায় থেকে যায় শঙ্কু আর হারিয়ে যায় দিলীপ রায়চৌধুরীর অরিজিনাল কিংবা কুলদারঞ্জনের অনুবাদ সাইফি। হয়ত এই কারণেই সসাঙ্গপাঙ্গ ত্রিদেব এবিসি যখন সেইসব অসামান্য সাইফির জন্ম দিয়ে চলেছে ইংরিজি ভাষায় সে সময়ে বাংলায় লিখতে বসে এইসব রূপকথার জন্ম দিতে হয়েছে শক্তিমান কলমদের। নইলে এ গল্পগুলোও হারিয়ে যেত। একজন লেখকের পক্ষে নিজেকে পাত্রের মাপে এইভাবে বামন বানিয়ে রাখা যন্ত্রণাদায়ক বটে, কিন্তু অস্তিত্ত্বের প্রশ্ন অনেকসময়েই তাঁকে তা করতে বাধ্য করে তোলে। কবজির জোর থাকলেও কমলকুমার বা জগদীশ গুপ্ত বা চিত্ত ঘোষাল হবার মত হবার মত কলজের জোর বেশি লোকের নেই।
খুব সুন্দর বিশ্লেষণাত্মক রিভিউ। আমি সামান্য যে কটা প্রফেসর নাটবল্টু চক্র পড়েছি, তাতে আমারও একই রকম অনুভূতি।
কিছু ব্যতিক্রম বাদে ব্যক্তিগতভাবে অদ্রীশ বর্ধনের মৌলিক লেখা আমাকে সেভাবে টানেনি কোনদিন। এর দুটো কারণ, এক ভাষার আড়ষ্টতা, দ্বিতীয়, অনেক সম্ভাবনাময় লেখার অন্যমার্গে যাত্রা। নাটবল্টু চক্রের ব্যাপারে ঋজুবাবুর সংগে সহমত। সেই তুলনায় ইন্দ্রনাথ রুদ্র অনেকাংশে সফল। কিন্তু বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে প্রনাবচ এবং দীনানা থেকে যাবেন সংগত কারণেই।
ঋজুর লেখা নিয়ে এই পোস্ট ও সকলের বক্তব্য দেখে আমারও দু-চার কথা বলতে ইচ্ছা হল। প্রথমেই বলি, কল্পবিশ্বের সম্পাদক মণ্ডলীর লক্ষ্যই ছিল সংখ্যাটিতে অদ্রীশ বর্ধনকে যত রকম ভাবে সম্ভব এক্সপ্লোর করা। তাই ঋজুর এই লেখাটি আমরা ছাপার সিদ্ধান্ত নিই। লেখাটি সম্পর্কে আমাদের মত, ঋজুর লেখাটি অত্যন্ত সুলিখিত । তিনি যা বলতে চেয়েছেন, সেটি স্পষ্ট করে বলতে পেরেছেন। তাই লেখাটির অনেক অংশের সঙ্গে সম্পূর্ণ একমত না হয়েও আমরা লেখাটি এই সংখ্যায় প্রকাশ করতে সম্মত হই। তা ছাড়া, আগেই বলেছি আমাদের উদ্দেশ্য অদ্রীশ বর্ধনকে এই সংখ্যায় যত রকম ভাবে সম্ভব এক্সপ্লোর করা। এই লেখা একটা অন্য দৃষ্টিকোণের সঙ্গে পাঠককে পরিচয় করিয়ে দেবে, সেই উদ্দেশ্যেই লেখাটি রাখা।
তবে, একজন সাধারণ পাঠক হিসেবে এই লেখার অনেক বক্তব্যের সঙ্গে আমি একমত নই। সেগুলিও একটু বলতে চাই। প্রথমত, অদ্রীশের নাটবল্টু চক্রের কাণ্ডকারখানা যে ‘উদ্ভট’ হবে, সেটাই কি স্বাভাবিক ছিল না? নামটাই তো লেখকের মনোভাবকে স্পষ্টকরে দেয়। এবং আমার মতে, অদ্রীশের লেখার একটি নিজস্ব সিগনেচার ছিল, যেখানে তিনি উদ্ভটতাকে প্রশ্রয় দিয়েছিলেন। সেই সিগনেচার অবশ্য কারও ভাল নাই লাগতে পারে। সেটা ব্যক্তিগত মত। কিন্তু আমার মনে হয়, আশ্চর্য লার্জার দ্যান লাইফ প্লটকে প্রতিষ্ঠা করতে এই ধরনের ভাষা বেশ সহায়ক।
দ্বিতীয়ত, ঋজু বলেছেন পাঠক কি নাটবল্টু চক্রের একটিও লেখা মনে করতে পারেন। আমি পারি। তাঁর ‘বৈজ্ঞানিক কুমোরটুলি’, ‘অমানুষিকী’ ইত্যাদি আরও অনেক লেখার কথা আমার আজও দারুণ ভাবে মনে আছে। একই ভাবে আরও কয়েকটা লেখার কথা তো বলাই যায়। কিন্তু তাতে লেখাটি অহেতুক দীর্ঘ হবে। মোদ্দা কথা হল, সেই লেখাগুলি তার প্লট ও আনুষঙ্গিক সব দিক থেকেই পাঠক হিসেবে তৃপ্ত করেছিল। কাজেই ঋজুর একটিও লেখা না মনে হবার মতো মনে হলেও আমি ভিন্নমত পোষণ করি। তা ছাড়া, নানা ব্যস্ততার কারণে বহু লেখা আজ আর পুরোপুরি মনেও করতে পারব না। কিন্তু সেই লেখাগুলির মুগ্ধতা আজও আমার সঙ্গে রয়েছে।
আর একটা কথা। অন্য সম্পাদক লেখার বিচার করলে আরও নিখুঁত হতে পারত লেখা, এই কথায় কিন্তু সম্পাদক অদ্রীশকেও নিশানায় এনে ফেলেছেন ঋজু। কিন্তু ঘটনা হল, অদ্রীশ সম্পাদক হিসেবে কেমন, তার অনেক উদাহরণই প্রবীণদের লেখা ও কথা থেকে জেনেছি। প্রসঙ্গত বলি, রণেনবাবুই বলেছেন, তাঁর একেকটা লেখা কীভাবে অদ্রীশের সম্পাদনায় পরিমার্জিত ও পরিবর্ধিত হয়ে অন্যরকম হয়ে যেত। সেই সম্পাদক নিজের লেখার বিষয়ে উদাসীন থাকতেন, এটা কি ঠিক বিচার হল?
শেষে যেটা বলতে চাই, সেটাই বোধহয় সবথেকে বড় কথা। হতেই পারে, নাটবল্টুর অনেক লেখাই আজ আর পড়তে ভাল লাগে না। কিন্তু মাথায় রাখতে হবে, কোন সময়ে দাঁড়িয়ে তিনি এগুলি লিখেছেন। একজন মানুষ ছয়-সাত-আটের দশকে যে কাজটি করেছেন, তাকে এত বছর পরে বিচার করতে আমাদের একটু অন্যভাবে দেখা দরকার। তবে হ্যাঁ, পত্রিকা চালাতে গিয়ে অনেক বেশি লেখার জোগান দিতে হয়েছে। কাজেই কখনও কখনও যে তিনি নিজের প্রতি সুবিচার করেননি, সেটা ঠিক। কিন্তু আমার প্রশ্ন হল, এতটা তাড়াহুড়ো ছাড়াও যাঁরা লেখেন, তাঁদের কারও সব লেখাই কি উতরেছে? তা কি কখনও সম্ভব?
যাই হোক, আপনি ভাল থাকুন ঋজু। নতুন নতুন আরও লেখা লিখুন। শুভেচ্ছা রইল।
প্রনাবচ কেন সেই অর্থে বাঙালি পাঠকের কাছে সমাদৃত হল না সেই বিষয়ে আমিও সহমত পোষণ করি। তবে আমার মনে হয় না অদ্রীশ বর্ধন তাঁর এই সিরিজটিকে অবহেলা করেছিলেন বলে। মনে হয় সচেতনভাবেই এই সিরিজ এবং চরিত্রগুলিকে তিনি এইরকমভাবেই উপস্থাপন করতে চেয়েছিলেন।