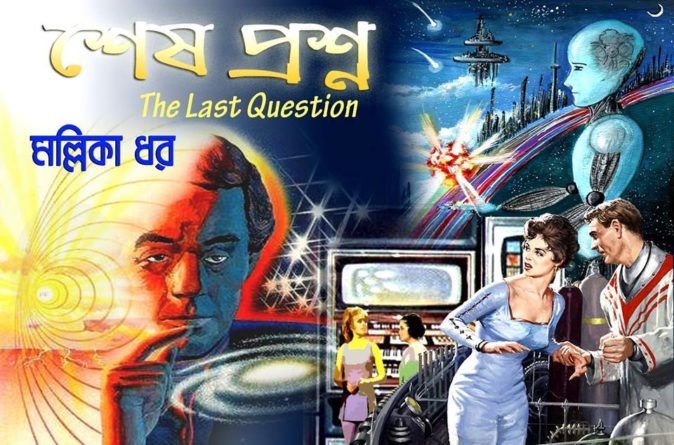শেষ প্রশ্ন
লেখক: মল্লিকা ধর
শিল্পী: দেবজ্যোতি ভট্টাচার্য (চিত্রচোর)
[আইজাক আসিমভের “The Last Question ” গল্পটি পড়ে অবাক হয়ে গেলাম! আশ্চর্য সুন্দর কল্পবিজ্ঞান। ভাবলাম অনেকেই হয়তো পড়েছেন কিন্তু কেউ কেউ যদি না পড়ে থাকেন? তাছাড়া নিজের ভাষায় পড়তে তো ইচ্ছা করে। তাই অনুবাদ করতে বসে গেলাম। সুধীগণ নিজগুণে ক্ষমা করবেন যদি এই দুর্বল কলমে ভালো না আসে, তবে যথাসাধ্য যত্নে কাজটুকু করার চেষ্টা ছিলো। ]
শেষ প্রশ্নটি প্রথম করা হয়েছিল একুশে মে, ২০৬১। মানবসভ্যতা তখন মাত্র সাতদিন হয় আলোতে প্রবেশ করেছে। প্রশ্নটা করা হয়েছিল একটা বাজি ধরাধরির ফল হিসাবে। ঘটনা এইভাবে ঘটে:
অ্যালেক্জান্ডার অ্যাডেল আর বার্ট্রাম লুপভ মাল্টিভ্যাকের দুই বিশ্বস্ত কর্মী। কোনো মানুষ যতদূর ভালো করে জানতে পারে তারা ততদূর ভালো করেই জানতো কয়েক মাইল জুড়ে ছড়ানো দৈত্যাকার কম্পুটার মালটিভ্যাকের ঠান্ডা, মসৃণ, আলোজ্বলানেভা অংশগুলোর আড়ালে কী কী আছে। অন্তত তাদের একটা পরিষ্কার ধারণা ছিলো এর ওভারঅল প্ল্যান, সার্কিট-এইসব বিষয়ে। আসলে টেকনোলজি এত এগিয়ে গেছে আর এত জটিল হয়ে গেছে ততদিনে যে একজন মানুষের পক্ষে ব্যাপারটা পুরোটা বোঝা আর সম্ভবই নয়।
মাল্টিভ্যাক ছিলো নিজের যন্ত্রাংশ নিজে অ্যাসেম্বল করতে সক্ষম আর স্বয়ংসংশোধক। একে এরকম করেই তৈরী করা হয়েছিল, কারণ মানুষ যথেষ্ট দ্রুত আর যথেষ্ট দক্ষতার সঙ্গে এতবড় যন্ত্র সামলাতে পারতো না। অ্যাডেল আর লুপভ মাল্টিভ্যাককে অপারেট করতো বাইরে থেকে, খুবই উপর-উপর। তারা তথ্য প্রবেশ করাতো, প্রশ্ন ঠিক জায়গামতন দিতো, উত্তর তর্জমা করতো। মাল্টিভ্যাক যা করতো তার ক্রেডিট ওরা আর ওদের মতন আরো কর্মীরাই পেতো। নইলে কে আর পাবে? সাধারণ মানুষের কাছে ওরাই ছিলো হিরো!
দশকের পর দশক ধরে মাল্টিভ্যাক স্পেসশিপ ডিজাইন করতে আর গ্রহ উপগ্রহের গতিপথ জানাতে সাহায্য করে গেছে। মাল্টিভ্যাক থাকায় মানুষের চাঁদে, মঙ্গলে, শুক্রে যেতে খুবই সুবিধে হয়েছিলো। কিন্তু তারপরে পৃথিবীর সীমিত সম্পদে টান পড়লো, আর এত সোজা হলো না ব্যাপার। দীর্ঘ মহাকাশ-অভিযানের বিপুল খরচ বহন করা কঠিন হয়ে পড়লো। যদিও কয়লা তেল ইউরেনিয়াম ইত্যাদি ক্রমশ বেশী বেশী এফিশিয়েন্সির সঙ্গেই ব্যবহৃত হচ্ছিল শক্তি উৎপাদনে, কিন্তু এসবই সীমিত যে! কিন্তু কেউ জানতো না, খুব ধীরে ধীরে মাল্টিভ্যাক গভীর এই শক্তিসমস্যার দীর্ঘস্থায়ী সমাধানের দিকে এগিয়ে চলেছিল। অবশেষে ১৪ই মে ২০৬১, মাল্টিভ্যাক সমাধান করে ফেললো। সূর্যের শক্তিকে বশ করে শক্তিসমস্যা মিটিয়ে ফেললো মাল্টিভ্যাক।
সূর্যের শক্তি এসে গেলো হাতের মুঠায়, এ শক্তি সংরক্ষণ ও ব্যবহারোপযোগী করা আর গোটা পৃথিবীগ্রহব্যাপী মানুষের সবরকম ব্যবহারের জন্য ব্যবস্থা করে দেওয়া, সবই করলো মাল্টিভ্যাক। কয়লা, তেল, ইউরেনিয়াম ফিসন ইত্যাদির ব্যবহারের প্রয়োজন আর রইলো না, সরাসরি সবাই যুক্ত হয়ে গেল এক মাইল ব্যাসের এক পাওয়ার স্টেশানের সঙ্গে, যেটা পৃথিবী ঘিরে ঘুরছে পৃথিবীর সঙ্গে চাঁদের যা দূরত্ব তার অর্ধেক দূরত্ব রেখে। গোটা গ্রহের সমস্ত শক্তিচাহিদা মিটতে লাগলো সূর্যের শক্তিতে।
এত বড় একটা ব্যাপার! শক্তিসমস্যার চিরকালীন সমাধান। মাত্র সাতদিনে কি ভরসাফূর্তি-উৎসব ফুরায়? অ্যাডেল আর লুপভের তো নানা সংবর্ধনা-পুরস্কার-পার্টি-নেমন্তন্ন-বক্তৃতার চক্করে পড়ে একেবারে মাথা বোঁবোঁ করে ঘোরার অবস্থা! কোনোরকমে একুশ তারিখে এইসবের খপ্পর থেকে বেরিয়ে ওরা দু’জনে মাটির তলার চেম্বারে চলে গেল। অন্তত এখানে কেউ খুঁজতে আসবে না।
মাল্টিভ্যাকের বিরাট শরীরের কিছুটা অংশ এখানে এই মাটির তলার চেম্বারে দৃশ্যমান, এখন আলো জ্বলানেভা নেই টার্মিনালে, তথ্য প্রবেশও করানো হচ্ছে না, প্রচুর পরিশ্রমের পরে মাল্টিভ্যাকও সাময়িক বিশ্রাম করছে। অ্যাডেল আর লুপভের কোনো ইচ্ছে ছিলো না সেই বিশ্রাম বিঘ্নিত করার। ওরা দুই বন্ধু ও সহকর্মী নিরিবিলিতে দুটো প্রাণের কথা কইতে আর একটু পান করতে এসেছিলো মাত্র। একটামাত্র সুরার বোতল আর দু’খান গেলাস আর বরফ এনেছিলো ওরা।
“ভাবো কি অবাক ব্যাপার!”, অ্যাডেল বললো। ওর চওড়া মুখে কিছু কুঁচকানো বয়সের রেখা, নিজের গেলাসের পানীয় সে আস্তে আস্তে নাড়ছিল কাঁচের সরু রড দিয়ে আর দেখছিলো বরফের খন্ডগুলো কেমন গলে মিশে যাচ্ছে। “ভাবো তো বার্ট, যত চাই তত শক্তি এখন আমরা পেতে পারি। ফ্রী। কি চমৎকার! নয়? ভাবো, এত শক্তি, গোটা পৃথিবীকে মুহূর্তে গলিয়ে দিতে পারে, বাষ্প করে দিতে পারে, কিন্তু তাতেও সামান্যই কমবে শক্তি। চিরকাল, চিরকালের জন্য আমরা পেয়ে গেছি অফুরন্ত শক্তিউৎস।”
লুপভ নিজের মাথাটাকে পাশের দিকে হেলালো। তর্কবিতর্ক করতে শুরু করার আগে এ তার পুরানো স্টাইল। সে এখন একচোট তর্ক করতে চাইছিল অ্যাডেলের সঙ্গে, হয়তো বরফের বাস্কেট আর গ্লাসগুলো বয়ে আনতে ওর মেজাজ একটু চটে গেছিল, নয়তো এমনিই অ্যাডেলের কথায় ভুল ধরতে ওর ভালো লাগে বলে। “চিরকাল? ন্যাহ, অ্যালেক্স। চিরকাল না।” সে বললো।
“প্রায় চিরকাল। যতদিন না সূর্য নিভে যায়।”
“সেটা কি চিরকাল?”
“আচ্ছা, ঠিকাছে, ঠিকাছে। শত শত কোটি বছর। কুড়ি বিলিয়ন বছর। এবারে খুশী?”
লুপভ নিজের আঙুলগুলো মাথার পাতলা হয়ে আসা চুলের মধ্যে আলতো করে চালাতে থাকে, সে প্রায়ই এরকম করে। হয়তো নিজেকে আশ্বস্ত করতে চায় এখনো কিছ চুল আছে, আহা এখনো কিছু আছে। তারপরে মৃদু চুমুক দেয় পানীয়ের গেলাসে, বলে, “কুড়ি বিলিয়ন বছর খুব বড় সময়, কিন্তু চিরকাল তো না।”
“চিরকাল না, কিন্তু আমাদের সময় পার হয়ে যাবে।” অ্যাডেল একটু পরিহাসের সুরে বলে।
“সে তো কয়লা তেল ইউরেনিয়াম দিয়ে চালালেও আমাদের সময় পার হয়ে যেত!”
“ঠিক আছে। মানছি। কিন্তু এখন তো স্পেসশিপকে সোলার স্টেশানে কানেক্ট করে দিয়ে প্রয়োজনীয় শক্তি নিয়ে প্লুটো পার হয়ে চলে যেতে পারবো আমরা। যতবার খুশী আসা যাওয়া করতে পারবো। আগে কি তা পারা যেতো ঐ তোমার কয়লা তেল ইউরেনিয়ামের যুগে? বিশ্বাস না হয় মাল্টিভ্যাককে জিগগেস করো।”
“আমি জানি পারতাম না, এর জন্য মাল্টিভ্যাককে জিজ্ঞাসা করতে হবে না।”
“তাহলে মাল্টিভ্যাকের কৃতিত্ব খাটো করে কথা বলা বন্ধ করো বার্ট। আমাদের জন্য মাল্টিভ্যাক যা করেছে, তা যুগান্তকারী।” খুব তেতে উঠে বললো অ্যাডেল।
“আরে আমি কখন বললাম করে নি? আমি শুধু বলছি সূর্য চিরকাল জ্বলবে না, একসময় ওর জ্বালানী ফুরিয়ে যাবে। এইটুকুই শুধু বলছি। আমরা দুহাজার কোটি বছর নির্বিঘ্নে শক্তি পাবো, তারপরে?” লুপভ তার অল্পকাঁপা তর্জনী সামনের দিকে অ্যাডেলের দিকে নির্দেশ করে, বলে,”বোলো না তখন আরেকটা তারার সঙ্গে কানেক্ট করে দেবো।”
খানিকটা সময় নীরবতা। কেউ কোনো কথা বলে না। অ্যাডেল নিজের গেলাস মুখে তোলে আর নামায়। লুপভের চোখ বুজে আসে। তারা বিশ্রাম করে।
হঠাৎ লুপভের চোখ খুলে যায়, সে বলে, “অ্যালেক্স তুমি ভাবছো আরেকটা তারার সঙ্গে আমাদের পাওয়ার স্টেশন জুড়ে দেবে যখন আমাদের সূর্য নিভে যাবে। ভাবছো না?”
“আমি কিছু ভাবছি না।” অ্যাডেল বলে।
“অবশ্যই ভাবছো। তুমি লজিকে খুব দুর্বল। সেটাই তোমার প্রধান সমস্যা। তুমি সেই গল্পের লোকটার মতন, বৃষ্টি এসেছে দেখে দৌড়ে যে বাগানে ঢুকে একটা গাছতলায় দাঁড়িয়েছিলো। সে একটুও দুশ্চিন্তায় পড়েনি, সে ভেবেছিল একটা গাছ যখন পুরো ভিজে যাবে তখন সে দৌড়ে আরেকটা গাছের তলায় যাবে। হা হা হা। যেন বাকী গাছগুলো শুকনো থাকবে।”
“আচ্ছা, বুঝেছি বার্ট। এত চিৎকার করতে হবে না তোমার। আমাদের সূর্য যখন নিভে যাবে বাকী তারাগুলোও ততদিনে নিভে যাবে।”
“ঠিক তাই।” লুপভ আস্তে আস্তে বলে। “সবকিছুর সৃষ্টি সেই মহাজাগতিক বিস্ফোরণ না কি বলে, সেই বিস্ফোরণে। সবকিছু নিভে যাবে যখন সব তারা নিভে যাবে জ্বালানী শেষ করে। কিছু কিছু তারা খুব বড়, তারা ঝটপট জ্বালানি শেষ করে, দৈত্যাকার তারাগুলো মাত্র কয়েক কোটি বছরের মধ্যেই শেষ হয়ে যায়। সূর্য মাঝারি ভরের, সে আস্তে আস্তে জ্বালানি খরচ করে। কুড়ি বিলিয়ন বছর সে জ্বলবে। আরো ছোটো বামন তারাগুলো হয়তো কয়েকশো বিলিয়ন বছর টিঁকবে। কিন্তু তারপরে? ট্রিলিয়ন বছর পরে? সব অন্ধকার! এনট্রপি ক্রমাগত বাড়তে থাকে, তাকে কখনোই উলটোবাগে ঘোরানো যায় না। এনট্রপিকে সর্বোচ্চে পৌঁছাতে হবে, সেটাই মহাবিশ্বের অনতিক্রম্য নিয়ম।”
“আমি জানি এনট্রপির নিয়মের কথা।” অ্যাডেল বলতে চেষ্টা করে যথাসম্ভব গাম্ভীর্য বজায় রেখে।
“জানোই তো।”
“তুমি যা জানো তা আমিও জানি বার্ট।”
“তাহলে তো জানোই। জানোই যে সবকিছুই একদিন নিভে যাবে। সব তারা, সব শক্তি উৎস। কোনো উৎসই চিরদিনের নয়।”
“ঠিক আছে। কে বলেছে যে নিভবে না?”
“তুমি। তুমি বলেছ গবেট অ্যালেক্স। বলেছ আমরা পেয়ে গেছি শক্তি চিরকালের জন্য। বলেছ চিরকালের জন্য। বলো নি?”
অ্যাডেল এইবার প্রতিবাদ করতে চেষ্টা করে, বলে,” হয়তো কোনোদিন, হয়তো দূর ভবিষ্যতে আমরা বানাতে পারবো তেমন শক্তিউৎস যা ফুরাবে না।”
“কখনো না।” লুপভ কঠোর গলায় বলে।
“কেন নয়, বার্ট? এখনকার কথা বলছি না, ভবিষ্যতে প্রযুক্তির উন্নতি হবে অনেক, তখন। আমাদের হাতে তো আছেই কুড়ি বিলিয়ন বছর।”
“কখনো পারবো না। কেউ কোনোদিন পারবে না।”
“বার্ট, মাল্টিভ্যাককে জিগ্গেস করো।”
“তোমার ইচ্ছে হলে তুমি জিগ্গেস করো গবেট। আমি জানি। পাঁচ ডলার বাজি। যাও, জিগ্গেস করো মাল্টিভ্যাককে।
অ্যাডেলের তখন নেশা ধরে এসেছে। সে এগিয়ে গেল। তখনও খুব মারাত্মক নেশা না, সে কীবোর্ডে টাইপ করতে লাগলো নির্দিষ্ট সিম্বলগুলো, ঠিকভাবেই। প্রশ্নটা দাঁড়ালো এরকম: মানবজাতি কি কোনোদিন কোনো শক্তিখরচ না করে, জ্বালানি ফুরিয়ে নিভে যাওয়া সূর্যকে আবার ফিরিয়ে আনতে পারবে তার জ্বলন্ত যৌবনে? সরলতর ভাবে বললে প্রশ্নটা ছিলো: মহাবিশ্বের মোট এনট্রপি কি ব্যাপক আকারে কমানো সম্ভব?
মাল্টিভ্যাক প্রশ্ন গ্রহণ করে চুপ করে গেল। একেবারে নীরব। জ্বলানেভা আলোগুলোও থেমে গেছে, ক্লিক ক্লিক শব্দও থেমে গেছে।
অনেকক্ষণ পরে, যখন ভীত সন্ত্রস্ত এই দু’জন আর পারছে না টেনশন নিতে, তখন মাল্টিভ্যাক সক্রিয় হয়ে উঠলো। উত্তর লিখে দিল মাল্টিভ্যাক, “তথ্য অপ্রতুল, এই প্রশ্নের সঠিক জবাব দেবার মতন তথ্য এখনো অপ্রতুল।”
“বাজি খতম।” লুপভ ফিসফিস করে বলে। তারা দু’জনে সেখান থেকে দ্রুত চলে যায়।
পরদিন তারা জেগে ওঠে মাথাব্যথা আর মুখে তেতো-তেতো ভাব নিয়ে, আগের রাতের সেই প্রশ্নের কথা বেমালুম ভুলে যায়।
(২)
জেরোড, জেরোডিন আর জেরোডেট ১ এবং জেরোডেট ২ তাকিয়েছিলো ভিজিপ্লেটের নক্ষত্রঠাসাঠাসি চলমান ছবির দিকে। তারা হাইপারস্পেসের মধ্য দিয়ে এসেছে বলে ব্যপারটা তাৎক্ষণিক, কোনো সময় ব্যয় না করেই তারা এসে গেছে তাদের গন্তব্যে। তারা-ঠাসাঠাসি চলচ্চিত্র হারিয়ে গিয়ে এবারে ভিজিপ্লেটের মাঝামাঝি স্থির হলো উজ্জ্বল গোল থালার মতন তাদের গন্তব্য তারাটি।
“ঐ যে এক্স-২৩”, জেরোড বলে।
“ওর গ্রহজগতেই আমরা যাচ্ছি।” জেরোডের গলায় আত্মবিশ্বাসের সুর বেশ প্রকট, সে তার হাত দু’খানা পিঠের দিকে দিয়ে এক হাত দিয়ে আরেক হাত শক্ত করে ধরে আছে, এত জোরে যে আঙুলগুলো সাদাটে দেখায়।
ছোট্টো দুই মেয়ে জেরোডেট ১ আর জেরোডেট ২ এইবারই প্রথম হাইপারস্পেসে ভ্রমণ করলো, তারা বেশ উত্তেজিত। প্রথমবারের মতন তারা পেয়েছে সেই মাথাগোলানো গা-গোলানো সেই অভিজ্ঞতা, সেই যে একটা মুহূর্ত যখন মনে হয় শরীরের ভিতরের সবকিছু বাইরে আর বাইরের সবকিছু শরীরের ভিতরে।
সেই সময়টা কেটে গেছে, বাচ্চা দু’জন এখন খুশীতে লাফালাফি করছে আর একজন আরেকজনকে তাড়া করছে তাদের মায়ের চারপাশে গোল হয়ে ঘুরতে ঘুরতে। “আমরা এক্স-২৩ এ এসে গেছি, এসে গেছি, এসে গেছি…..” তারা চিৎকার করে বলে সমস্বরে ।
“এই শশশ, চুপ, সোনামণিরা, চুপ “, জেরোডিন মেয়েদের থামায়, জেরোডের দিকে ফিরে বলে, “তুমি ঠিক বলছো তো জেরোড?”
“একদম ঠিক, মানুষের ভুল হতে পারে কিন্তু মাইক্রোভ্যাকের ভুল হয় না।”
তারা দুজনেই তাকায় তাদের হাইপারস্পেসশিপের ছাদ বরাবার চলে যাওয়া সরু ধাতব অংশটির দিকে, ছাদের একপ্রান্ত থেকে শুরু হয়ে অন্যপ্রান্তে এসে হারিয়ে গেছে। ওরা শুধু জানে ওটার নাম মাইক্রোভ্যাক, কিভাবে ওটা কাজ করে তার প্রায় কিছুই জানে না। ঐ মাইক্রোভ্যাকই তো এই হাইপারস্পেসশিপের গতিপথ নিয়ন্ত্রণ করে, হাইপারস্পেসে ভ্রমণের সমীকরণ সমাধান করা আর হিসেবগুলো গণনা করা-সবই করে মাইক্রোভ্যাক। ওর শক্তির সরবরাহ আসে সাব-গ্যালাকটিক পাওয়ারস্টেশন থেকে। জেরোড আর তার পরিবারকে শুধু হাইপারযানের আরামদায়ক ঘরে অপেক্ষা করা ছাড়া আর কিছুই করতে হয় না।
ভিজিপ্লেটের দিকে চেয়ে জেরোডিনের চোখ ঝাপসা হয়ে আসে হঠাৎ, সে খুব অপ্রস্তুত হয়ে চোখ মুছতে থাকে। জেরোড বলে, “কি হলো?”
জেরোডিন চোখ মুছতে মুছতে বলে, “কিজানি কেন এমন হয়। পৃথিবী ছেড়ে চলে এসেছি ভাবলেই পৃথিবীর জন্য মনকেমন করে।”
“কেন? কিসের জন্য? সেখানে কি আছে আমাদের?” জেরোডের গলা শুকনো আর অনাবশ্যক কঠিন। “এক্স-২৩ এ আমরা সবকিছু পাবো। তাছাড়া আমরাই তো প্রথম না, ওখানে এখন লাখ লাখ লোক। ইতিমধ্যেই এত লোক ওখানে বসতি করে ফেলেছে, বুঝলে? এই হারে চললে আমাদের নাতিপুতিদের আবার বেরোতে হবে নতুন নক্ষত্রের গ্রহজগতে বসতি করতে কারণ ততদিনে এক্স-২৩ একেবারে ভরে যাবে।”
একটুক্ষণ চুপ করে থাকে সে, তারপরে আস্তে আস্তে বলে, “জেরোডিন, দ্যাখো আমাদের ভাগ্য কত ভালো, মাইক্রোভ্যাক আমাদের এই আন্ত:-নাক্ষত্রিক ভ্রমণের সব হিসাব করে দিয়েছে। নইলে যে হারে আমাদের জনসংখ্যা বেড়েছে, এইরকম না হলে কি হতো ভাবতে পারো?”
জেরোডিন ফিসফিস করে বলে, “জানি, আমরা গোটা মানবজাতি শেষ হয়ে যেতাম। আমাদের বাঁচিয়েছে মাইক্রোভ্যাক।”
“তবে? ভাগ্যকে ধনবাদ দাও জেরোডিন।”
ছোট্টো জেরোডেট-১ জেরোডের কাছে এসে লাফাতে লাফাতে বলে, “আমাদের মাইক্রোভ্যাক সব্বার সেরা। তাই না বাবা?”
জেরোডেট১ এর ঝুঁটিতে হালকা নাড়া দিয়ে জেরোড হেসে বলে, “হ্যাঁ, সোনামণি।”
নিজস্ব একটা মাইক্রোভ্যাক থাকা যে কি আরামের অনুভূতি সে জেরোড জানে। তার বাবার আমলে এইসব ছিল বিরাট, মাইলমাইল ছড়ানো দৈত্যাকার যন্ত্র। মাটির তলার টানেলে রাখা থাকতো সে জিনিস। গোটা পৃথিবীতে একটাই ছিল, প্রত্যেক গ্রহের জন্য একটা করে। এক হাজার বছর ধরে এদের সাইজ শুধু বাড়তেই থাকছিলো, তারপরে হঠাৎ এলো যাকে বলে বৈপ্লবিক পরিবর্তন। ট্রানজিস্টরের জায়গায় এলো আণবিক ভালভ, আকার গেল অনেক কমে, এখন তো তা মাইক্রোভ্যাক, স্পেসশিপেই হেসেখেলে ধরে যায়।
জেরোড বেশ একটা আত্মসন্তুষ্টিতে ভোগে যখন সে ভাবে তার এই ছোটো ব্যক্তিগত মাইক্রোভ্যাক সেই বিরাট মাইল মাইল টানেলে রাখা যন্ত্রের তুলনায় কত বেশী জটিল! সেই প্রাচীন মাল্টিভ্যাক যা কিনা সূর্যের শক্তিকে বশ করেছিলো প্রথম তার থেকে কত জটিল! আর তারপরে সেই যন্ত্র যা কিনা প্রথম হাইপারস্পেসে ভ্রমণের জটিল সমীকরণ সমাধান করেছিলো, তার থেকে কত জটিল!
জেরোডিন নিজের মনের জটিল অলিগলিতে হারিয়ে গেছিল, সে নিজের মনে মনে কথা বলার মতন বললো, “কত তারা, কত গ্রহ! আমাদের মতন কত পরিবার এভাবে হয়তো যাবে সেসব গ্রহে ভবিষতে! চিরকাল যাবে, নতুন নতুন গ্রহে।”
জেরোড হেসে বলে, “চিরকাল না। একসময় সব থেমে যাবে। তবে কিনা বহু বিলিয়ন বছরের আগে না। তারাগুলোকে একসময় তো নিভে যেতে হবেই, এনট্রপি তো বাড়তেই থাকে কেবল, কমে না। তাই একসময় সব তারাই নিভে যাবে।”
জেরোডেট২ কাছিয়ে আসে, জিজ্ঞাসা করে, “বাবা, এনট্রপি কি?”
জেরোড বলে, “সোনামণি, এনট্রপি হলো….. ইয়ে এনট্রপি হলো গিয়ে একটা কথা যা কিনা বোঝায় সবকিছু একদিন পুরানো হয়ে যায়, তারপরে আর চলে না। এই যে যেমন তোমার কথাবলা রোবট, নতুনবেলা চলে, কথা বলে-তারপরে পুরানো হয়ে যায় আর একসময় আর চলে না।”
“নতুন পাওয়ার-ইউনিট ভরে দিলে আবার তো চলে কথাবলা রোবট!”
“হ্যাঁ তো! ঠিক। আমার সোনামণির বুদ্ধি আছে! কিন্তু আমাদের এই বিরাট জগতের পাওয়ার-ইউনিটগুলো কি? ঐ তারারা। যখন ওগুলো নিভে যাবে, আমাদের আর পাওয়ার-ইউনিট কোথায় তখন?”
এই অবধি শুনে জেরোডেট১ কেঁদে ফেলে, চিৎকার করে বলে, “বাবা, ওদের নিভতে দিও না, নিভতে দিও না। তারাদের নিভে যেতে দিও না।”
জেরোডিন রেগে যায়, “দ্যাখো তো কি করলে!” মেয়েকে কোলে তুলে নিয়ে চোখ মোছাতে মোছাতে বলে, “ইশ, কাঁদে না সোনা।”
তারপরে জেরোডের দিকে ফিরে বলে, “তোমার কি আক্কেলবুদ্ধি হবে না? কি দরকার ছিলো ঐসব এনট্রপি ফেনট্রপি নিয়ে বলার? এতটুকু টুকু বাচ্চা, এখনই কি ওরা পন্ডিত হবে?”
জেরোড থতমত খেয়ে গেছে, কোনোক্রমে বলে, “আরে আমি কিকরে জানবো বাচ্চারা ভয় পেয়ে যাবে?”
জেরোডেট১ ফোঁপাতে ফোঁপাতে বলে, “মাইক্রোভ্যাককে জিজ্ঞাসা করো বাবা, ওকে জিজ্ঞাসা করো কেমন করে নিভে যাওয়া তারা আবার জ্বালানো যায়।”
জেরোডিন বলে, “হ্যাঁ, শিগগীর। উফ এ দেখি আরেকজনও কাঁদতে শুরু করেছে। আয় মামণি, কোলে আয়, কাঁদে না, এই দ্যাখ তোদের বাবা এখুনি মাইক্রোভ্যাককে জিগ্গেস করবে।”
জেরোড তাড়াতাড়ি বলে, “এই যে মামণিরা, এক্ষুনি জিগ্গেস করছি মাইক্রোভ্যাককে। কাঁদে না সোনারা, দ্যাখ ঠিক ও বলে দেবে আমাদের।”
জেরোড মাইক্রোভ্যাককে প্রশ্নটা জিগ্গেস করে, তাড়াতাড়ি সঙ্গে জুড়ে দেয়, “উত্তর ছাপিয়ে দাও।”
উত্তর ছাপানো পাতলা সেলুফিল্মের ফালিটা হাতে নিয়ে জেরোড আনন্দিত গলায় বলে, “দ্যাখো মিষ্টিমণিরা, আমি কী বলেছিলাম? মাইক্রোভ্যাক বলেছে সে সবকিছু ঠিক করে দেবে। যখন সময় আসবে সে সব ঠিক করে দেবে।”
জেরোডিন মেয়েদের বলে, “এখন শুতে চলো সোনারা। ঘুমের সময় হলো। কাল আমরা আমাদের নতুন বাড়ীতে যাবো, কত মজা হবে। চলো এখন শুতে চলো।”
জেরোড পাতলা ফিল্মটাকে নষ্ট করার আগে আরেকবার চোখ বুলায়, তাতে লেখা ছিলো, “তথ্য অপ্রতুল, এই প্রশ্নের সঠিক জবাব দেবার মতন তথ্য এখনো অপ্রতুল।”
কাধ ঝাঁকিয়ে সে ফিল্মটা ট্র্যাশক্যানে ছুঁড়ে দেয়, ভিজিপ্লেটে তখন এক্স-২৩ আরো বড়, আরো স্পষ্ট। কাল তারা নতুন গ্রহে পৌঁছাবে, নতুন জীবন, নতুন দিন তাদের সামনে।
(৩)
লামেথ এর ভি জে ২৩এক্স তার হাতে ধরা ত্রিমাত্রিক ম্যাপটার দিকে তাকিয়েছিল, এটা মিল্কি-ওয়ে গ্যালাক্সির ম্যাপ। সে বললো, “আমার কেমন যেন লাগছে রিপোর্টটা লিখতে। এইটা কি এত গুরুত্বপূর্ণ?”
নাইক্রনের এমকিউ ১৭ জে বলে, “গুরুত্বপূর্ণ, অবশ্যই গুরুত্বপূর্ণ। আপনি তো জানেন এই হারে কলোনাইজেশন চললে গ্যালাক্সি ভরে যাবে আর মাত্র পাঁচ বছরের মধ্যেই।”
এই দু’জন, ভি জে ২৩এক্স আর এম কিউ ১৭জে দেখতে তরুণ, মজবুত আর ধারালো দীঘল চেহারা।
ভি জে ইতস্তত করে বলে, “আমি জানি। তবু। এমকিউ, এরকম একটা নিরাশার রিপোর্ট লিখতে হাত সরছে না আমার।”
“কিন্তু লিখতে তো হবেই। একটু আধটু মুচড়ে পালটিয়ে দিলেও শেষপর্যন্ত বলতেই হবে।”
ভি জে দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলে, “স্পেস অসীম, অনন্ত। একশো বিলিয়ন গ্যালাক্সি রয়েছে, তার বেশীও হতে পারে।”
“একশো বিলিয়ন বা তার বেশী মোটেই অসীম না, আর কলোনাইজেশন হতে থাকলে ক্রমেই কমতে থাকবে খালি গ্যালাক্সি। ভেবে দেখুন, কুড়ি হাজার বছর আগে মানুষজাতি প্রথম নক্ষত্রের শক্তিকে সরাসরি ব্যবহার করতে শিখলো তাদের প্রাচীন প্রিমিটিভ মালটিভ্যাক এর সহায়তায়। কয়েক শতক পরে আন্ত:-নাক্ষত্রিক অভিযান সম্ভব হলো। মানবজাতির এক মিলিয়ান বছর লেগেছিল একটা ছোট্টো গ্রহকে প্রথম ভর্তি করে ফেলতে। তারপরে মাত্র পনেরো হাজার বছরে গ্যালাক্সির বাকীটা তার দখলে এসে গেছে। এখন জনসংখ্যা প্রতি দশ বছরে দ্বিগুণ হয় –“
ভি জে কথার মাঝখানেই বলে, “অমরত্বের সৌজন্যে।”
এম কিউ বলে, ” মানছি অমরত্বের ব্যাপারটা একটা জটিল সমস্যা। কিন্তু এইটা তো মানবেন যে এটাকে পাশ কাটানো যাবে না। গ্যালাক্টিভ্যাক আমাদের কত সমস্যা সমাধান করে উপকার করেছে, কিন্তু মৃত্যু-সমস্যা মিটিয়ে ফেলে আগের বাকি সব সমাধান নয়ছয় করে ফেলেছে।”
অদ্ভুত হেসে ভি জে বলে, “অমরত্ব! কী সাংঘাতিক সমস্যা! কিন্তু ভেবে বলুন তো, আপনি কি নিজের জীবন সাধ করে ছেড়ে দিতে চান?”
এম কিউ চট করে উত্তেজিত হয়ে বলে, “না না, কিছুতেই না।” তারপরে কিছুটা শান্ত হয়ে বলে, “আরে আমার কথা আসছে কেন? আমার এখনো বেশী বয়স না। যদি কিছু মনে না করেন ভি জে, আপনার বয়স কত?”
“আমার এখন দু’শ তেইশ বছর চলছে। আপনার?”
“আমার এখনো দু’শই হয় নি। ঠিক আছে, কাজের কথায় আসা যাক। প্রতি দশবছরে জনসংখ্যা দ্বিগুণ হয়। এই গ্যালাক্সি ভরে গেলে তার পাশেরটা ভরে যাবে দশ বছরে। আর দশ বছর, আরো দুটো গ্যালাক্সি। আর এক দশক, আরো চারটে। এইভাবে একশো বছরে এক হাজার গ্যালাক্সি। হাজার বছরে এক মিলিয়ন। দশ হাজার বছরে সমস্ত গ্যালাক্সি শেষ। তারপরে?”
ভি জে বলে, “তারপরে আছে যাতায়াতের খরচ। কত সানপাওয়ার ইউনিট যে লাগবে একেক জনকে একেক গ্যালাক্সি থেকে আরেক গ্যালাক্সিতে যেতে, কে জানে।”
“ঠিক বলেছেন, খুব গুরুত্বপূর্ণ পয়েন্ট এটাও। ইতিমধ্যেই বছরে দুইখানা সানপাওয়ার ইউনিট করে লাগছে মানবজাতির।”
“আরে তার বেশীটাই তো অপচয়। বছরে এমনি এমনি জ্বলে শেষ হয়ে যাচ্ছে হাজার সানপাওয়ার ইউনিট, শুধু আমাদের গ্যালাক্সিতেই। কি করবেন? প্রাকৃতিক ব্যাপার!”
“মানছি তাও। কিন্তু যদি একশো পারসেন্ট এফিসিয়েন্সিও থাকতো, তাও তো একসময় সরবরাহ ফুরাতো। এমনিতেই শক্তিচাহিদা জনসংখ্যার চেয়েও দ্রুত বাড়ে। আমরা গ্রহণযোগ্য গ্যালাক্সি ফুরানোর অনেক আগেই ফুরিয়ে ফেলবো আমাদের শক্তি-উৎস। খুব ভালো একটা দিক তুলে ধরেছেন আপনি, ধন্যবাদ ভি জে।”
ভি জে বলে, “আন্ত:নাক্ষত্রিক গ্যাস থেকে নতুন তারা বানাতে হবে আমাদের।”
এম কিউ হাসে, বলে, “যে শক্তি ছড়িয়ে যায় তার পুরোটা উদ্ধার করা যায় না।”
ভি জে খড়কুটা আঁকড়াবার মতন বলে, “হয়তো কোনো উপায় আছে এনট্রপি উল্টোদিকে ঘুরিয়ে দেবার, গ্যালাক্টিভ্যাক বলতে পারবে।”
ভি জে ঠিক সিরিয়াসলি বলে নি, কিন্তু মুহূর্তের মধ্যে এম কিউ পকেট থেকে বার করে আনলো কনট্যাক্ট ক্রিস্টাল, রাখলো সেটা সামনে টেবিলে, বললো, “তবে এখুনি জিগ্গেস করা যাক গ্যালাক্টিভ্যাককে।”
এম কিউ বলে, “আমারও অনেকদিন থেকেই এই কৌতূহল। একদিন না একদিন মানুষজাতিকে তো এই প্রশ্নের উত্তর খুঁজতেই হবে।”
টেবিলের উপরে রাখা কন্ট্যাক্ট ক্রিস্টালটার দিকে শান্ত দৃষ্টিতে চেয়ে থাকে সে, দুই ইঞ্চি লম্বা, দুই ইঞ্চি চওড়া আর দুই ইঞ্চি উচ্চতার নিখুঁত ঘনক একটি, হাইপারস্পেসের মধ্য দিয়ে জুড়ে আছে গ্যালাক্টিভ্যাকের সঙ্গে। কী অদ্ভুত আশ্চর্য ব্যাপার! এইটুকু জিনিসটা মুহূর্তের মধ্যে ঐ সুবিশাল গ্যালাক্টিভ্যাকের সঙ্গে জুড়ে যেতে পারছে!
এম কিউ মাঝে মাঝে কল্পনা করতে ভালোবাসে তার বিরাট অমর জীবনে সে কখনো সুযোগ পাবে নাকি গ্যালাক্টিভ্যাকের দেখা পাবার। সে নাকি একটা ভিন্ন জগৎ, সেখানে নাকি অচিন্তনীয় উপায়ে চলছে তথ্যের আদানপ্রদান। পুরানো আণবিক ভালভের জায়গা নিয়েছে সাব-মেসনিক স্রোতোধারা, মাকড়সার জালের মতন ছড়িয়ে আছে বলরেখারা, বেশীরভাগ অংশই আছে হাইপারস্পেসে, যেটুকু অনুভবগ্রাহ্য ত্রিমাত্রিক জগতে আছে সেটুকুও নাকি হাজার মাইল!
এম কিউ ১৭-জে হঠাৎ করে ঝুঁকে পড়ে কন্ট্যাক্ট ক্রিস্টালের দিকে, জিজ্ঞাসা করে, “গ্যালাক্টিভ্যাক, এনট্রপির বেড়ে চলা কী উল্টোদিকে ঘুরিয়ে দেওয়া যাবে কোনোদিন?”
ভি জে ২৩-এক্স শুনে চমকে ওঠে, প্রায় আঁতকে ওঠা গলায় সে বলে, “আহ, এ কি জিগ্গেস করলেন? আমি ঠিক একথা বলতে চাই নি তখন।”
এম কিউ বলে, “কেন নয়? প্রশ্নটা তো ভালো প্রশ্ন।”
“আরে সবাই জানে এনট্রপি উল্টোদিকে ঘুরিয়ে দেওয়া যায় না। ধোঁয়া আর ছাই থেকে গাছ বানানো যায় না।”
“এখনো গাছ আছে আপনাদের ওখানে?” এম কিউ কৌতূহলী হয়ে বলে।
ভি জে কিছু বলে না, চুপ করে চেয়ে থাকে ক্রিস্টালটার দিকে। হঠাৎ নীরবতার বুক ফুঁড়ে বেরিয়ে আসে কোমল সুন্দর একটা স্বর, গ্যালাক্টিভ্যাকের গলা, ক্রিসটাল কন্ট্যাক্ট থেকে, সে বলছে, “তথ্য অপ্রতুল, এই প্রশ্নের সঠিক জবাব দেবার মতন তথ্য এখনো অপ্রতুল।”
মানুষ দু’জন শুনে শান্ত হয়, ফিরে যায় তাদের রিপোর্ট লেখায়। গ্যালাক্টিক কাউন্সিলে রিপোর্ট দাখিল করতে হবে তাদের, সময় বেশী নেই।
(৪)
জীপ্রাইমের মন নতুন গ্যালাক্সিটার অসংখ্য তারার দিকে চেয়ে থাকে, এখান থেকে তারাগুলি মিহিন বালিচুর্ণের মতন লাগে। এই গ্যালাক্সিটা আগে দেখে নি জীপ্রাইম, সবগুলো কী সে কোনোদিন দেখতে পাবে? কত কত গ্যালাক্সি, মহাশূন্যে ছড়িয়ে আছে তাদের নিজের নিজের মানুষদের নিয়ে। মানুষদের দেহগুলো কেবল নানা নক্ষত্রের গ্রহে গ্রহে রয়ে গেছে, মনগুলো মুক্ত হয়ে মহাশূন্যে বিচরণ করছে। এই যেমন জীপ্রাইমের মন ঘুরে বেড়াচ্ছে এখানে, এই নতুন গ্যালাক্সিটার কাছে।
ঘুরে বেড়াচ্ছে তার মন, অমর শরীর রয়েছে তার আপন গ্রহে। এখন সকলেরই এরকম। শরীরগুলো যুগযুগ ধরে হিমকক্ষে ঘুমিয়ে আছে, জীবনরক্ষার প্রক্রিয়া যন্ত্রের নিয়ন্ত্রণে, ত্রুটিহীন নিখুঁত যত্নে আছে দেহগুলি। মাঝে মাঝে, খুব বিরল যদিও, কেউ কেউ জেগে ওঠে, স্বাভাবিক জীবনযাপন করে কিছুদিন, আবার ঘুমিয়ে পড়ে হিমকক্ষে গিয়ে। নতুন মানুষের জন্ম খুব বিরল হয়ে গেছে, আর তার দরকারই বা কি? এমনিতেই অমর মানবদল মহাবিশ্ব ভরে আছে, নতুনরা যদি ক্রমাগত আসতে থাকে, তাদের জন্য যথেষ্ট জায়গা কোথায়? তারচেয়ে এই ভালো।
জীপ্রাইম নিজের চিন্তার জলে ডুবে গেছিলো, হঠাৎ ভেসে উঠলো, কাছে এসেছে আরেকটি মন। তার মন সক্রিয় হয়ে উঠলো পরিচয়ের জন্য। “আমি জীপ্রাইম, আপনি?”
উত্তর এলো, “আমি ডীসাবইয়ুন। আপনি কোন্ গ্যালাক্সি থেকে?”
জীপ্রাইম বলে, “আমরা আমাদের গ্যালাক্সিটাকে শুধু গ্যালাক্সি ই বলি। আপনারা আপনাদেরটাকে কি বলেন?”
“আমরাও। মনে হয় সব মানুষই তাদের গ্যালাক্সিকে শুধু গ্যালাক্সিই বলে। আর বলবে নাই বা কেন?”
“ঠিকই। কেনই বা বলবে না। সবই তো সমান।”
“না, সব গ্যালাক্সি এক না কিন্তু। কোনো একটা গ্যালাক্সিতে মানুষের উদ্ভব হয়েছিল একদিন।”
জীপ্রাইম মহাশূন্যে দৃষ্টি ছড়িয়ে দিয়ে বলে, “কোন্ গ্যালাক্সি সেটা?”
ডীসাবইয়ুন বলে, “আমি তো জানি না। কিন্তু ইউনিভ্যাক বলতে পারবে।”
জীপ্রাইমের মন কৌতূহলে জ্বলজ্বল করে ওঠে, “জিজ্ঞাসা করি ওকে?”
ইচ্ছাপ্রকাশমাত্র জীপ্রাইমের অনুভব ছড়িয়ে যেতে থাকে, ছড়িয়ে যেতে থাকে কোটি কোটি গ্যালাক্সিভরা মহাবিশ্বে। আহা, বিন্দু বিন্দু রত্নের মতন মহাবিশ্বের গভীর বুকে ছড়িয়ে আছে কোটি কোটি নক্ষত্রজগৎ, একেকটি কয়েকশো বিলিয়ন নক্ষত্র ধারণ করে। কত শতসহস্র কোটি মানুষ ঘুমিয়ে আছে বিলিয়ন বিলিয়ন গ্রহে, কত শত সহস্র কোটি মন ঘুরে বেড়াচ্ছে মহাশূন্যে। তবু এই সমুদ্রতীরে বালুকণার মতন ছড়িয়ে থাকা অসংখ্য গ্যালাক্সিদের মধ্যে একটা অনন্য, সেখানে মানবজাতির সূচনা হয়েছিলো কোন্ বহু পুরাতন যুগে। একটা সময় ছিলো যখন শুধু সেখানেই মানুষ ছিলো, অন্য সব গ্যালাক্সিতে তখন মানুষের চিহ্নও ছিল না।
জীপ্রাইমের কৌতূহল তার ধৈর্যকে ছাড়িয়ে যায়, সে বলে, “ইউনিভ্যাক, বলতে পারো কোন্ গ্যালাক্সিতে মানুষের উদ্ভব?”
ইউনিভ্যাক শুনলো, কারণ জগতের প্রতিটি স্থানেই তার গ্রাহকযন্ত্র রয়েছে, হাইপারস্পেসের মধ্য দিয়ে সেগুলো পৌঁছেছে মূল ইউনিভ্যাকে। মূল ইউনিভ্যাক ঠিক কোথায় আছে, তা বোঝা আজ আর কারুর পক্ষেই সম্ভব না। জীপ্রাইম শুধু একজনকে জানতো যার মন ইউনিভ্যাকের খুব কাছে গেছিলো, অনুভবযোগ্য দূরত্বে, সে তাকে বলেছিলো সে কেবল একটা উজ্জ্বল গোলক দেখেছে, মাত্র ফুট দুয়েক ব্যাসের একটা জ্বলজ্বলে গোলক। জীপ্রাইম অবাক হয়ে ওকে জিগ্গেস করেছিল, “মাত্র এইটুকু? এইটুকু জিনিস কিকরে ইউনিভ্যাক হতে পারে?” সে ওকে বুঝিয়ে বলেছিল, “ইউনিভ্যাকের প্রায় সবটাই আছে হাইপারস্পেসে, সেটা কিরকম তা আমরা বুঝতে পারবো না, আমরা যে ত্রিমাত্রিক, দৈর্ঘ প্রস্থ উচ্চতার জগতে সীমাবদ্ধ। হাইপারস্পেস আমাদের কল্পনারও বাইরে।”
সত্যি, আর বুঝতে পারা সম্ভব না। সেদিন চলে গেছে যখন মানুষ কিছুটা বুঝতে পারতো, ছুঁতে পারতো, দেখতে পেতো তাদের সরলসোজা মালটিভ্যাক বা মাইক্রোভ্যাককে। এমনকি গ্যালাক্টিভ্যাকের সময়ও কনট্যাক্ট-ক্রিস্টাল দেখা যেতো, ছোঁয়া যেত। কিন্তু এখন সবই হাইপারস্পেসে। যন্ত্র নিজে নিজে ক্রমাগত উন্নতি ঘটিয়ে গেছে নিজের, জটিল থেকে জটিলতর হয়েছে, পূর্বতন যন্ত্র তার সমস্ত তথ্যের উত্তরাধিকার দিয়ে গেছে নতুনতরকে। মিলিয়ন বছরের বিবর্তনে আজকে এসে এমন জায়গায় পৌঁছেছে তার আদিনির্মাতারা কল্পনাতেও আনতে পারেনি।
ইউনিভ্যাক জীপ্রাইমের প্রশ্ন শুনতে পেয়ে সেইমত তার চিন্তাকে সংহত করে দিল। কোটি কোটি গ্যালাক্সির মধ্যে একটির উপরে এসে তার মন স্থির হলো। বিন্দুর মতন দেখতে পাওয়া গ্যালাক্সি বড় হয়ে উঠতে লাগলো, তারাগুলো স্পষ্ট হলো। এবারে ইউনিভ্যাকের চিন্তা ভেসে এলো, অসীম দূর থেকে ভেসে এলো অসাধারণ স্পষ্ট হয়ে, ইউনিভক বললো, “এই হলো সেই গ্যালাক্সি যেখানে মানুষের উদ্ভব।”
জীপ্রাইম দেখলো সেটা একইরকম দেখতে, তেমন কোনো বিশেষত্ব নেই। একটু হতাশ হলো সে, ভেবেছিলো কোনো দারুণরকম কিছু দেখবে বুঝি। নিজের হতাশাকে সে লুকাতে চেষ্টা করে।
ডীসাবইয়ুন কাছেই ছিলো, সেও দেখছিলো। একটা তারার দিকে নির্দেশ করে সে ইউনিভ্যাককে জিগ্গেস করে, “আর ঐ তারাটা? ওটাই বুঝি মানুষের সূচনাগ্রহের জীবনতারা?”
ইউনিভ্যাক বলে, “না, মানুষের সূচনা যে গ্রহে হয়েছিল, সেই গ্রহজগতের কেন্দ্রতারাটি অনেক আগেই নোভা হয়ে বিস্ফোরিত হয়ে গেছে। এখন সেটা একটা শ্বেতবামন তারা।”
“আর মানুষগুলো? তাদের কি হলো?” জীপ্রাইম এত হতচকিত হয়ে গেছে যে সে আর কিছু ভাবতে পারছে না ভালো করে, প্রশ্নটা একেবারে স্বতস্ফূর্তভাবে বেরিয়ে এসেছে।
ইউনিভ্যাক বললো, “মানুষগুলোর জন্য নতুন জগত তৈরী করে দেওয়া হয়েছে, তাদের অমর দেহগুলো সেখানে নিরাপদে আছে।”
“হ্যাঁ, তা তো ঠিকই, তাতো ঠিকই। ভুলে গেছিলাম।” জীপ্রাইম তাড়াতাড়ি বলে, কিন্তু গভীর একটা বেদনা তার মনের খুব ভিতরে চারিয়ে যেতে থাকে, হারিয়ে ফেলার বেদনা। সে মন সরিয়ে নেয় মানুষের সূচনা গ্যালাক্সি থেকে, সেটা আবার বিন্দুবৎ হয়ে দূরে মহাশূন্যে হারিয়ে যায়। সে আর তা দেখতে চায় না, কোনোদিন না।
ডীসাবইয়ুন অনুমান করেছিলো কিছু একটা, সে জিগ্গেস করে, ” জীপ্রাইম, কি হলো আপনার?”
অবসন্ন-মন জীপ্রাইম বলে,” নক্ষত্রেরা মরে যাচ্ছে। মানুষের সূচনা-নক্ষত্র মরে গেছে। “
“নক্ষত্রের তো মৃত্যু আছেই। সবাই জানে। তাতে কেন আপনি ভেঙে পড়লেন এত?”
“যখন জগতের সব তারা নিভে যাবে, সব কর্মযোগ্য শক্তি শেষ হয়ে যাবে, তখন আমাদের সকলের অমর দেহগুলোও শেষ হয়ে যাবে। কেউ রক্ষা পাবে না ডীসাবইয়ুন, আমি না, আপনি না, কেউ না।”
“তার এখনও অনেক বিলিয়ন বছর দেরি আছে জীপ্রাইম।”
“আমি তা চাই না। বিলিয়ন বছর পরেও না। ইউনিভ্যাক, নক্ষত্রদের কি মৃত্যু থেকে রক্ষা করা যায় না?”
ডীসাবইয়ুন মজা পেয়ে বলে, “মানে আপনি এনট্রপি উলটোদিকে ঘুরিয়ে দেবার কথা বলছেন ? “
ইউনিভ্যাক উত্তর দেয়,” তথ্য অপ্রতুল, এই প্রশ্নের সঠিক জবাব দেবার মতন তথ্য এখনো অপ্রতুল।”
জীপ্রাইমের চিন্তা তার নিজের গ্যালাক্সির দিকে ফেরে, সে ডীসাবইয়ুনের কথা ভুলে যায়, ভুলে যায় তার বহু বিলিয়ন বছরের আশ্বাস, ভুলে যায় তার এনট্রপির নিয়ম মনে করিয়ে দেওয়ানো। দ্রুত নিজের গ্যালাক্সির দিকে ভেসে যেতে থাকে জীপ্রাইম, বিদায় নিয়েও আসে না ডীসাবইয়ুনের কাছে। কোথাকার কে ডীসাবইয়ুন, ট্রিলিয়ন আলোকবর্ষ দূরের কোনো গ্যালাক্সিতে হয়তো ঘুমিয়ে আছে তার দেহ, অথবা হয়তো তত দূরে না, পাশের তারাজগতেই সে ঘুমিয়ে আছে। কিছুতেই কিছু যায় আসে না জীপ্রাইমের। সে চায় না ডীসাবইয়ুনের নিরাশার কথা শুনতে, আহা ন্যাকা, বিলিয়ন বছর বাকী! তারপরে? নেকু, এনট্রপির বেড়ে চলে, তার বেড়ে চলা ঘুরিয়ে কমে চলা করে দেওয়া যায় না। শুনে যেন মনটা তর হয়ে যাবে! বিরক্ত লাগে!
আর্ত ও অবসন্ন মনে জীপ্রাইম আন্তর্নাক্ষত্রিক হাইড্রোজেন সংগ্রহ করতে থাকে, একটা ছোটো নক্ষত্র তাকে বানাতে হবে, যদিও নক্ষত্রেরা মরে যায় তবু হয়তো নতুন কিছু নক্ষত্র বানানো সম্ভব।
(৫)
সব মানুষের মন মিলে এখন এক অতিমানব। বহু কোটি মানুষের মনের সমন্বয়ে এই অতিমানব, সবাই মিলে একজন। বহু কোটি জীবন্ত কোষ মিলে যেমন একটিমাত্র জীবদেহ, তেমনি ট্রিলিয়ন ট্রিলিয়ন মানুষের মন মিলে এই একজন অতিমানব। এইসব মানুষের অমর দেহগুলি সযত্নে ঘুমন্ত আছে গ্রহে গ্রহে, নিখুঁত যান্ত্রিক দেখাশোনায়, এইসব যন্ত্রপাতি স্বয়ংক্রিয়, এরা আছে কস্মিভ্যাকের নিয়ন্ত্রণে। কস্মিভ্যাকের কখনো ভুল হয় না, তাই এইসব যন্ত্রপাতি একেবারে নিখুঁত। বহু বিলিয়ন গ্যালাক্সি ভরা এইসব অজর অমর বহুকোটি মানুষের মন একসাথে মিশে গিয়েই অতিমানব, মুক্ত সেই অতিমানব মহাশূন্যে বিচরণরত।
অতিমানব বলে, ” মহাবিশ্ব শেষ হয়ে আসছে।”
সে তাকায় ক্ষীণ হয়ে আসা গ্যালাক্সিদের দিকে, দৈত্যাকার তারারা সুদূর অতীতেই বিস্ফোরিত হয়ে শেষ হয়ে গেছে, মাঝারি তারারাও আর নেই, এখন প্রায় সব তারাই শ্বেতবামন তারা, নিজস্ব জ্বালানি শেষ, ভিতরে থেকে যাওয়া তাপ আস্তে আস্তে বিকিরণ করতে করতে নিভে যাবার দিকে চলেছে এরা সবাই। মহাবিশ্ব শেষ হয়ে আসছে।
আন্তর্নাক্ষত্রিক ধূলা গ্যাস ইতদি জড়ো করে নতুন নক্ষত্র তৈরী হয়েছে অনেক, কিছু কিছু প্রাকৃতিক উপায়েই হয়েছে, কিছু কিছু কৃত্রিমভাবে। সেইসব তারাও জ্বলে জ্বলে শেষ হবার পথে। বহু শ্বেতবামন তারা একসঙ্গে পিষ্ঠ করে নতুন নক্ষত্র তৈরী হয়েছে, কিন্তু ওভাবে বেশী হয় না। প্রতি হাজারে একটা বড়োজোড়। সেগুলোও শেষ হবার পথে।
অতিমানব বলে, “মহাবিশ্বে এখনো যা শক্তি আছে, খুব ভালোভাবে সতর্কতার সঙ্গে, কস্মিভ্যাকের নির্দেশ অনুসারে ব্যবহার করলে কয়েক বিলিয়ন বছর চলবে। তাও একদিন না একদিন সব শেষ হবেই। এনট্রপিকে সর্বোচ্চে পৌঁছাতে হবে, মহাবিশ্বের অনতিক্রম্য এই নিয়ম। এই নিয়মের কি ব্যতিক্রম সম্ভব? জিজ্ঞাসা করি কস্মিভ্যাককে। “
কস্মিভ্যাক তাদের ঘিরে আছে সবদিক থেকে, কিন্তু এখন এর পুরোটাই হাইপারস্পেসে। এর সামান্য ভগ্নাংশ ও এখন ত্রিমাত্রিক বিশ্বে নেই, সবটাই হাইপারস্পেসে। কস্মিভ্যাক কোনো বস্তু বা শক্তি দিয়ে নির্মিত নয়, বস্তু বা শক্তির ধারণাই আর সেখানে চলে না। এই অতিমানবও কিছুই জানে না কস্মিভ্যাকের, কিভাবে তা কাজ করে কিরকম তার আকারপ্রকার, এসব ব্যপারগুলো অতিমানবেরও কল্পনার অতীত।
অতিমানব বলে, ” কস্মিভ্যাক, এনট্রপিকে কি রিভার্স করা যায়?”
কস্মিভ্যাক বলে, ” তথ্য অপ্রতুল, এই প্রশ্নের সঠিক জবাব দেবার মতন তথ্য এখনো অপ্রতুল।”
অতিমানব বলে, ” প্রয়োজনীয় তথ্য সংগ্রহ করো।”
কস্মিভ্যাক বলে, ” করবো। আমি এই কাজ করে চলেছি একশো বিলিয়ন বছর ধরে। আমি আর আমার পূর্বতন যন্ত্রেরা সকলেই এর উপরে কাজ করে গেছে। তাদের সংগৃহীত সব তথ্য উত্তরাধিকারসূত্রে পেয়েছি আমি। এই প্রশ্ন বহুবার আমাদের করেছে মানুষ, কিন্তু সবসময়েই তথ্য অপ্রতুল ছিল। এই প্রশ্নের সঠিক জবাব দেবার মতন তথ্য এখনো অপ্রতুল।”
অতিমানব বলে, “এমন কি কোনো সময় আসবে যখন এই প্রশ্নের জবাবের মতন যথেষ্ট তথ্য থাকবে? নাকি এই প্রশ্নের সমাধান চিরকালের জন্যই অসম্ভব? “
কস্মিভ্যাক বলে, “কোনো প্রশ্নের সমাধানই চিরকালের জন্য অসম্ভব নয়।”
অতিমানব বলে, “কখন পাবে সমাধানের জন্য যথেষ্ট তথ্য?”
কস্মিভ্যাক বলে, ” তা বলতে পারি না। আমি কাজ করে চলবো।”
অতিমানব বলে, “বেশ। আমরা অপেক্ষায় থাকলাম।”
(৬)
সমস্ত নক্ষত্র আর সব গ্যালাক্সিরা শেষ, মহাবিশ্ব এখন প্রায় পুরোটাই অন্ধকার। দশ ট্রিলিয়ন বছরের জীবন শেষে এখন মহাবিশ্ব চিরনির্বানের দিকে চলেছে।
অতিমানবসত্ত্বা থেকে এক এক করে মানুষমনগুলি মিশে যাচ্ছে কস্মিভ্যাকের সঙ্গে, তাদের আর কোনো ভিন্নতাই রইলো না, তারা এক হয়ে মিশে গেল কস্মিভ্যাকে- যার আকারপ্রকার বিষয়ে কোনো ধারণাই তারা করতে পারতো না, সে শক্তি না বস্তু এই কথাটারই মানে হতো না, আজ তারা তাতেই মিশে যাচ্ছে এক হয়ে। অমর মানবদেহগুলি শেষ হয়ে গেলো বটে কিন্তু তাতে কোনো ক্ষতি আর নেই।
শেষ মানবমনটি কস্মিভ্যাকের সঙ্গে মিলে যাবার আগে একটু থমকে দাঁড়ালো, তাকিয়ে দেখলো তারানেভা, গ্যালাক্সিনেভা অন্ধকার মহাবিশ্বের দিকে, ধীর অথচ নিশ্চিত গতিতে যে পরম শূন্য তাপমাত্রার দিকে চলেছে। এনট্রপি চলেছে সর্বোচ্চের দিকে, অনতিক্রম্য সেই নিয়ম যে নিয়মের কথা কোন আদিযুগ থেকে মানুষকে প্রশ্নার্ত করে রেখেছে।
শেষ মানবমন বললো,” কস্মিভ্যাক, এই কি জগতের শেষ? এই বিশৃঙ্খলা থেকে কি নতুন করে মহাবিশ্ব সৃষ্টি করা যাবে নাকি এইখানেই সব শেষ?”
কস্মিভ্যাক বললো, ” তথ্য অপ্রতুল, এই প্রশ্নের সঠিক জবাব দেবার মতন তথ্য এখনো অপ্রতুল।”
শেষ মানবমন মিলে গেল কস্মিভ্যাকের সঙ্গে, এখন শুধু রইলো কস্মিভ্যাক, সেও হাইপারস্পেসে।
বস্তু আর শক্তি শেষ হয়ে গেল, এমনকি স্পেসটাইমও শেষ। কেবল কস্মিভ্যাক রইলো হাইপারস্পেসে, শেষ প্রশ্নের জবাব না দেওয়া পর্যন্ত তার মুক্তি নেই অস্তিত্ব থেকে। সেই বহুযুগের প্রশ্নটি, দশ ট্রিলিয়ন বছর আগের প্রিমিটিভ মাল্টিভ্যাক যে প্রশ্ন প্রথম শুনেছিল দু’জন মানুষের কাছে, সেই দুজন মানুষের সঙ্গে এই কস্মিভ্যাকে মিলে যাওয়া অতিমানবের যত তফাত, তার চেয়ে বহুগুণ বেশী তফাত সেই মাল্টিভ্যাকের সঙ্গে আজকের কস্মিভ্যাকের। কিন্তু সেই প্রশ্নটি বেঁচে আছে, আজো অমীমাংসিত। বাকী সব প্রশ্নের জবার এসে গেছে, কিন্তু শেষ প্রশ্নটির সমাধান হওয়ার আগে কস্মিভ্যাক মুক্তি পাবে না।
একনিষ্ঠার সঙ্গে কস্মিভ্যাক সংগ্রহ করে চলে তথ্য, একসময় সব তথ্য সংগ্রহ শেষ হয়। এখন এগুলোকে সব ঝাড়াই বাছাই করে সমাধান বার করতে হবে। কেজানে কত যুগের পর যুগ কেটে যায়, জানা যাবে না, কারণ প্রচলিত স্পেসটাইম ই তো নেই আর! একসময় কস্মিভ্যাক পেয়ে যায় উত্তর, সে এনট্রপিকে রিভার্স করার উপায় পেয়ে যায়। কোনো মানুষ নেই, কাকে দেবে সে উত্তর? কিন্তু তাতে কিছু আসে যায় না, মানুষ থাক আর না থাক, এই মহাউত্তর নিজেকে প্রকাশ করবে নিজেই।
হাইপারস্পেসে আরো বহু বহু মহাযুগ অতিক্রান্ত হয়, ভাবতে ভাবতে খুঁজতে খুঁজতে একসময় কস্মিভ্যাক খুঁজে পায় সমাধান প্রকাশের সর্বোত্তম পন্থা, সে ধাপে ধাপে সেইভাবে সবকিছু ঠিকঠাক করে।
উত্তর প্রকাশের মহামুহূর্ত সমাগত হলে কস্মিভ্যাক বলে, “এইবার!!!! “
শেষপ্রশ্নের উত্তর প্রকাশিত হয় মহাবিস্ফোরণে, তীব্র আলোর বন্যা নিয়ে বেরিয়ে আসে নতুন মহাজগৎ।
এতকাল পরে কস্মিভ্যাক চিরবিশ্রামে যায়।
Tags: গল্প, দেবজ্যোতি ভট্টাচার্য (চিত্রচোর), প্রথম বর্ষ প্রথম সংখ্যা, মল্লিকা ধর, শেষ প্রশ্ন