রুপোলি পর্দার যন্ত্রমানব
লেখক: বিশ্বদীপ দে
শিল্পী: মূল প্রচ্ছদ
আশির দশকের মাঝামাঝি যাদের ছেলেবেলা কেটেছে তাদের সকলেরই বোধহয় দুজন কমন বন্ধু (আজকের ফেসবুকের ভাষায় মিউচুয়াল ফ্রেন্ড) ছিল। একজন জনি সোকো। অন্যজন তার উড়ুক্কু রোবট। তখন টিভি বলতে সাদা-কালো, চ্যানেল বলতে দূরদর্শন। টিভির সেই আদ্যিকালের দর্শকদের কাছে জনি সোকো ও তার রোবটের কার্যকলাপ থ্রি-ডির মতোই জ্যান্ত হয়ে উঠত।
জনি সোকো তার হাতঘড়ির কাছে মুখ নিয়ে গিয়ে কিছু আদেশ করলেই রোবট তা পালন করত মুহূর্তে। সমস্ত প্রতিকূলতার বিরুদ্ধে সে ছিল অপরাজেয়। টিভিতে দেখার পর টিউবলাইটের বাক্স হাতের মধ্যে ঢুকিয়ে রোবট সাজার সেই ছেলেবেলা সকলেরই মনে আছে নিশ্চয়ই। আজকের কিশোরদের কাছে অবশ্য সেই সিরিয়াল নেহাতই হাস্যকর ঠেকবে। আশির দশকে কলকাতায় দেখানো হলেও সিরিয়ালটা তারও বহু আগে তৈরি। সেই ষাটের দশকের শেষদিকে। আজকের প্রজন্মের পক্ষে সেই আদ্যিকালের স্পেশাল এফেক্ট হজম করা সত্যি কঠিন। তবু, নিজে সেই সময়ের প্রতিনিধি বলে রোবট নিয়ে লেখার শুরুতে সেই প্রাচীন সিরিয়ালের কাছেই ফিরে যেতে হল।

‘জনি সোকো অ্যান্ড হিজ ফ্লাইং রোবট’। গারগোয়াল গ্যাঙের পাঠানো একের পর এক মনস্টারের সঙ্গে ফ্লায়িং রোবটের ধুন্ধুমার লড়াই বাধত। বলাই বাহুল্য, সেই লড়াইয়ে সব সময় জিতত ফ্লাইং রোবট। এবং অবধারিতভাবে শেষ লড়াইয়ে তার মৃত্যু হয়। যা আমাদের অনেকেরই কাছে প্রথম মৃত্যু-অভিজ্ঞতা। সেদিনের অনেক শিশুরই চোখে জল এসেছিল জনি সোকোর সাধের রোবটের ধ্বংসপ্রাপ্তি দেখে। কিন্তু আজ ভেবে দেখলে মনে হয়, জনি সোকোর ফ্লাইং রোবট আসলে একজন সুপারহিরো মাত্র। ত্রাতা বা অবতারের ঢঙে তার কীর্তিকলাপ আমাদের মুগ্ধ করে রাখত। তার বেশি কিছু নয়। এই তালিকায় ‘রোবোকপ’-কেও রাখা যায়। ‘রোবোকপ’ নাম্নী সাইবর্গের অ্যাকশন ছিল অনবদ্য জমকালো। ছোটবেলায় দারুণ লাগত। কিন্তু পরবর্তী সময়ে দেখা রোবটের অন্যান্য সিনেমাগুলোয় মানুষ ও যন্ত্রের সম্পর্কের রসায়ন নিয়ে যে প্রশ্নগুলো উঠে এসেছে ‘রোবোকপ’ বা ‘জনি সোকো অ্যান্ড হিজ ফ্লাইং রোবট’-এ সে-সব কিছু ছিল না। সেখানে অ্যাডভেঞ্চারই ছিল একমাত্র উপভোগ্য। পরবর্তী সময়ে রজনীকান্তের ‘রোবট’ কিংবা শাহরুখ খানের ‘রা ওয়ান’-ও সেই গোত্রের ছবি। সেখানে আবার রোবট সুন্দরী নায়িকার কোমর জড়িয়ে নাচেও বেশ দক্ষ!

রোবট নিয়ে সত্যিকারের ভালো ছবির কথা বলার আগে বলা যাক যন্ত্রের কথা। যন্ত্রের সঙ্গে মানুষের সম্পর্ক নিয়ে অসাধারণ, বলা চলে রীতিমতো ক্লাসিক ছবি হয়েছে। দুটো ছবির কথা এখুনি মনে পড়ছে, যা বোধহয় সকলেই দেখেছে। একটা চার্লি চ্যাপলিনের ‘মডার্ন টাইমস’, অন্যটা ঋত্বিক ঘটকের ‘অযান্ত্রিক’। মানুষ ও যন্ত্রের সম্পর্কের দুটি আলাদা আলাদা দৃষ্টিভঙ্গি দুটি ছবির বিষয়বস্তু। যদিও ১৯৩৬ সালে নির্মিত চ্যাপলিনের ছবি আরও অনেক কথা বলে। তবু জায়ান্ট মেশিনের ওপর শায়িত লিটল ট্রাম্পের (চ্যাপলিন অভিনীত চরিত্রটি) অনবদ্য ভঙ্গিটির বিশ্ববিখ্যাত চিত্রকল্পটিকে অগ্রাহ্য করার উপায় কই? ঋত্বিকের ‘অযান্ত্রিক’ অবশ্য কেবলমাত্র মানুষ ও যন্ত্রের সম্পর্কের কথাই বলে। ১৯৫৮ সালে নির্মিত এ ছবিতে আরও অনেক চরিত্র এসেছে বটে, কিন্তু শেষ পর্যন্ত তা ট্যাক্সি ড্রাইভার বিমল ও তার সাধের গাড়ি জগদ্দলেরই কাহিনি। বাকি চরিত্ররা কেবল সেই সম্পর্ককে পরিস্ফুট করে তুলতে ব্যবহৃত হয়েছে। বিমলের ভূমিকায় কালী বন্দ্যোপাধ্যায়ের অভিনয়, জগদ্দলের প্রতি তার ভালোবাসা, স্নেহ, অভিমান— বিশ্ব-চলচ্চিত্রের এক মাইলস্টোন। একেবারে শেষ দৃশ্যে যখন ধ্বংস হয়ে যাওয়া জগদ্দলের হর্ন বাজাতে থাকে বাচ্চা ছেলেটি, সেই সময় কালী বন্দ্যোপাধ্যায়ের এক্সপ্রেশন আমাদের কাঁদায়, আবিষ্ট করে। আমাদের একেবারও মনে হয় না এ অশ্রু অকারণ। অথচ মনে হওয়া কি উচিত ছিল না? কেননা, যতই বিমল জগদ্দলকে ‘জ্যান্ত’ মনে করুক, শেষ পর্যন্ত তো সে একটা নিষ্প্রাণ যন্ত্রই!
রোবটের ছবি নিয়ে আলোচনা করতে বসে ‘অযান্ত্রিক’-এর প্রসঙ্গ উত্থাপন অনেকের কাছেই বাড়াবাড়ি মনে হতে পারে। তাদের একটু মনে করিয়ে দেওয়া যাক, বহু বছর পরে নির্মিত একটি ইংরেজি ছবির কথা। হলিউডে নির্মিত জেমস ক্যামেরন পরিচালিত ঝাঁ-চকচকে স্পেশাল এফেক্টের সেই সাই ফাই ছবির সঙ্গে কম বাজেটের সাদা-কালো বাংলা ছবি ‘অযান্ত্রিক’ স্বাভাবিকভাবেই কোনও দিক থেকে মেলে না। তবু ছবির শেষ দৃশ্যে কীভাবে যেন ‘অযান্ত্রিক’ এসে পড়ে। ছবিটির নাম ‘টার্মিনেটর টু’। দশ বছরের বালক জন কোনরের মুখোমুখি টার্মিনেটররূপী আর্নল্ড সোয়ারজেনেগার। মিশন শেষ। কোনরকে হত্যার জন্য যে রোবটটিকে পাঠানো হয়েছিল ভবিষ্যৎ থেকে, তাকে ধ্বংস করেছে কোনরের রক্ষাকর্তা হিসেবে আগত আর্নল্ড। সেও রোবট। কোনরের মা সারার গলায় স্বস্তি ঝড়ে পড়ে, ‘ইট’স ফাইনালি ওভার’। কিন্তু আর্নল্ড তাকে চমকে নিয়ে জানায়, ‘নো, দেয়ার ইজ অ্যানাদার চিপ। অ্যান্ড ইট মাস্ট বি ডেস্ট্রয়েড অলসো।’ তার নির্লিপ্ত ঘোষণায় চমকে ওঠে সারা ও জন। জন বাধা দেয়। কাঁদে। কিন্তু সে কান্নায় আর্নল্ড টলে না। নিজেকে ধবংস করে ফেলার আগে অবশ্য সে ক্রন্দনরত জনকে বলে যায়, ‘আই অ্যাম সরি, জন।’ বলে যায়, ‘আই নো নাউ হোয়াই ইউ ক্রাই। বাট ইট ইজ সামথিং আই ক্যান নেভার ডু।’ গোটা ছবি জুড়েই সে কান্নাকে বুঝতে চেয়েছে। প্রথমবার জনকে কাঁদতে দেখে সে অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করেছিল, ‘হোয়াটস রং উইথ ইওর আইজ?’ পরে জনকে সে জিজ্ঞাসাও করেছিল, মানুষ কেন কাঁদে? জন তাকে বুঝিয়েছিল। কিন্তু সে বোঝেনি। কেননা যতই সে মানুষের মতো হোক, শেষ পর্যন্ত তো সে যন্ত্রই। তার নিজের ভাষায়, ‘আই অ্যাম এ সাইবারনেটিক অর্গানিজম। লিভিং টিস্যু ওভার এ মেটাল এভোস্কোলিটন।… আই হ্যাভ টু স্টে ফাংশনাল আনটিল মাই মিশন ইজ কমপ্লিট।’ কিন্তু ধীরে ধীরে তার নির্লিপ্তির বদল ঘটে। সে বুঝতে পারে অশ্রুর ভাষা। কিন্তু ওই পর্যন্তই। তার নিজের কান্নার ক্ষমতা নেই। ধীরে ধীরে সে মৃত্যুর নীল জলে ডুবে যায়। আর কান্নায় ভেঙে পড়ে জন। আর এখানেই কীভাবে যেন এসে পড়ে ‘অযান্ত্রিক’-এর ট্যাক্সি ড্রাইভার বিমল। সে কেঁদেছিল তার লজঝড়ে জগদ্দলের জন্য। আর জন কাঁদছে তার রক্ষাকর্তা টারমিনেটরের জন্য। দুটো কান্নাই আসলে একই বিন্দুতে দাঁড়িয়ে। যন্ত্রের জন্য মানুষের অশ্রু।
আপাতদৃষ্টিতে ‘রোবট’ শব্দটার মধ্যে একটা যান্ত্রিকতা আছে। অথচ আশ্চর্যের এটাই, সারা পৃথিবী জুড়ে শ্রেষ্ঠ রোবট মুভিগুলির অধিকাংশই কিন্তু যান্ত্রিকতাকে ছাপিয়ে মনুষ্যত্বের কথাই বলে। আসলে রোবটের মধ্যে ফুটে ওঠা মানবিকতা সময়ে সময়ে মানুষের মধ্যে গড়ে উঠতে থাকা যান্ত্রিকতাকেই প্রতিফলিত করে যেন। পাশাপাশি যন্ত্র ও মানুষের দ্বৈরথও বহু ছবির বিষয় হয়ে উঠেছে। এ প্রসঙ্গে যে ছবিটার কথা বলা যেতে পারে তার নাম ‘আই, রোবট’। তবে ছবিটার কথায় যাওয়ার আগে ‘থ্রি ল’জ অব রোবোটিকস’-এর কথা একটু বলা দরকার। তার কারণ এর সঙ্গে সিনেমাটার একটা নিবিড় সম্পর্ক রয়েছে। বিশ্ববিখ্যাত সেই সাই ফাই লেখক আইজ্যাক আসিমভ তাঁর ১৯৪২ সালে লেখা ‘রান অ্যারাউন্ড’ নামের ছোটগল্পতে এই ল-গুলির কথা লেখেন। ল-গুলি হল—
১। একটি রোবট কখনওই একটি মানুষকে আঘাত করতে পারবে না।
২। রোবট সবসময়ই মানুষের দেওয়া নির্দেশ মান্য করে চলবে। কেবলমাত্র তখনই সে তা করবে না যখন সেই নির্দেশের ফলে প্রথম নিয়মটি বিঘ্নিত হয়।
৩। একজন রোবট অবশ্যই নিজেকে রক্ষা করবে। কিন্তু প্রথম বা দ্বিতীয় নিয়মটিকে লঙ্ঘন করে সে তা করতে পারবে না।
‘আই, রোবট’ সিনেমাটিও আইজ্যাক আসিমভের গল্প নিয়েই তৈরি। ‘আই, রোবট’ তাঁর লেখা একটি ছোটগল্পের সংকলন। যদিও সিনেমার গল্পটি সংকলনের কোনও গল্পের সঙ্গেই মেলে না। তবে সব ক’টি গল্পের অন্তঃচরিত্রের সঙ্গে ছবির গল্পের কাঠামোর চরিত্রকে মেলানো যায়।

২০৩৫ সাল। অ্যানথ্রোপোমরফিক রোবটেরা সারা পৃথিবী জুড়ে মানুষের সেবা করছে। তাদের শিখিয়ে দেওয়া আছে যেন তারা ‘থ্রি লজ অব রোবোটিকস’ মেনে চলে। এমতাবস্থায় ‘ইউ এস রোবট’-এর প্রধান রোবোটিসিস্ট ড. অ্যালফ্রেড ল্যানিং নিজের অফিসের জানলা দিয়ে লাফ দিয়ে আত্মহত্যা করেন। ওই জানলা কোনও মানুষের পক্ষে ভাঙা অসম্ভব। তবুও সকলে ওটাকে আত্মহত্যা বলেই মেনে নিয়েছিল। কিন্তু মানলেন না একজন। তিনি গোয়েন্দা ডেল স্পুনার (ভূমিকায় উইল স্মিথ)। একবার তিনি ভয়াবহ গাড়ি দুর্ঘটনার সম্মুখীন হয়েছিলেন। সেই মুহূর্তে এক রোবট এসে স্পুনারকে বাঁচায়। কিন্তু তাঁর বারো বছরের মেয়েকে বাঁচায় না। কেননা সেই মুহূর্তে ‘হায়েস্ট প্রবাবলিটি অব সার্ভাইভাল’ থাকা স্পুনারকে বাঁচানোই রোবটটির কাছে সঠিক বলে মনে হয়েছিল। এই ঘটনার পর থেকেই স্পুনার রোবটদের ওপর তাঁর বিশ্বাস হারিয়েছিলেন। তিনি ল্যানিংকে চিনতেন। দুর্ঘটনায় তাঁর হাত নষ্ট হয়ে যাওয়ায় এই ল্যানিং-ই তাঁর জন্য নির্মাণ করে দিয়েছিলেন ‘রোবোটিক আর্ম’। স্পুনার ল্যানিং-এর মৃত্যু নিয়ে তদন্ত শুরু করলেন, এবং অচিরেই আবিষ্কার করলেন ল্যানিংকে সত্যিই হত্যা করা হয়েছিল। হত্যাকারী এক রোবট, যার নাম সনি। আর তাকে এই হত্যার নির্দেশ দিয়েছিল ওই বিল্ডিংয়ের সুপার কম্পিউটার ভিআইকেআই (ভারচুয়াল ইন্টার অ্যাকটিভ কাইনেটিক ইন্টেলিজেন্স)! ক্রমে আবিষ্কৃত হল এক চাঞ্চল্যকর তথ্য। নব্য নির্মিত রোবটরা রোবোটিকসের কোনও সূত্ৰই মানতে চায় না। তারা মানুষকে বন্দি করে মানবসভ্যতার ওপর কর্তৃত্ব করতে চায়। মানুষদের ভরসা এখন পুরনো রোবটরা। যারা এখনও মানুষদের নির্দেশ মেনেই চলছে। শুরু হয় এক দ্বৈরথ। মানুষ বনাম রোবট।
এই লড়াই আমরা দেখেছি পুরো ‘টার্মিনেটর’ সিরিজ জুড়েই। যেখানে দেখানো হয়েছে ভবিষ্যতে রোবটরা মানুষকে সরিয়ে পৃথিবীর শাসনের অধিকার চায়। আর তাই শুরু হয়েছে এক মহাযুদ্ধ। সেই যুদ্ধে মানুষের অন্যতম নেতা জন কোনর। ভবিষ্যৎ থেকে রোবট পাঠানো হচ্ছে। উদ্দেশ্য কখনও জন কোনরের মা-কে মেরে ফেলা, যাতে সে জনের জন্মই না দিতে পারে (দ্য টার্মিনেটর), কখনও বা বালক জনকেই হত্যা করা (টার্মিনেটর টু, জাজমেন্ট ডে)। কখনও আবার জনের হবু স্ত্রী তাদের আক্রমণের লক্ষ্য (টার্মিনেটর থ্রি, রাইজ অব দ্য মেশিনস)। এবং সব ক্ষেত্রেই মানুষদের তরফ থেকেও পাঠানো হয়েছে রোবট। যাদের মিশন ওই রোবটগুলিকে ধ্বংস করা।
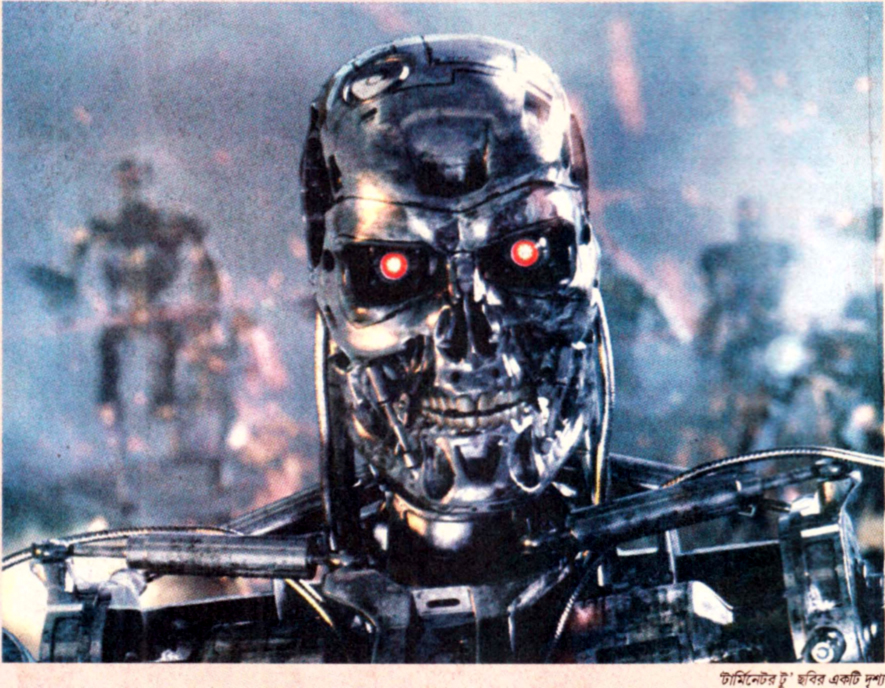
অনেক যুদ্ধবিগ্রহের কথা হল। কিন্তু রোবটকে নিয়ে হওয়া ছবি কেবল ধ্বংসের কথা বলে না। বরং অসংখ্য ছবি তার ঠিক উলটো কথাই বলে। ভালোবাসা, মমত্ব, স্নেহের যে নিবিড় বন্ধন মানুষের মধ্যে থাকে, তেমনটি যে যন্ত্রের সঙ্গেও হয় বা হতে পারে এই সব ছবি যেন সেই কথাই বলে। এই তালিকায় অন্যতম ছবি ‘বাইসেন্টিনিয়াল ম্যান’। ১৯৯৯ সালে নির্মিত ক্রিস কলম্বাস পরিচালিত এই ছবি আইজ্যাক আসিমভ ও রবার্ট সিলভারবার্গের উপন্যাস ‘দ্য পজিট্রনিক ম্যান’ অবলম্বনে তৈরি। যার মূল অবলম্বন ছিল বহু বছর আগে লেখা আইজ্যাক আসিমভের নভেলা ‘বাইসেন্টিনিয়াল ম্যান’। ছবির প্রধান চরিত্র এক অ্যান্ড্রয়েড। তার নাম অ্যান্ড্রু। সে নিছক যন্ত্রমানব নয়। তার মধ্যে রয়েছে আবেগ। শুধু তা-ই নয়, সে একজন শিল্পীও বটে। চমৎকার কাঠের কাজ জানে সে। মার্টিন পরিবারে একজন হাউসকিপার হিসেবে তার আগমন। অচিরেই আবিষ্কৃত হয় তার বিশেষত্ব। সে আর পাঁচটা রোবটের মতো নয় জেনে সেই পরিবারের সকলেই উত্তেজিত হয়। ধীরে ধীরে সে পরিবারের একজন হয়ে ওঠে। অ্যান্ড্রুর কাঠের কাজ রীতিমতো প্রশংসিত হতে থাকে, এবং চড়া দামে লোকে তা কিনতেও থাকে। পরিবারের কর্তা স্যার জেরাল্ড মার্টিন তার নামে একটি ব্যাংক অ্যাকাউন্ট খুলে দেন। সে ক্রমে ধনী হয়ে ওঠে। বেশ কিছু বছর কাটানোর পর অ্যান্ড্রু স্বাধীনতা চায়। স্যার জেরাল্ড তাকে মুক্তি দেন। সে সমুদ্রতীরে এসে বসবাস শুরু করে। কাহিনি কিন্তু এখানেই শেষ নয়। অ্যান্ড্রু ক্রমে অনুভব করে তার দুঃখবোধ আছে, কিন্তু সে কাঁদতে পারে না। সে বোঝে সে মানুষের মতন হলেও মানুষ নয়। শেষ পর্যন্ত সে একজন বিশেষ অ্যান্ড্রয়েড মাত্র, যার মধ্যে আবেগ ও সৃষ্টিশীলতা আছে। অ্যান্ড্রু স্বপ্ন দেখে একজন মানুষ হয়ে ওঠার। ছবির শেষে দেখা যায় মার্টিন পরিবারের মেয়ে পোর্শিয়ার সঙ্গে তার প্রেমের সম্পর্ক স্থাপিত হয়েছে। অবধারিতভাবে এসেছে যৌনতাও। তবে তারা জানে তাদের এই সম্পর্ককে সমাজ মেনে নেবে না। তাই অ্যান্ড্রু আবেদন জানায় ওয়ার্ল্ড কংগ্রেসের কাছে। সে চায় তাকে সমাজ একজন ‘মানুষ’ হিসেবে মেনে নিক। বলা বাহুল্য, তার আবেদন খারিজ হয়ে যায়। স্পিকার জানান, একটি দীর্ঘজীবী যন্ত্র সমাজ মেনে নিতে পারে। কিন্তু একজন ‘অমর মানুষ’ সমাজ মেনে নেবে না। অর্থাৎ যেন পরোক্ষে তাকে বলে দেওয়া হল মৃত্যু না হলে সমাজ তাকে ‘হিউম্যান বিয়িং’-এর স্বীকৃতি দেবে না। ছবির একদম শেষে অবশ্য তাকে মানুষ বলে মেনে নেয় সমাজ। ততদিনে আর বয়স প্রায় দুশো বছর। তার মৃত্যুর পরে অশক্ত পোর্শিয়া তার কানে কানে বলে ওঠে, ‘সি ইউ সুন।’ কর্মদক্ষতা, স্বাধীনতা, প্রেম, যৌনতা, মৃত্যু— এসবের মধ্যে দিয়ে অ্যান্ড্রুর মনুষ্যত্ব লাভের অসাধারণ এই কাহিনি চলচ্চিত্রের ইতিহাসে ক্লাসিক ছবির মর্যাদা পেয়েছে এরই মধ্যে।
আরেক ছবি ‘এডওয়ার্ড সিজারহ্যান্ডস’। পরিচালনায় টিম বার্টন। এডওয়ার্ডের নামভূমিকায় ছিলেন জনি ডেপ। এক পাহাড়ের ওপর নির্জন দুর্গের মধ্যে এডওয়ার্ডের বাস। তার ‘সৃষ্টিকর্তা’ তাকে সম্পূর্ণ করার আগেই মারা যান। সেই থেকে সে একলাই সেখানে থাকে। সে সম্পূর্ণ নয়। তার হাতের জায়গায় লাগানো রয়েছে ছুরি-কাঁচি! যদিও এ ছবি রূপকথার। ঠিক ‘টিপিক্যাল’ রোবট বলা যায় না এডওয়ার্ডকে। তবু তাকে যেহেতু পরীক্ষাগারে তৈরি করা হয়েছিল কৃত্রিম মানুষ হিসেবে, তাই আমরা তাকে ‘রোবট’-ই বলব। এডওয়ার্ড কিছুই সেভাবে করতে পারে না। হাতের জায়গায় ছুরি-কাঁচি থাকলে কীভাবেই বা কেউ কাজ করতে পারে। কিন্তু একটা কাজ সে দারুণভাবে পারে। তা হল যে-কোনও কিছুকে নিপুণভাবে ছাঁটতে পারা। তা চুল হোক বা গাছের পাতা।
আসলে এডওয়ার্ডের মধ্যে লুকিয়ে আছে এক অসহায় শিল্পীর রূপক। ‘নিস্ফল হতাশের দলে’ থাকা একজন শিল্পী তো কেবল তার শিল্পকর্মের কাজেই সাবলীল। সে কেবল জানে সৃষ্টি করতে। আর জানে ভালোবাসতে। এডওয়ার্ডও ভালোবেসেছিল। কিমকে। বড় আশ্চর্য সে ভালোবাসা! এডওয়ার্ডের ‘সিজার হ্যান্ড’ বা ছুরি-কাঁচিওয়ালা হাত কিমকে ধরতে গেলে কিম আহত হয়। আবার সেই হাত দিয়েই সে ক্রিসমাসের সময় বরফের তৈরি পরি বানিয়ে দেয় কিমের জন্য। সে এক অনবদ্য সৃষ্টি! তুষারপাতের এফেক্টও সে বানিয়ে দেয় পরির সঙ্গে। তার তলায় মনের খেয়ালে নেচে বেড়াতে থাকে কিম। অথচ কিমের প্রেমিক জিম আর প্রতিবেশী মহিলা জয়েসের ষড়যন্ত্রে এডওয়ার্ড সমাজের চোখে একজন অপরাধী হিসেবে পরিগণিত হয়। যদিও আইন তার ‘অস্বাভাবিকত্বে’র জন্য তাকে মুক্তি দেয়। ছবির একদম শেষে এডওয়ার্ডের সঙ্গে যুদ্ধ বাঁধে জিমের। জিম মৃত হয়, এডওয়ার্ডই হত্যা করে তাকে। আসলে জিম কিমের সঙ্গে দুর্বিনীত আচরণ করেছিল। তাই এডওয়ার্ডের হাত-রূপী ছুরি-কাঁচিতে রক্তের ছিটে লাগল! সবাই ধরে নিল এডওয়ার্ডও আর বেঁচে নেই। কিন্তু কিম জানে তার এডওয়ার্ড আছে সেই পুরনো দুর্গেই। একা। সময় গড়ায়। বৃদ্ধা কিম গল্প শোনায় নাতনিকে। কল্পনা করে এডওয়ার্ড আজও সৃষ্টি করে চলেছে। পাহাড়ের চুড়োয় বসে সে বরফ কেটে তুষার বানাচ্ছে। যাতে সেই তুষারের তলায় তার প্রিয়তমা কিম নেচে উঠতে পারে। কিম নাতনিকে বলে, ‘সামটাইমস ইউ ক্যান স্টিল ক্যাচ মি ড্যান্সিং ইন ইট।’ এডওয়ার্ড সমাজের চোখে ‘মানুষ’ নয়। অথচ তার মতন হৃদয়বত্তা আছে ক-জন মানুষের?
আরও তো কতই ছবি আছে, যার প্রধান চরিত্র রোবট। কিন্তু ক’টার কথাই বা একটা লেখায় বলা যায়? তবু শেষ করার আগে আর একটি ছবির কথা বলতেই হবে। সেই ছবি, স্টিভেন স্পিলবার্গের ‘আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স’ বা সংক্ষেপে ‘এ. আই’। সাই ফাই মানেই যে উড়ন্ত চাকি, এলিয়েন, রোবট আর লেজার পিস্তল নয়— বরং তা যে এসবকে ছাপিয়ে কত সুদূরপ্রসারী হতে পারে এই হৃদয় মোচড়ানো ছবি তার এক অন্যতম উদাহরণ। হেনরি আর মনিকার একমাত্র সন্তান মার্টিন সিনক্লেয়ার ভাইরাসের প্রকোপে শয্যাশায়ী। তাকে সুস্থ করার আপ্রাণ চেষ্টা চলছে। কিন্তু এই রোগের তখনও অবধি কোনও চিকিৎসা নেই। তাই তার সুস্থ হওয়ার সম্ভাবনা বেশ কম। এমতাবস্থায় হেনরি-মনিকার সংসারে আসে বালক ডেভিড। সে মানুষ নয়। এক রোবট। তাকে বানিয়েছে নিউ জার্সির সাইবারট্রনিকস, যেখানে চাকরি করে হেনরি। মনিকা প্রথমে ডেভিডকে মেনে নিতে পারে না। ভয় পায়। কিন্তু ক্রমে তার মনে ডেভিডের প্রতি ভালোবাসা জন্মায়। সে ভালোবাসা এক সন্তানের জন্য ভালোবাসা। ডেভিড ক্রমে ওই দম্পতির সন্তান হয়ে ওঠে। ডেভিডের সঙ্গী ছিল এক রোবো টেডি।
হঠাৎ একদিন মার্টিনের অসুখের চিকিৎসা আবিষ্কৃত হয়। সে সুস্থ হয়ে ফিরে আসে। স্বাভাবিকভাবেই ডেভিড ও মার্টিন, কেউই পরস্পরকে মেনে নিতে পারে না। এক পুল পার্টিতে ডেভিড চড়াও হয় মার্টিনের ওপর। যদিও তার পেছনে ছিল মার্টিনের বন্ধুদের যড়যন্ত্র, তবু হেনরি বোঝে ভালোবাসা নামের আবেগটির জন্ম হওয়ার দরুন ডেভিডের মধ্যে জন্ম নিয়েছে ভালোবাসার উলটো পিঠে থাকা ঘৃণাও! এখন তাকে সাইবারট্রনিকসে ফেরত দিয়ে দেওয়াই ভালো। সেখানে তাকে ধ্বংস করে ফেলা হবে। কিন্তু মনিকা তাতে রাজি হয় না। তার মাতৃসত্তা প্রবল হয়ে ওঠে। সে ডেভিডকে ছেড়ে আসে জঙ্গলে। সেখানে সব বাতিল রোবটেরা থাকে। গল্প এগিয়ে চলে। বালকের মন নিয়ে ডেভিড খুঁজে চলে নীল পরিকে, যে তাকে রোবট থেকে মানুষ করে তুলবে।
এরপর সময় গিয়েছে চলে দু-হাজার বছরের পার। পৃথিবী থেকে মানুষ বিলুপ্ত হয়েছে। রয়ে গেছে রোবটেরা। তারা মানুষ নিয়ে গবেষণা করছে। এমতাবস্থায় বরফের তলায় খুঁজে পাওয়া যায় ডেভিডকে। জেগে উঠে ডেভিড মায়ের কাছে ফিরতে চায়। ডেভিডের সাধের টেডির কাছে ছিল মনিকার চুলের গোছা। সেই চুলের গোছার মধ্যে থাকা ডি এন এ থেকে রোবটেরা ফিরিয়ে দিতে পারে মনিকাকে। কিন্তু সেই প্রত্যাবর্তনের মেয়াদ হবে মাত্র একদিনের। ডেভিডকে ভেবে দেখতে বলা হয়। কিন্তু ডেভিড তাতেই রাজি। কারণ সেই একটি দিনই যে তার কাছে তার জীবনের শ্রেষ্ঠ দিন। ফিরে আসে মনিকা। জানতে চায়, ‘হোয়াট ডে ইজ টুডে?’ ডেভিড জানায়, ‘ইট ইজ টুডে।’ সে তার মা’কে জড়িয়ে ধরে শুয়ে থাকে। মা জানায় সে ডেভিডকে খুব ভালোবাসে। তারপর একসময় ঘুমের মধ্যে তলিয়ে যেতে থাকে মনিকা। যে ঘুম থেকে সে আর কোনও দিনই জেগে উঠবে না। তার কোল ঘেঁষে শুয়ে থাকে ডেভিড। সে ঘুমের মধ্যে দিয়ে পৌঁছতে চায় সেখানে, যেখানে স্বপ্নেরা জন্ম নেয়। হেয়ার ড্রিমস আর বর্ন।
এ দৃশ্যের পরে আর কথা চলে না। শুধু বলব, রোবটের মধ্যে জেগে ওঠা ভালোবাসা, সময়ে সময়ে কোনও মানুষের থেকে কোনও অংশে কম নয়। আসলে এসব সিনেমার ভেতর থেকে একটা বার্তা উঠে আসে। যন্ত্র যদি মনুষ্যত্ব অর্জন করতে পারে, তবে মানুষ কেন স্বধর্ম ত্যাগ করে নিজেকে যান্ত্রিকতায় আবদ্ধ করে ফেলছে? ত্যাগ করছে সমস্ত শুভ চেতনা? মানুষ ফিরে যাক নিজের ভেতরকার পবিত্রতার কাছে, ভালোবাসার কাছে। না হলে বলা যায় না, হয়তো ভবিষ্যতের রোবটরা মানুষকে হৃদয়বত্তায় হারিয়েও দিতে পারে!
(পুনর্মুদ্রিত)
Tags: প্রবন্ধ, বিশেষ আকর্ষণ, বিশ্বদীপ দে, মূল প্রচ্ছদ, ষষ্ঠ বর্ষ প্রথম সংখ্যা

