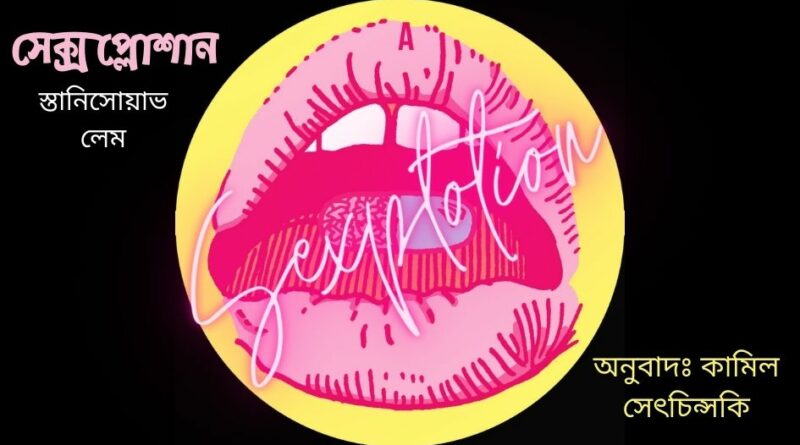সেক্সপ্লোশন
লেখক: Stanislaw Lem; অনুবাদ: কামিল শেৎচিন্সকি
শিল্পী: দীপ ঘোষ
নিখুঁত শূন্যতা (১৯৭১)
অর্থাৎ ভবিষ্যতে লেখা সম্ভাব্য বইগুলির সমালোচনার সংকলনে অন্তর্ভুক্ত
সিমন মেরিলের সেক্সপ্লোশন
(ওয়াকের এন্ড কোম্পানি – নিউ ইয়র্ক)
আমরা যদি লেখকদের কথা সত্য বলে ধরে থাকি – যেমন কল্পবিজ্ঞান লেখকদের বিশ্বাস করার প্রবণতা বাড়ছে দিনে দিনে! – তাহলে আজকাল যৌনতার যে পরিমাণ বাড়বাড়ন্ত দেখা যায় সামাজিক জীবনে তা আশি দশকের মধ্যে সারা দুনিয়াকে দেবে ভাসিয়ে। তবু ‘সেক্সপ্লোশন’ উপন্যাসের শুরুটা আশি দশকের থেকে আরও বিশ বছর এগিয়ে, কনকনে শীতে বরফ-চাপা নিউ ইয়র্কে। একজন অজ্ঞাতনামা বৃদ্ধ পিচ্ছিল বরফের উপর গুটিগুটি পায়ে বরফে-জমা গাড়ির সারিতে ঠোকা খেতে খেতে এক নিষ্প্রাণ বহুতল অট্টালিকার সামনে দাঁড়ান। পুরু কোটের পকেটে লুকিয়ে রাখা চাবি বার করে ভারি লোহার দরজা খোলেন আর চৌকাঠ পেরিয়েই পাড়ি জমান এই অট্টালিকার পাতালঘরে। এই পাতাল-বিহারে তাঁর স্মৃতিচারণই এই উপন্যাসের মূল কাহিনী।
বৃদ্ধের কাঁপা হাতের টর্চের আলো এই থমথমে পাতালের আনাচে-কানাচে পড়েছে, কিন্তু ঠিক বোঝা মুশকিল এটা কি জাদুঘর, নাকি মস্ত কোনো বাণিজ্যিক-সংস্থার জোগানি (নাকি যৌন-জোগানি) গুদাম – যে সময় আমেরিকা পুনরায় ইউরোপের উপর আধিপত্য বিস্তার করছিল, সেই আমলেরই তৈরি। ইউরোপের আধা-কারিগরি কারখানাগুলি মার্কিনি যান্ত্রিক উৎপাদনের দুর্ধর্ষ গতির সাথে পাল্লায় পড়ে এই বিজ্ঞান-প্রযুক্তির জ্বালানিতে চালিত শিল্পোত্তর দানোর কাছে হার মানতে বাধ্য হল। যুদ্ধের ময়দানে টিকে গেল মাত্র তিনটে খেলোয়াড়: জেনারেল সেক্সোটিক্স, সাইবোরডেলিক্স এবং লাভ ইনকর্পোরেটেড। এই তিনটে দানোদের উৎপাদন যখন তুঙ্গে, তখন যৌনতা ব্যক্তিগত সম্পর্ক, মাঠে-ঘাটে করা ব্যায়াম, টাইমপাস, স্ট্যাটিস্টিক্স চড়ানো খেলার গণ্ডি পেরিয়ে বিশ্ব-সভ্যতার মূল দর্শনে পরিণত হল।
ডঃ ম্যাক-ল্যাহান যিনি বুড়ো হয়েও এখনো বেঁচে আছেন, তিনি তাঁর রচিত “কামতন্ত্র”-এ প্রমাণ করে দেখিয়েছিলেন, যে যবে থেকে মানুষ প্রযুক্তির পথে প্রথম পা ফেলেছে তবে থেকেই এই পরিণাম তার কপালে আঁকা ছিল। আদিকেলে নাবিকদের দাঁড় বাওয়া, সুদূর উত্তরের কাঠুরেদের করাত ঘষা, স্টিভেনসনের ভোঁসভোঁসে বাষ্পীয় ইঞ্জিন সে সমস্ত উদ্ভাবন ছন্দ, রূপ আর ভঙ্গির অর্থ নির্ণয় করছিল মনুষ্য সংগমের, মানে মনুষ্য সংসারের। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের যান্ত্রিক উৎপাদন ব্যবস্থা প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের জ্ঞান-বিজ্ঞান গ্রাস করে নিল। এরপর মধ্যযুগীয় সতীত্বের নিগড় ভেঙে তালা-ভাঙা বেল্টের যুগ শুরু হলো… আর যাবতীয় শিল্পকলাকে পুরোদমে লুচ্চাইন, নুনুটান, লিঙ্গুড়ি, পাছুটিপ, ভগভুগি, পানুকব্জা, কুলফিকল ইত্যাদির যৌনযন্ত্রের নির্মাণে লাগানো হয়েছে। ফোলা-ফাঁপা কারখানা থেকে বেরোচ্ছিল লাগাই-গাড়ি, স্বয়ংচল ধর্ষযান, ঘরোয়া চিঙ্কি-কিঙ্কি আর সুবহ কামালয়। এছাড়া নতুন নতুন গবেষণাকেন্দ্রে অভিনব কৌশল বার করা হচ্ছিল কি ভাবে প্রজননের দায় থেকে মুক্তি পেয়ে বিশুদ্ধ তৃপ্তি পাওয়া যায়।
যৌনতা এখন আর শুধু ব্যবসায়িক পণ্য নয়—এটি এক নতুন ধর্মে পরিণত হয়েছে। নিত্যদিনের কাজ এখন যৌনতৃপ্তি অর্জন, আর তার পরিমাপক যন্ত্রগুলো রাস্তা-অফিসে টেলিফোনের মতোই সর্বত্র ছড়িয়ে আছে। তাহলে সেই পাতালযাত্রী বুড়ো আদতে কে? জেনারেল সেক্সোটিক্সের উকিল? তাঁর সৃতিচারণে বারবার ফিরে আসে সেই হাইকোর্ট-ঘেঁষা নামি-দামি মকদ্দমা, মানব-পুতুল দিয়ে বিখ্যাত ব্যক্তিদের রূপচেহারা নকল করার সেই অধিকার-আন্দোলন (ইউএসের রাষ্ট্রপতির স্ত্রীও বাদ যায়নি!)। আবার ১২ মিলিয়ন ডলারের খরচে জেনারেল সেক্সোটিক্স জিতেওছিল। এখন সেই বৃদ্ধের টর্চের আলোয় দেখা যায় ধুলোয় ঢাকা প্লাস্টিকের ডিসপ্লে কেসে সাজানো হলিউডের নায়িকা, তারকা, রাজকুমারি আর মহারানিদের চিরসুন্দর মূর্তি। আদালতের রায় অনুযায়ী, তাদের ‘শালীনতা’ বজায় রেখেই এগুলো প্রদর্শন করতে হবে!
কৃত্রিম মৈথুন মাত্র এক দশকের মধ্যে প্রাথমিক ফুঁতে-ফোলানো ও হাতে-ঘোরানো পুতুল থেকে শীততাপনিয়ন্ত্রিত ও প্রতিক্রিয়া-সক্ষম যৌনসঙ্গী রোবটে উন্নীত হল। এই রোবটগুলির মডেল হিসেবে ব্যবহৃত ব্যক্তিরা হয় মৃত্যুবরণ করেছেন নয়তো বার্ধক্যে পৌঁছেছেন, যখন টেফ্লোন, নাইলন, ড্রালোন আর সেক্সোফিক্সের মতো টেকসই পদার্থ কালপ্রবাহকে দিব্যি জিইয়ে চলেছে। এখন সেই মোমপুতুলের জাদুঘরের মতো সাজানো প্লাস্টিক অপ্সররা পথভোলা বুড়োর দিকে স্থির হাসিতে নিবদ্ধ। প্রত্যেকের হাতে রয়েছে একটা টেপরেকর্ডার, যার মধ্যে ভরা আছে এক একজনের মনমোহিনী গান। উল্লেখ্য, হাইকোর্টের আদেশে টেপ-বসানো পুতুল বেচার উপর মানা ছিল, তবে খদ্দের তার পছন্দমতো রেকর্ডিং ভরতে পারত।
নিঃসঙ্গ বৃদ্ধটির ধীর এলোমেলো পদক্ষেপে উঠতে লাগল ধুলোর পর্দা। সেই ধূলিকণার ফাঁকে ফাঁকে গোলাপি আলোর মধ্যে ঝলকায় জমা-জমা রমণের দৃশ্যরাশি, কোনও কোনও ক্ষেত্রে ৩০ জনের অঙ্গপ্রত্যঙ্গ বিশাল ছানার জিলিপির মতো সস্নেহে পেঁচানো। হয়ত বা জেনারেল সেক্সোটিক্সের স্বয়ং অধিকর্তা সুবহ কামালয় আর স্বয়ংচল ধর্ষযানের মধ্যে পায়চারি করছেন? অথবা কোম্পানির সেই প্রধান ডিজাইনার, যে আমেরিকা আর বিশ্বকে যৌনাঙ্গের ছাঁচে ঢালাই করেছিল? এই যে কল-কব্জায় ভর্তি সেই বিখ্যাত চশমা, যার চোখের সীসার পর্দা নিয়ে ৬টা আদালতে একসাথে মামলা চলছিল একসময়; এই যে রপ্তানির জন্য প্রস্তুত রকমারি বয়াম – জাপানি বল, ডিলডো, পূর্বরাগের মলম জাতীয় হাজারো পণ্যতে ভরাট। প্রত্যেকটিতে নির্দেশাবলীর ফর্দ এবং হেল্পবুক সংযুক্ত।
সেই সময়টি ছিল পূর্ণাঙ্গ গণতন্ত্রের স্বর্ণযুগ: সবাই সবকিছু করতে পারত – সবার সাথে। বণিক-সংস্থাগুলি তাদের পয়সায় পোষা ভবিষ্যৎবাদীদের পরামর্শ নিয়ে, একচেটিয়া-বিরোধী আইন টপকে, চুপি চুপি বিশ্বের বাজার ভাগ করে নিল। এখন তিনটে কোম্পানি এক একটা বিশেষ ক্ষেত্রের উপর থাবা বসাল। জেনারেল সেক্সোটিক্স যৌন-বিকারের মুক্তি-আন্দোলন চালাচ্ছিল, যখন বাকি দুটো কোম্পানি স্বয়ংক্রিয়করণের পিছনে ফলাও করে টাকা ঢালছিল। ধারালো চাবুক, কেলেঙ্কাটোর, পিটুনি-টিউবের প্রোটোটাইপ পাব্লিককে দেখালে কোন লাভ ছিল না কেননা সঙ্গে সঙ্গেই বিশাল উৎপাদন-ব্যবস্থার দরকার ছিল। আবার বিশাল ব্যবস্থা হতে গেলে শুধু চাহিদা মেটালে চলবে না, চাহিদা সৃষ্টিও করতে হয়! ঘরোয়া লালসার সাবেকি যত যন্ত্রপাতি, সেগুলি চকমকি-পাথর আর নিয়ান্ডার্থালের গদার পাশেই জমা দেওয়া উচিত জাদুঘরে। পণ্ডিতমণ্ডলী ছ’-আট বছরের কোর্স এবং তুলনামূলক রমণরীতির উচ্চবিদ্যালয়ের পাঠক্রম তৈরি করেছেন। তারপরে বাজারে আসতে লাগল স্নায়ু-মন্থনী, খাবিচুম, চুপিছিপ আর বিশেষ ধরণের শব্দশোষক সিমেন্ট – যাতে পাড়াপড়শীরা একে অপরের শান্তি বিঘ্নিত না করে।
তবুও এগিয়ে চলতে হল এই অমানবিক অবিশ্রান্ত দৌড়েই, কারণ উৎপাদনের কাছে স্থিতি হল মৃত্যুর সমান। ব্যক্তিগত উপভোগের জন্য ওলিম্প পর্বতের দেবালয় পরিকল্পিত হচ্ছিল। সাইবরডেলিক্সের সাইবারডেলিক্সের ঝলসানো বিজ্ঞাপনে প্রথম প্লাস্টিকের গ্রীক দেবদেবীদের ঐশ্বর্যময় কামকিংকর দেখানো হত। ফেরেশতা-দেবদূতদের নিয়ে কথাও উঠেছিল – এমনকি গির্জার সঙ্গে মামলা করার জন্য বিশেষ আমানত বরাদ্দ করা হল। যদিও কিছু খুঁতখুঁতে বিষয় এখনও মীমাংসা পায়নি যেমন ডানাগুলি কিসের হলে ভালো; আসল পালক তো কারো নাকে চুলকোতে পারে, আবার বেশি নড়াচড়া করলে এতে কী অসুবিধে হতে পারে। মাথার উপর দৈব্য দৈব জ্যোতি নিয়ে কি হবে? তাকে চালু আর বন্ধ করার ব্যবস্থা কোথায় থাকবে ইত্যাদি ইত্যাদি। ঠিক সেই সময় বজ্রপাত এল।
একটা রসায়নিক পদার্থ (বোধ হয় সত্তর দশকে) আবিষ্কৃত হল, যার সাংকেতিক নাম নো-সেক্স। শুধুমাত্র মুষ্টিমেয় উচ্চপদস্থ বিজ্ঞানী ও কর্মকর্তা তার অস্তিত্ব সম্বন্ধে অবগত ছিলেন। এই পদার্থটি একটা গুপ্ত অস্ত্র বলে পরিচিতি পেল এবং তার তৈয়ারি একটি ছোট পেন্টাগন-সংশ্লিষ্ট কোম্পানির কীর্তি। বাস্তবপক্ষে, গ্যাসীয় অবস্থায় নো-সেক্স যে-কোন দেশের জনসংখ্যা শূন্যের ঘরে নামাতে পারে, কেননা এটি যৌনক্রিয়ার সমস্ত সুখের অনুভূতি নিমেষের মধ্যে নিঃশেষ করে ফেলে। কার্যত, যৌনমিলন সম্ভব হলেও তা সিঁধ কাটা বা ভিজে কাপড় নিংড়ানোর মতো একেবারেই নীরস, ক্লান্তিকর কাজে পরিণত হয়। তারপর নো-সেক্স দিয়ে তৃতীয় বিশ্বের জনবিস্ফোরণ আটকানোর প্রস্তাবও এল, কিন্তু তাকে বাতিল করতে হল অতিরিক্ত খতরনাক বলে।
বিশ্বব্যাপী এই সর্বনাশের সঠিক কারণ আজও অজানা। নো-সেক্সের গোপন ভাণ্ডারগুলো কি বৈদ্যুতিক দুর্ঘটনায় বিস্ফোরিত হয়ে ইথারের সাথে মিশে গেল? এতে কি একচেটিয়া তিনটে কোম্পানির কোন প্রতিদ্বন্দ্বী হাত দিল? নাকি এটা কোন উগ্রবাদী, রক্ষণশীল বা ধর্মীয় দলের ষড়যন্ত্র? এই প্রশ্নটি নিরুত্তর থেকে যাবে।
পাতালের অন্তহীন করিডোর পেরিয়ে ক্লান্ত বৃদ্ধ প্লাস্টিকের ক্লিওপাত্রার তাপনিয়ন্ত্রিত কোলে বসে (তার আগে ব্র্যাক কষে নিয়ে) স্মৃতিসাগরে পাড়ি দিলেন ১৯৯৮ সালের ভয়াবহ অর্থনৈতিক সঙ্কটের দিকে। রাতারাতি সব লোক বাজার-ঠাসা মালপত্র ঘৃণার সঙ্গে নস্যাৎ করেছিল। গতকাল যা যা শরীর-মন তুলত রাঙিয়ে, আজ এসব শ্রান্ত কাঠুরের জন্য যেমন কুড়াল, ধোবার জন্য যেমন ভাটি তেমনি করে ঠেকতে লাগল। প্রকৃতি মানবজাতিকে এদ্দিন ধরে যে চিরন্তন মোহমায়ায়, জাদুর জালে রেখেছিল, তা পুরোপুরি মুছে গেল। এখন থেকে স্তন দেখে খালি এই কথা মনে পড়ে যে মানুষ স্তন্যপায়ী, পা – দ্বিপদচারী, পাছা – বসার জন্য একটি প্ল্যাটফর্ম। আর কিছুই নয়! ডঃ ম্যাক-ল্যাহানের ভাগ্য ভালো যে তিনি এই ভয়াবহ সময় দেখে যেতে বাঁচেননি। ক্যাথিড্রাল আর মহাকাশযান, জেট-ইঞ্জিন, ট্যারবাইন, বায়ুকল, নুনদানি, টুপি, আপেক্ষিকতাতত্ব, অঙ্কের বন্ধনী, শূন্য ও বিস্ময়ক চিহ্ন, এই সব সেই একি মৌলিক ও স্বয়ংসম্পূর্ণ কর্মক্রিয়ার অনুরূপে আর অনুসারে কাজ করবে বলে তিনি আরো আগে আন্দাজ করেছিলেন। এবার তাঁর যাবতীয় অনুমান ব্যর্থ হয়ে গিয়েছে, যখন মানবজাতি নিঃসন্তান বিলোপের ঝুঁকির সামনে দাঁড়িয়েছে।
নো-সেক্সের প্রভাবে সমাজে যে বিপর্যয় নেমে এল, তার ধারাবাহিকতায় ১৯৯৮ সালে এমন এক অর্থনৈতিক সঙ্কট দেখা দিল, যার তুলনায় ১৯২৯ সালের মহামন্দাও তুচ্ছ ঘটনা বলে মনে হল। প্রথমদিকে “প্লেবয়”-এর সম্পাদকবৃন্দ সমেত গোটা প্রকাশনা পুড়ে গেল; অনাহারে কিংবা জানলা থেকে ঝাঁপ দিয়ে মরত বেশ্যা-রক্ষিতা-গনিতা আর স্ট্রিপ-ক্লাবের নট-নটিনী যত; দেউলে হয়ে পড়ল ছবিওয়ালা পত্রিকাগুলি, গ্লোবাল পর্ন ইন্ডাস্ট্রি, বিজ্ঞাপন-বাড়ি, রূপচর্চাকেন্দ্র সবই ধ্বসে গেল। সৌন্দর্য-সুগন্ধির কারবার, অন্তর্বাসের ব্যবসাও বেজায় মার খেয়ে গেল – ১৯৯৯ সালে আমেরিকার বেকারত্বের সংখ্যা প্রায় সাড়ে তিন কোটি।
এই অবস্থায় জনগণের মন কি দিয়ে ভোলানো যায়? ধনুষ্টঙ্কারের বেল্ট, নকল কুঁজো, পাকা পরাচুলা, বিকলাঙ্গের উইলচেয়ারে বসা কাঁপো কাঁপো পুতুল, অন্তত যেগুলো দেখে যৌনশ্রমের পীড়াপীড়ি, সেই প্রাকৃত অত্যাচার ভোলা যেতে পারে। শুধু এই ধরণের যন্ত্র যৌনাঙ্গের নিরাপত্তায় রাখতে পারে, কাজেই নিস্তার ও শান্তির মাধ্যম হয়ে উঠল এইগুলি। সব দেশের সরকার বিপদের গুরুত্ব বুঝে মানবজাতির অস্তিত্ব রক্ষায় জরুরি পদক্ষেপ নিল।
খবরের কাগজে বিবেক জাগরণের আবেদন ছাপা হতে লাগল, টেলিভিশনে ধর্মগুরুরা আত্মসমর্পণের ডাক দিলেন—কিন্তু জনসাধারণের কাছে তাদের বক্তব্য ফাঁপা ঠেকল।
ঘৃণা কাটানোর জন্য যাবতীয় ডাকাডাকি ও সম্প্রচার ব্যর্থ হল। বিছানার ক্ষেত্রে এতে খুব একটা ফল ফলেনি। শুধুমাত্র একটা সবিশেষ দায়িত্ববোধের অধিকারী জাপানি জাতি দাঁত চেপে আদেশ অনুসরণ করতে চলেছে। ঐ সময় বিশেষ আর্থিক সুবিধে, বেতন বৃদ্ধি, সাম্মানিক, সম্মানপত্র, মর্যাদাদান, সংবর্ধনা, স্বর্ণপদক, পুরস্কার ট্রফি আর অবশেষে সংগমের প্রতিযোগিতা প্রতিষ্ঠিত হল। যখন এতেও কোনও ফল ফলেনি, তখন জোরজবরদস্তির পালা শুরু হল। তবুও মানুষ প্রজননের দায়িত্ব এড়াতে অসংখ্য কৌশল বার করতে শিখেছে। ছেলেমেয়েরা বনে-জঙ্গলে ঘাপটি দিয়ে থাকত, পুরুষমহিলারা অক্ষমতার নকল সার্টিফিকেট দেখাত, সামাজিক নিয়ন্ত্রণের সভা-সমিতির প্রাচীরে ফাটল ধরল । সেক্স থেকে নিজেকে বাঁচানোর জন্যে মানুষ কি না করত! এজন্যেই নজরদারি আর খচ্চরগিরিও বেড়েছে।
এখন ক্লিওপাত্রার কোলে বসা আমাদের বৃদ্ধটির কাছে এই দুর্যোগকালও নেহাৎই স্মৃতি। মানবজাতি মরে যায়নি; বর্তমানে নিষিক্তকরণ একটা স্যানিটারি-হাইজিনিক পদ্ধতিতে করানো হয়, খানিকটা টিকা নেওয়ার মতো। উত্তপ্ত উদ্যোগপর্বের পর মোটামুটি একটা স্থিতিশীল অবস্থা ফেরানো হল। তবুও সংস্কৃতির কোনো রকম ফাঁক সয় না; যৌনতার অন্তঃস্ফুরণের পর থেকে যে দুঃসহ অভাব খাঁ খাঁ করতে লাগল, রমণের অবসানের পর যে গহ্বর তৈরি হয়েছিল, তা এখন পূরণ করেছে ‘খাদ্য-কাম’। রান্নাবান্না এবার রসালো আর অতি-রসালোতে ভাগ করা হয়। ভোজকামিতা, রেস্তরাঁর ফুডপানুর এ্যালবাম আর কোন কোন খাদ্যবস্তু সবিশেষ ভঙ্গিতে ভক্ষণ করলে অকথ্য অশ্লীল বলে মনে করা হয়। যেমন হাঁটু পেতে ফল খাওয়াটা টাবু (আবার এইটুকু স্বাধীনতার জন্য হাঁটু-পাতা-পার্টি লড়াই করে), আধা করে পা উঁচিয়ে শাক বা ডিমের ভাজি খাওয়াও নিষিদ্ধ। তবুও আছে – থাকাটাই স্বাভাবিক! – কিছু গোপন হোটেল, যেখানে রসিক ও বিশেষজ্ঞদের জন্য নোংরামির মেলা পাতা আছে। সেখানে পাকাপোক্ত রেকর্ডমারি পেটুকেরা এমন গিলেঠুসে খায় যে দর্শকদের মুখে লালা ভরে। দিনেমার থেকে ফুড-পানু পাচার হয়, যেগুলির মধ্যে বিকৃতির একশেষ: একজন স্ট্র দিয়ে ভুজিয়া শুষে খায়, তার সঙ্গে আর একজন টেবিলের উপর শুয়ে, গায়ে মেজপোশ মুড়ানো, ঝাল-রসুন দেওয়া পুঁইশাকে আঙুল ডুবিয়ে কেপ্সিতে কষানো শুয়োর মাংসের স্টুর ঘ্রাণ আস্বাদন করে। আবার তার দু’পা দড়ি দিয়ে দুধ চায়ের কেটলিতে বাঁধা, যা এই দৃশ্যে ঝাড়বাতির বদলে ব্যবহার করা হয়েছে। সাহিত্যেও এই প্রবণতা: এই বছরের যে উপন্যাস “ফেমিনা” পুরস্কার পেয়েছে তার প্রধান নায়ক পোস্ত বাটা দিয়ে তার মেঝেটা মাখিয়ে মাটিটা চেটে চেটে উপভোগ করে, তার আগে চাউমিনের মধ্যে আকণ্ঠ লুটোপুটি খেয়ে। রূপচেহারার আদর্শও পাল্টে গেল। এখন ১৩০ কেজির স্থূল শরীর রাখা কাম্য, এতে প্রমাণ পায় পাকস্থলির ক্ষমতা। ফ্যাশন-কায়দার ক্ষেত্রেও অদলবদল: আশাকপোশাক দেখে স্ত্রী না পুরুষ চেনা ভার। মুষ্টিমেয় অগ্রগতি দেশের সরকারে এই আলোচনা উঠেছে, স্কুলে বাচ্চাদের পাকতন্ত্রের নিগূঢ় তত্ব এই বয়সে শেখানো উচিত কিনা। এদ্দিনে এই প্রসঙ্গটি অশ্লীল বলে টাবুর সংগোপনীয়তায় আগলে রাখা ছিল।
শেষ পর্যন্ত জীববিজ্ঞান লিঙ্গভেদ পুরোপুরি মুছে ফেলার পথে অগ্রসর হয়েছে – সে এক অপ্রয়োজনীয় প্রাগঐতিহাসিক বোঝা। ভ্রূণ এখন সিনথেটিক পদ্ধতিতে তৈরি হবে এবং জেনেটিক ইঞ্জিনিয়ারিংয়ের মাধ্যমে প্রোগ্রাম করা হবে। কাজেই মানুষ থাকবে সম্পূর্ণ লিঙ্গহীন। এতেই যৌনতার দুঃস্বপ্ন থেকে মুক্তি পাবে মানবজাতি। ঝকঝকে পরীক্ষাগারে, সেই প্রগতির দেবালয়ে, সৃষ্টি হবে অর্ধনারীশ্বর, বরং নরনারীত্বহীন নতুন মানুষ এবং অবশেষে মানবজাতি আদিকেলে কালিমা থেকে মুক্তি পেয়ে সমস্ত রকম ফল উপভোগ করতে পারবে… কেবলমাত্র রন্ধনবিধি দ্বারা নিষিদ্ধ কিছু ব্যতীত।
[মূল পোল ভাষা থেকে অনুবাদ – কামিল শেৎচিন্সকি]
সম্পাদনাঃ দীপ ঘোষ
Tags: kalpabiswa y7n1, Stanislaw Lem, কামিল শেৎচিন্সকি, দীপ ঘোষ, স্তানিসোয়াভ লেম