মাউন্ট শাস্তা
লেখক: দীপেন ভট্টাচার্য
শিল্পী: জটায়ু
অমলের কথা
এক মহাকবি বা দার্শনিক নাকি বলেছিলেন মহাবিশ্ব আমাদের সঙ্গে খেলা করে। কিন্তু আমরা সেই মহাবিশ্বের অংশ, আমাদের পক্ষে কি সেই খেলার প্রকৃতি বোঝা সম্ভব? আমার পক্ষে আর সম্ভব নয়, আমার সময় ফুরিয়ে এসেছে। তাই সবকিছু ভুলে যাবার আগে শেষ কয়েকটা কথা লিখে যেতে হবে। গুরুত্বপূর্ণ কিছু কথা। আমার জন্য সেই কথাগুলির প্রয়োজনীয়তা ফুরিয়েছে, কিন্তু আপনাদের জন্য সেগুলোর অর্থ আছে। হয়তো আজকে সেটা বুঝবেন না, কিন্তু একদিন হঠাৎ করে রাস্তায়, কিংবা বিছানায় শুয়ে, কারখানায় কাপড় সেলাই করতে করতে অথবা দুপুরের খাবার খেতে খেতে, টেলিভিশন দেখতে দেখতে, কিংবা ক্লাসে লেকচার দিতে গিয়ে আপনার মনে হতে পারে আপনার জন্য সময় থেমে গেছে। ঠিক থেমে গেছে বলব না, বরং মনে হবে আপনার জীবনে যা কিছু হবার ছিল সবই ঘটে গেছে, রয়ে গেছে শুধু একটা অস্পষ্ট মলিন প্রতিফলন, যে প্রতিফলন দেখা যায় পুরাতন কাঁসার বাসনের পেছনে। কিন্তু এসব নিয়ে বেশি দার্শনিকতা করবার সময় আমার নেই, আগেই বলেছি সময় আমার ফুরিয়ে যাচ্ছে দ্রুত, খুব দ্রুত।
কিন্তু এখন আমার ভয় হচ্ছে যে লিখতে লিখতে পুরোনো লেখা অদৃশ্য হয়ে যেতে পারে, অর্থাৎ ‘অর্থাৎ’ লিখতে না-লিখতেই ‘ৎ’-এর লেজ মুছে যেতে থাকবে, তারপর ‘ৎ’-এর মাথা মুছে যেতে পারে, তা-ই যদি হয় তবে কোনওভাবেই হয়তো ভবিষ্যতে এগোনো সম্ভব নয়, আর আমার ইতিহাসটাও পুরোপুরি জানানো সম্ভব নয়। আমি ইতিমধ্যেই ভবিষ্যতের কথা ভুলে গেছি, এখন শুধু অতীতকে পুনর্গঠন করতে চাইছি। কিন্তু কিছুক্ষণের মধ্যেই অতীত ও ভবিষ্যৎ দুটোই আমার হাতছাড়া হয়ে যাবে, আমি নিশ্চিত জানি সেটা, আমি হব বর্তমানের দাস।
কিন্তু তার আগে, আমার সময় এই আধো-অন্ধকারে ফুরিয়ে যাবার আগে, সহৃদয় পাঠককে জিজ্ঞেস করব তিনি এই লেখাটি আগে পড়েছেন কি না। হয়তো প্রথম কয়েকটা প্যারা পড়ে তিনি সিদ্ধান্ত নিতে পারবেন না, কিন্তু আমার গত কয়েক ঘণ্টার অভিজ্ঞতা ভাষায় প্রকাশ করার ক্ষুদ্র প্রয়াসকে তিনি যদি একটু সময় দেন, তা হলে তিনি বুঝতে পারবেন আমি কী বলতে চাইছি, তারপর নিজের জীবনের সঙ্গে মিলিয়ে উত্তরটা দিতে পারবেন।
এবার বলি গত কয়েক ঘণ্টায়, সঠিক কত ঘণ্টা কেটেছে সেটা বলতে পারব না, আমি এমন কিছুর সম্মুখীন হয়েছি, যা কিনা আমার মাঝে এক অদ্ভুত ধারণার জন্ম দিয়েছে। তার মধ্যে একটি হল এই লেখাটি আপনি অন্তত একবার হলেও পড়েছেন, দু-বারও পড়তে পারেন, এমনকী হাজার বার, অথবা অসীম বার। এর যে-কোনওটিই ঠিক হতে পারে। চোখ বুজে মনের গভীরে সেই স্মৃতিকে খোঁজার চেষ্টা করুন। মনে হয় আপনারা কেউই সেই স্মৃতির খোঁজ পাবেন না। কিন্তু তবুও, আমার বিশ্বাস আপনাদের মধ্যে এমন একজন থাকতে পারেন যিনি কিনা এই লেখাটি ভুলে যাননি। অর্থাৎ পাঠকদের মধ্যে এমন একজন আছেন, যিনি ভবিষ্যৎকে মনে রেখেছেন। সেই ভবিষ্যৎ এখন তাঁর অতীত, সেই ভবিষ্যতের স্মৃতিভরা অতীতকে তিনি স্মরণ করতে পারছেন হয়তো খুবই আবছাভাবে। আমি তাঁকে ভাগ্যবান বলব না। তাকে আমি ঈর্ষা করি না একদমই। কারণ সেই বিরল পাঠক বুঝতে পারছেন না যে তাঁর free will বা স্বাধীন-চিন্তা বলে কিছু নেই। কারণ তিনি জানেন না মহাবিশ্বের এক অদ্ভুত রেফারেন্স কাঠামোয় তিনি বন্দি, স্থান-কালের এক নির্মোহ বক্ররেখার তিনি আবদ্ধ।
গল্পে বা চলচ্চিত্রে আমি ফ্ল্যাশ-ব্যাক বা ফ্ল্যাশ-ফরোয়ার্ড কোনওটাই পছন্দ করি না, কিন্তু এই কাহিনিটা এক ধরনের ফ্ল্যাশের আশ্রয় নিতে বাধ্য। কেন বাধ্য সেটা আপনারা অচিরেই বুঝতে পারবেন। তবুও যতটুকু আমার পক্ষে সম্ভব ততটুকু আমি পাঠকের কাছ থেকে আড়াল করে রাখব, যদিও আড়াল করে রাখার মতো মানসিক দক্ষতা দেখাবার সময় আমার হাতে নেই। এই চাতুর্যের উদ্দেশ্য কোনও অভাবনীয় পট-পরিবর্তনের মাধ্যমে পাঠককে চমকে দেওয়া নয়, বরং রহস্যের বেড়াজালে দু-একজন পাঠককে তাঁর ভুলে যাওয়া স্মৃতির স্রোতে এই কাহিনিকে মনে করিয়ে দেবার প্রচেষ্টা মাত্র। আমার একান্ত অনুরোধ, সত্যি সত্যিই যদি আপনাদের মধ্যে কেউ এই কাহিনি মনে করতে পারেন, তা হলে তিনি যেন আমার বন্ধু পাওলো সিয়ুংয়ের সঙ্গে নীচে দেওয়া ঠিকানায় যোগাযোগ করেন। পাওলোর ই-মেইল ঠিকানা হল paolosiung111@gmail.com।
এবার পাওলোর কথা কিছু বলি। পাওলো সিয়ুংয়ের মা ছিলেন জার্মানভাষী সুইস, সুইজারল্যান্ডের অধিবাসী, আর বাবা ইউরোপে অভিবাসী চৈনিক। পাওলো বড় হয়েছে সুইজারল্যান্ডে, পরে পড়াশোনা করেছে ফ্র্যান্সের প্যারিসে। পদার্থবিদ। তার সঙ্গে বন্ধুত্ব আমার মার্কিন দেশে, যখন সে পিএইচডি শেষ করে দু-বছরের জন্য পোস্ট-ডক করতে আসে তখন। বর্তমানে পাওলো জুরিখের একটি স্কুলে বিজ্ঞান পড়ায়। পাওলো একজন পর্বতারোহী, তাকে দেখতে অনেকটা হংকংয়ের সুপার হিরো জ্যাকি চ্যানের মতো। অনেকে তাকে দক্ষিণ আমেরিকার আন্দিয়ান পর্বতমালার অধিবাসী বলে মনে করে।
আপনারা ‘পাঁচ-সেকেন্ড নীতি’র কথা শুনেছেন কি না জানি না, তবে ‘পাঁচ সেকেন্ড নীতি’ অনুসারে হাত থেকে কোনও খাদ্য রেস্তোরাঁর মেঝেতে পড়ে গেলে পাঁচ সেকেন্ডের মধ্যে সেটা তুলে নিলে খাওয়া যাবে। বলাই বাহুল্য, এটা কোনও বৈজ্ঞানিক নীতি নয়, বরং এই নীতি প্রণয়ন নিতান্তই মজা করবার জন্য। তবে পাওলো ‘পাঁচ-সেকেন্ড নীতি’র অনুসারী ছিল। রেস্তোরাঁ বা ফাস্টফুডের দোকানে হাত থেকে বার্গার বা আলুভাজা পড়ে গেলে কোনও রকম দ্বিধাদ্বন্দ্ব ছাড়াই সেটা তুলে নিয়ে মুখে পুরত। পাওলো ছিল সমস্ত অপচয়ের বিরুদ্ধে। একবার ইউরোপে তার সঙ্গে গাড়ি চালাতে চালাতে ও রাস্তার ধারে ক্যাম্পিং করতে করতে সেটা আমি বুঝেছিলাম। দু-একবার তার সঙ্গে আলপসের পাহাড়ে হাইকিং করেছি। পাওলোর ফিটনেস সাংঘাতিক, সে এগিয়ে গেলেও প্রতিবারই গলদঘর্ম হয়ে আমাকে রণে ভঙ্গ দিতে হয়েছে, চূড়ায় না উঠে ফিরে আসতে হয়েছে।
গত সপ্তাহে পাওলো উড়ে এল ক্যালিফোর্নিয়ায়। আমাদের এবারের পরিকল্পনা শাস্তা পাহাড়ে উঠব। শাস্তা ক্যালিফোর্নিয়ার একেবারে উত্তর প্রান্তে। উচ্চতা ১৪,০০০ ফুটের একটু ওপর, মাটির অভ্যন্তর থেকে নির্গত আন্ডেসাইট লাভা স্রোতে ছয় লক্ষ বছর ধরে একা একাই সে গড়ে উঠেছে। শাস্তার মতো পাহাড়কে বলা হয় স্ট্রাটো-ভলকানো বা স্ট্রাটো-আগ্নেয়গিরি। যুক্তরাষ্ট্রের উত্তর-পশ্চিমে কাসকেড আগ্নেয়গিরিমালার মধ্যে শাস্তা হচ্ছে একটি। শাস্ত হিমালয়ের মতো উঁচু নয়, কিন্তু তার আশপাশে কোনও পাহাড় না থাকায় সে একাই একশো, তাকে ১০০ মাইল দূর থেকে দিগন্তে দেখা যায়, তারপর যত কাছে যাওয়া যায় ততই সে মাথা তুলে বড় হতে থাকে। একাকী দাঁড়িয়ে থাকে মাউন্ট শাস্তা, যেন প্রান্তরের মাঝে সুউচ্চ সুবিশাল মহীরুহ, শুভ্র তুষারে তার মাথা আবৃত।
মার্কিন আদিবাসী ক্লামাথ জাতির কাছে শাস্তা একটি অলৌকিক স্থান, যা কিনা পৃথিবীর উৎপত্তির সঙ্গে জড়িত। এমনকী আধুনিককালেও অনেক নিউ-এইজ দর্শনের মানুষ মাউন্ট শাস্তাকে একটি শক্তিশালী আধ্যাত্মিক বিন্দু বলে মনে করে। তাই শাস্তা পাহাড়ের পাদদেশে ছোট্ট শাস্তা শহরজুড়ে ছড়িয়ে আছে বহু স্ফটিকের দোকান। অনেকে মনে করে, এই স্ফটিক মানুষের মন ও দেহের সঙ্গে মহাবিশ্বের আত্মিক বন্ধন রচনা করে।
সারাদিন গাড়ি চালিয়ে শাস্তা শহরে পৌঁছাতে সন্ধ্যা হয়ে গেল। একটা মোটেলে ঘর নিয়ে রাতের খাবার রেস্তোরাঁয় খেয়ে ফিরে এসে শুয়ে পড়ি তাড়াতাড়ি। খুব সকালে উঠে আমরা রওনা দিই। একটা গাড়ির রাস্তা শহর থেকে উত্তর দিকে শাস্তার কোল ঘেঁষে প্রায় ছয় হাজার ফুট উঁচুতে উঠেছে। সেই রাস্তার শেষ প্রান্তে গিয়ে গাড়ি রেখে পিঠে বোঝা নিয়ে রওনা হই। প্রথমে নানা ধরনের পাইনগাছ, পন্ডেরোসা, জেফরি ও লজপোল পাইন আর সিডার, ওক এবং ফারগাছের বনের মধ্য দিয়ে উঠি। ধীরে ধীরে গাছের সংখ্যা কমে আসে, একটা সময়ে গাছ শেষ হয়ে যায়। সবুজ মস-শ্যাওলায় ঢাকা পাথরের মধ্য দিয়ে সরু রাস্তাটা ওপরে ওঠে। চার হাজার ফুট হেঁটে উঠতে উঠতে বিকেল হয়ে যায়। আমরা ক্যাম্প ফেলি দশ হাজার ফুট উচ্চতায় এক বরফ জমা হ্রদের পাশে, সেই হ্রদের নাম ছিল হেলেন লেক।
তাঁবু খাটিয়ে, স্টোভে রাতের খাবার তৈরি করে খেতে খেতে সন্ধ্যা সাতটা বেজে যায়। ক্যাম্প ফায়ার না হলে পাহাড়ে সবাই রাতে তাড়াতাড়ি শুয়ে পড়ে, সকাল সকাল ওঠে। কিন্তু শোবার আগেই আকাশে মেঘ জমে। পাওলো তার আইসপিক বা গাঁইতি আকাশের দিকে তুলে বাজ পড়ার সম্ভাবনা বিচার করছিল। আকাশে তড়িৎ-আধানের পরিমাণ বেশি হলে ধাতব গাঁইতি আধানে আবেশিত হয়। সেই আবেশ নাকি হাত দিয়ে বোঝা যায়। কিন্তু বজ্রপাতের সময় আকাশে ধাতব গাঁইতি তুলে ধরা একেবারেই অনুচিত, পাওলো সেটা বলে আমাকে সাবধান করে দিল। খোলা আকাশের নীচে বাজ পড়ার আশঙ্কা অমূলক নয়, প্রতিবছরই ক্যালিফোর্নিয়ার পাহাড়ে হাইকারদের বজ্রপাতে মৃত্যুর কথা শোনা যায়।
কিছুক্ষণ পরেই বিজলি চমকাতে শুরু করল হেলেন লেকের উত্তরে পাহাড়ের ঢালকে আলোকিত করে। তারপর বৃষ্টি শুরু হল, আমরা তাঁবুতে ঢুকে পড়ি। দক্ষিণের খোলা উপত্যকা থেকে বাতাস এসে পাহাড়ে ধাক্কা খায়। সারা রাত ধরে এমন শোঁ শোঁ শব্দ হল, মনে হল যেন জেট বিমানে বসে আছি। বাতাসের ধাক্কায় মনে হচ্ছিল যেন আমাদের তাঁবু উড়ে যাবে। তাঁবুর একটা জিপার পুরো আটকানো যাচ্ছিল না, সারা রাত সেখান থেকে জল চুঁইয়ে পড়তে লাগল ভেতরে। আমরা কোনওরকমে আমাদের স্লিপিং ব্যাগের মুখ আটকে জলের হাত থেকে রক্ষা পেলাম। আমি ভাবলাম এমন অবস্থা, কাল আর পাহাড়ে ওঠা হবে না। ভালোই হবে, ভাবলাম। কেন জানি হঠাৎ করে আমার পাহাড়ে ওঠার সমস্ত শখ উবে গেল।
যা-হোক, সেই রাত তো কাটল। সকাল ছ-টায় উঠে দেখি মেঘের চিহ্নমাত্র নেই। কে বলবে কাল রাতে এত ঝঞ্ঝা ছিল। পাওলো স্টোভে কফি বানাচ্ছে। বলল, তৈরি হয়ে নাও। আমি একটু দমেই গেলাম, কিন্তু এত দূর এসে পাওলোকে তো আর বলা যায় না যে, না উঠলেও চলবে।
তৈরি হয়ে রওনা হলাম সাতটার মধ্যে। জুতোর নীচে কাঁটাওয়ালা ক্রাম্পন, হাতে বরফ-গাঁইতি, পেছনের ছোট ব্যাকপ্যাকে দড়ি। চার ঘণ্টা ধরে একটানা অ্যাভালেঞ্চ গালচ বা হিমধসের খাঁড়ি ধরে ওপরে উঠলাম— পাওলো সামনে, আমি পেছনে। পুরোটাই তুষারঢাকা পথ, পায়ের নীচে ক্রাম্পন আমাকে তুষারে পা দুটোকে ধরে রাখতে সাহায্য করছিল। অনেক নীচে শাস্তার জনবসতি পড়ে থাকে। প্রথম তিন ঘণ্টা পাওলোর সঙ্গে পাল্লা দিয়ে চলতে পারলেও শেষ ঘণ্টায় পিছিয়ে পড়লাম। পাওলো ভাবল আমি তার পেছন পেছন ঠিকমতোই আসছি, তাই সে না থেমে এগিয়ে যেতে থাকল। এইভাবে ধীরে ধীরে সে আমার চোখের আড়ালে চলে গেল।
অ্যাভালেঞ্চ খাঁড়ি শেষ হয়েছে একটা লালচে পাথরের রেখার সীমানায়, যাকে রেড ব্যাংক্স বলা হয়। তবে রেড ব্যাংক্সে পৌঁছাতে হলে প্রায় পাঁচশো ফুট খুব খাড়াই উচ্চতার একটা সংকীর্ণ গিরিখাতের মধ্য দিয়ে ওপরে উঠতে হয়। সেই গিরিখাত ছোট-বড়-মাঝারি সব ধরনের পাথরে পূর্ণ। হাতের বরফ-গাঁইতি ও পায়ের ক্রাম্পন খুলে পেছনের ব্যাগে ঢোকাই, পাথরের ওপর কাঁটাওয়ালা ক্রাম্পন কাজে লাগবে না। খুব সন্তর্পণে একটা পাথর থেকে আর একটা পাথরে পা ফেলে ফেলে উঠতে থাকি। ভারসাম্য রাখতে দু-হাত দু-দিকে মেলে ধরি। বলতে কোনও দ্বিধা নেই যে পাওলোকে না দেখতে পেয়ে এই সময়ে আমি একটু ঘাবড়ে গিয়েছিলাম। মূল অ্যাভালেঞ্চ গালচ পাড়ি দিতে আমার তেমন কোনও ভয় করেনি, কিন্তু এখন পাথর থেকে পাথরে পা ফেলতে বেশ অসহায় লাগছিল।
এর মধ্যে ওপর দিকে তাকিয়ে দেখি রেড ব্যাংক্স ঘন কুয়াশায় ঢেকে গেছে। কুয়াশা অর্থাৎ মেঘ। কিন্তু এই কয়েক মিনিট আগেও আকাশে মেঘের চিহ্ন ছিল না, তবে আমি পাহাড়ের অন্যপাশটা দেখতে পাচ্ছিলাম না, ওইদিকে কি মেঘ জমছে? ওপরের কুয়াশা দেখতে দেখতেই আমি অসাবধানে ডান পা-টা একটা পাথরের ওপর রাখি। সেটা রাখামাত্র পাথরটা টলে গেল, আর আমার ডান পা পিছলে গিয়ে দুটো পাথরের মধ্যে ঢুকে গেল। আমার গলা দিয়ে একটা অস্ফুট আর্তনাদ বের হয়, ‘আঃ!’ আমার পা-টা হয়তো ছড়ে গিয়েছিল, কিন্তু পরক্ষণেই বুঝলাম ব্যাপারটা একটু গুরুতর, কারণ আমার ডান পা হাঁটু পর্যন্ত তিনটে পাথরের সীমানায় আটকে গেছে।
কেউ কোথাও নেই, আমি দুটো হাত দুটো পাথরের ওপর ভর দিয়ে শরীরকে ওপর দিকে টানতে চাই, পা-টা পায়ের পাতা পর্যন্ত ওঠে, কিন্তু পুরু বুটজুতো তিনটে পাথরের মাঝখানের ফাঁকা জায়গায় আটকে যায়। আমি অসহায় হয়ে ওপরের দিকে তাকাই। ওপর থেকে কুয়াশা আরও নীচে নেমে আসে। পাওলো কোথায় এখন? ভাবলাম চিৎকার করে পাওলোকে ডাকব, যদিও জানতাম পাওলো সেটা শুনতে পাবে না। এ রকমভাবে মনে হল মিনিট দশেক গেল, আসলে এখন বুঝছি যে খুব বেশি হলে মিনিট দুইয়ের বেশি সময় যায়নি যখন হঠাৎ ওপরের ঘন কুয়াশা থেকে একজন বের হয়ে আসে। সেই মানুষটি নীচে নামছিল পেছন ফিরে। সে ছিল পুরুষ, তার গায়ে ছিল লাল জ্যাকেট আর সবুজ প্যান্ট। সেই পেছন ফিরে নামার ভঙ্গিটা এমনই অদ্ভুত ছিল যে সেটা প্রথমেই আমার মনে দাগ কাটে। কিন্তু তবুও স্বস্তি পাই, যাক, একজনকে পাওয়া গেল, পাহাড়ে সবাই সবার বন্ধু, এখানে কেউ কাউকে ফেলে চলে যায় না।
লোকটিকে আমি এক দৃষ্টিতে দেখতে থাকি। সে খাড়াই পাথুরে পথ নীচের দিকে না তাকিয়েই নামছে, এমন যেন সে আগে থেকেই জানে কোন পাথরটা কোথায় আছে, কোথায় পা দিতে হবে। সে কি পরীক্ষা করছে নীচের দিকে না তাকিয়ে নামা যায় কি না? কিন্তু কোনও পর্বতারোহীই সেটা করবে না। যে-কোনও মুহূর্তেই পা হড়কাতে পারে, আর এখানে একবার পা ছুটে গেলে পাঁচশো ফুট ধরে গড়িয়ে নীচে পড়ে মৃত্যু অবধারিত। প্রার্থনা করতে থাকলাম সে যেন সব কিছু সামলে আমি যেখানে আছি সেখান পর্যন্ত ভালোমতো পৌঁছাতে পারে, তার সাহায্য আমার খুবই প্রয়োজন। এইরকম সাত-পাঁচ ভাবছি, তখন আমার থেকে তার দূরত্ব মাত্র বিশ-পঁচিশ হাত হবে, সে মুখ ফিরিয়ে নীচের দিকে তাকাল।
তার মুখ দেখে আমার হৃৎপিণ্ড বন্ধ হয়ে গেল। যেন একটা প্রবল ব্রেক কষে কয়লার রেল ইঞ্জিন থেমে গেল— ধক। তারপর ইঞ্জিন একশো মাইল গতিতে চলল, খুব দ্রুতগতিতে হৃৎপিণ্ড খুলল, বন্ধ হল, খুলল, বন্ধ হল, ধক ধক ধক ধক। আমার মতো, তার মুখ আমার মতো। তার গায়ের রং, চলার ভঙ্গি আমার মতোই ছিল। গায়ের লাল কলাম্বিয়া কোম্পানির জ্যাকেট আর চেন-দেওয়া পকেট নিয়ে বাংলাদেশে তৈরি সবুজ পলিয়েস্টারের প্যান্ট— সেগুলো তো আমিই পরে ছিলাম।
আমিই যেন অদ্ভুতভাবে নীচে নামছি। সে আবার মুখ ঘুরিয়ে নীচের দিকে তাকাল, এবার বুঝলাম লোকটি নীচে পাহাড়ের দিকে তাকাচ্ছিল না, বরং যেন আমাকেই দেখার চেষ্টা করছিল। কিন্তু পাহাড়ে যে রকম সামাজিক নিয়ম সে রকম ‘হ্যালো’ বা ‘হাই’ কিছুই বলল না। আরও দশ ফুট নীচে নামল সে, সোজাসুজি আমার দিকে তাকাল। এমন যেন সে জানত আমাকে সে এইখানে দেখবে। কিন্তু তার মুখে এক ধরনের বিভ্রান্তি ছিল। এই তাকানোর ভঙ্গিটা আমার এত পরিচিত। আয়নাতে যেমন আমি নিজের মুখ দেখতে পছন্দ করি না, হঠাৎ চোখ পড়লে সরিয়ে নিই, সে রকম। সে যেন আমার উপস্থিতির কথা জানে, তবুও যেন খুব অনিচ্ছাসহকারে দেখতে হচ্ছে। এমন একটা মুহূর্ত যে আসবে সেটা সে যেমন জানত, সেই সাক্ষাৎ সম্মেলন থেকে ফলপ্রসূ কিছু পাওয়া যাবে না, সেই বোধটাও যেন তার চোখে ব্যক্ত ছিল।
সে মাথা ঘুরিয়ে নিয়ে আবার নামতে শুরু করে। দ্রুত। আমি পা আটকে যেখানে দাঁড়িয়ে আছি, ঠিক সেদিকেই নেমে আসতে থাকে। এমন যেন এই চলার ওপর তার কোনও হাত নেই, সে যেন বাধ্য এই পথে ওই রকমভাবে চলতে। কোনও পর্বতারোহীই এ রকম পাগলামো করবে না। তার কি মাথা খারাপ হয়ে গেছে? কিন্তু এসব ভাবার বেশি সময় নেই। আমি প্রাণপণে পা-টাকে ওপরে টানতে থাকি, আর সে যখন ঠিক আমার ওপরে এসে পড়বে তখন শেষ মুহূর্তে পা-টা পাথরের ফাটল থেকে বের হয়ে আসে। আমি কোনওরকমে দু-হাতে ভর দিয়ে শরীরটাকে টেনে ডান দিকের একটা পাথরের ওপর ডান পায়ে ভর করে লাফ দিয়ে তার পথ থেকে সরে যেতে পারি। যে মুহূর্তে আমি সরে যাই সেই মুহূর্তে সে আমার পূর্বতন জায়গায় তার ডান পা-টা রাখে।
আমার প্রতিলিপি ভারসাম্য রাখতে পারে না, তার পা— আমার পা যে-ফাটলে আটকে গিয়েছিল সেখানেই পড়ে, আমি একটা অদ্ভুত গা-কাঁটা দেওয়া অস্ফুট আওয়াজ শুনি। সে ওপরে আমার দিকে তাকায়, কিন্তু আমাকে যেন দেখেও দেখে না। আমি তাকে নীচে নেমে সাহায্য করার কথা ভাবি, কিন্তু সেই মুহূর্তে ওপরের কুয়াশা নেমে আসে আরও ঘন হয়ে, মাত্র পাঁচ হাত নীচে আমার প্রতিলিপিকে ঢেকে দেয়।
কুয়াশা সবকিছু ঢেকে দেয়। আমি একটা টলায়মান পাথরের ওপর দাঁড়িয়ে থাকি, কুয়াশা একটা ঘন অস্বচ্ছ দেয়াল সৃষ্টি করে আমাকে ঘিরে রাখে। কোনওদিকে পা ফেলার উপায় নেই। আমার একটু নীচে আমার সেই প্রতিলিপি কী করছে, সেটাও জানার উপায় ছিল না। আমি চিৎকার করে তাকে ডাকি, ‘এই যে, শুনতে পাচ্ছেন?’ প্রথমে ইংরেজিতে, তারপর বাংলায়। আবার বলি, ‘আপনি কি আঘাত পেয়েছেন? উত্তর দিন, আমি আপনার আওয়াজ শুনে নীচে নামতে পারি। আমি আপনাকে সাহায্য করতে পারি।’ আমি একবার যেন তার কথা শুনতে পাই, কিন্তু সেটা একেবারেই অবোধ্য একটা যেন কিছু, একটা টেপ বা রেকর্ড উলটো করে চালালে যেমন মোচড়ানো, কষ্টকর, দুর্বোধ্য শব্দ বের হয়— সে রকম। তারপর নীচ থেকে আর কোনও আওয়াজ শুনি না।
কাল রাতের হাওয়া, বৃষ্টি, বজ্র আজ সকালে মিলিয়ে গিয়েছিল এক সুনীল সূর্যকরোজ্জ্বল আকাশে। আমরা হেলেন লেক থেকে রওনা দিয়েছিলাম আনন্দে, নতুন আশা নিয়ে। কিন্তু কুয়াশার এই নিঃশব্দ ফেনিল দুর্গে সেই আশা পরিণত হয়েছে চরম অসহায়ত্বে। সময় কীভাবে প্রবাহিত হচ্ছে তার ধারণাও হারিয়ে গিয়েছিল, কিন্তু মনে হল এভাবে প্রায় আধঘণ্টা কাটল। তারপর কুয়াশাটা অল্প অল্প করে হালকা হল। কিন্তু নীচের দিকে তাকিয়ে আমি তাকে আর দেখতে পেলাম না। তা হলে সে তার পা-টা পাথরের ফাটল থেকে মুক্ত করতে পেরেছে। কিন্তু তারপর? এই ঘন কুয়াশায় সে কেমন করে নীচে নামছে? নাকি পা হড়কে পাথরের ওপর বরফের পিছল আস্তরণের ওপর দিয়ে পড়ে গেছে বহু নীচে? এমন একটা অদ্ভুত ব্যাপার, সমুদ্রপৃষ্ঠ থেকে তেরো হাজার ফুট ওপরে আমি যেন দ্বিতীয় অমলের সাক্ষাৎ পেলাম। এর কী অর্থ হতে পারে?
কিন্তু আমার পক্ষে এই জায়গায় আর দাঁড়িয়ে থাকা সম্ভব নয়। বাতাস ঠান্ডা হয়ে আসে। আমাকে এই কুয়াশার মধ্যেই ওপরে উঠতে হবে। কিছুটা ঘোরের মধ্যেই ওপরে উঠতে থাকি, অনেকটা আন্দাজেই একটা পাথর থেকে অন্য একটি পাথরের ওপর পা ফেলি। আধঘণ্টা পরে চড়াই ঢাল কিছুটা সমতল হয়, কিন্তু রেড ব্যাংক্সের লাল আস্তরণ খুঁজে পাই না। কুয়াশা আমাকে শাস্তার চূড়া দেখতে দেয় না, পাওলোকেও খুঁজে পাই না। আমি চিৎকার করি, ‘পাওলো, পাওলো!’ কেউ উত্তর দেয় না। আমি জানতাম রেড ব্যাংক্স পার হলে শাস্তার মাথা মাত্র মাইলখানেক পথ উত্তর-পশ্চিমে, খুব একটা চড়াইও নয়। পকেট থেকে কম্পাস বের করি, কম্পাস দেখে উত্তর-পশ্চিম দিকে এগোতে থাকি। কুয়াশা আবার ঘন হয়ে চেপে বসে, শাস্তায় এই সময়ে কুয়াশা হবার কথা নয়।
আমার মনে ঝড় বইতে থাকে, শ্রান্ত শরীর অশান্ত মনে পা ফেলে। ডান পা-টার চামড়া নিশ্চয় সেই ফাটলে পড়ে ছড়ে গেছে, সেখানে একটা চিনচিন ব্যথা তীক্ষ্ণ থেকে তীক্ষ্ণতর হয়ে ওঠে। তার মধ্যেও আমি গত কয়েক ঘণ্টার ঘটনাবলির খতিয়ান করতে থাকি। পাহাড় থেকে অদ্ভুতভাবে যে মানুষটি নেমে আসছিল, সে কি আমিই? দ্বিতীয় অমল— যে কিনা প্রথম অমল যা করেছে তারই পুনরাবৃত্তি করছিল উলটোভাবে। এমন যেন তার সময় বইছিল আমার সময়ের বিপরীতে।
এই রকম অসম্ভব সব ঘটনার সম্ভাবনা আমার যৌক্তিক চিন্তাধারার স্রোতকে এলোমেলো করে দেয়, আমি আর কিছু ভাবতে পারি না। কুয়াশার মধ্যে অন্ধের মতো চলি একটা পাথর থেকে আর একটা পাথরে পা ফেলে খুব সন্তর্পণে। কতক্ষণ চলি তার হিসাব রাখতে পারি না, হঠাৎ করেই সামনে একটা পাথরের খাড়া দেয়ালে পা পড়ে। এইখানে তো এ রকম কোনও উঁচু জায়গা থাকবার কথা নয়! দেয়ালটা দেখা যায় না, আমি হাত দিয়ে সেটার পিঠ স্পর্শ করি। একেবারে মসৃণ তল, আগ্নেয়গিরির উদগীরণে জমে যেন সৃষ্টি হয়েছে লাভার পাহাড়। কিন্তু শাস্তার মাথায় কোনও লাভার উঁচু পাহাড় থাকার কথা নয়। আমি যেন অন্য কোনও পাহাড়ের চূড়ায় অলৌকিকভাবে আবির্ভূত হয়েছি। দেয়ালটা ধরে আরও কিছুক্ষণ এগোতে থাকি। এ রকমভাবে আরও মিনিট দশেক কেটে যায়। হঠাৎ হাত পড়ে একটা ফাঁকা জায়গায়। দেয়ালের মধ্যেই একটা মানুষ-সমান ফাটল, যার ভেতরে হালকা লাল আভা দেখা যায়। গুহা? মাউন্ট শাস্তার মাথায় এ রকম কোনও কিছুই থাকার কথা নয়। আমি গুহার ভেতরে ঢুকি।
গুহার ভেতরে কোনও কুয়াশা নেই। গুহাটা খুব বড় ছিল না, দৈর্ঘ্যে-প্রস্থে খুব বেশি হলে দশ-বারো হাত, কিন্তু তার একদিকে আর একটা লম্বালম্বি ফাটল ছিল, যেখান থেকে লাল আভা বের হচ্ছিল। আমি সেদিকে এগোই, তারপর কোনও দ্বিধা ছাড়াই সেই ফাটলে ঢুকি শরীরটাকে আড়াআড়ি করে। মাথা নীচু করে হাঁটতে হয়, লাল আলোটা আরও তীব্র হয়, বাতাস আরও গরম হয়ে ওঠে। কুড়ি-পঁচিশ হাত গিয়ে সুড়ঙ্গটা শেষ হয়ে যায়। একদম শেষে সুড়ঙ্গের ছাদটা নীচে নেমে আসে, আমাকে হামাগুড়ি দিয়ে এগোতে হয়। সুড়ঙ্গ শেষে মাথা বের করে দেখি আর একটা গুহা, তবে সেটা ছিল একটা বিশাল গুহা, তার শেষ দেখা যাচ্ছিল না। গুহার ঠিক মাঝখানে একটা বিশাল গহ্বর। তার থেকে বাষ্প বের হচ্ছে, লাল রঙের বাষ্প। সারা গুহাটাই সেই গহ্বর থেকে নির্গত লাল আলোয় রাঙা হয়েছিল।
সুড়ঙ্গের মুখটা মাটি থেকে কয়েক ফুট ওপরে। আমি লাফ দিয়ে নীচে নেমে সেই গহ্বরে দিকে এগোই। তার পাশে এসে নীচে তাকিয়ে দেখি গভীর গহ্বর, প্রায় দুশো ফুট নীচে গলন্ত লাভা তার লাল রং নিয়ে স্থিত হয়ে আছে। আমি নিশ্চিত হলাম আমি শাস্তা পাহাড়ে আর নেই, সেই পাহাড়ে শেষ অগ্ন্যুৎপাত হয়েছিল ১৭৮৬ সনে আর অগ্ন্যুৎপাতের পর্যায়কাল প্রায় ৬০০ বছর। শাস্তা পাহাড় এখন একেবারেই শান্ত।
গরমে ঘামতে থাকি। একটা পাথরের ওপর বসি। গুহাটা লাভার রক্তিম আলোতে একটা অপার্থিব রূপ নেয়। এবার গুছিয়ে চিন্তা করার পালা। প্রথমত, পাওলোকে একেবারে হারিয়ে ফেরার কোনও কারণ আমি দেখি না, আমি পেছনে নেই দেখে পাওলোর ফিরে আসার কথা। দ্বিতীয়ত, এই মেঘমুক্ত সকালে হঠাৎ কুয়াশা বা মেঘের সৃষ্টি হবার কথা নয় এবং যার কোনও ধরনের ব্যাখ্যা আমি করতে পারছি না। তৃতীয়ত, আমার এক প্রতিলিপির আবির্ভাব, শুধু আবির্ভূত হয়েই সে আমাকে চমকে দেয়নি, তার প্রতিটি ভঙ্গি ছিল যেন আমার কৃত ভঙ্গির প্রতিরূপ। সময়ের সম্মুখগতির বিপরীত দিকে প্রতিফলন, একটি চলচ্চিত্রকে যখন উলটোদিকে চালানো হয় সে রকম। এর নিশ্চয় কোনও যৌক্তিক ব্যাখ্যা আছে। আমার হ্যালুসিনেশন হচ্ছে। ক্লান্ত শরীরে, পাহাড়ের হালকা বায়ুতে মস্তিষ্কের ভারসাম্য নষ্ট হয়েছে। সেই উন্মত্ত মস্তিষ্ক আমার dopplegangar-এর আবির্ভাব ঘটিয়েছে। ডপলগ্যাংগার একটি জার্মান শব্দ, যার মানে হচ্ছে ভৌতিক প্রতিলিপি; যে কিনা কোনও অশুভ উদ্দেশ্যে পৃথিবীতে দেখা দেয়। তা ছাড়া আমি শুনেছি স্কিৎসোফ্রেনিয়ার রোগীরা নাকি নিজেদেরকে দূর থেকে দেখতে পায়। আমার স্কিৎসোফ্রেনিয়া নেই, আর আমি ডপলগ্যাংগারে বিশ্বাস করি না। চতুর্থত, পাহাড়ের ওপর এই লাভাকুণ্ডের আবিষ্কার।
ধীরে ধীরে আর একটি সম্ভাবনার কথা আমার মাথায় আসে। আমার সময় ছেড়ে আমি অন্য একটি সময়ের স্রোতধারায় প্রবেশ করছি। কুয়াশাটা যখন ওপর থেকে নেমে আসে তখন। শুধু যে অন্য সময়ে প্রবেশ করেছি তাই নয়, অন্য কোনও স্থানে বা দেশে আমি আবির্ভূত হয়েছি। দুই সময়ের বা দেশের সীমানায় আমি ক্ষণিকের জন্য আমার প্রতিলিপিকে দেখেছি। সেই প্রতিলিপির জন্য সময় উলটোদিকে প্রবাহিত হচ্ছিল। আমি তাকে দ্বিতীয় অমল নাম দিলাম।
কিন্তু তার সময় বিপরীত দিকে বইলেও সেই প্রতিলিপি বুঝতে পারছিল না যে তার জন্য সময়ের প্রকৃতি ভিন্ন ছিল। আমার মনে হল, তার রেফারেন্স কাঠামোয় ভবিষ্যৎ ক্রমাগতই মুছে যাচ্ছিল। তার পা যখন পাথরের ফাটলে আটকে গেল, ততক্ষণে সে যে কিছুক্ষণ আগেই ওপর থেকে নেমে এসেছে সেই স্মৃতি তার মন থেকে মুছে গিয়েছিল। বরং তখন সে মনে করছিল ‘আমাকে এখন পা-টা ফাটল থেকে উদ্ধার করে ওপরে উঠতে হবে।’ আর সে যখন নামছিল তার মুখ দেখে মনে হয়েছিল এই পাহাড়ে তার সঙ্গে যে আমার সাক্ষাৎ হয়েছিল সেটা সে জানত, কিন্তু আমাকে পার হয়ে নীচে যাবার পরে সেই স্মৃতি তার মন থেকে মুছে গিয়েছিল। তার কাছে প্রতিটি মুহূর্ত ছিল বাস্তব, কিন্তু পরের মুহূর্তটি তাকে অতীতে নিয়ে যাচ্ছে আগের মুহূর্তটিকে বিলীন করে দিয়ে। ধীরে ধীরে আমার এই বোধটি হল যে আমার প্রতিলিপির কোনও স্বাধীন ইচ্ছা নেই। পৃথিবীর পথে আমি যা করেছি, যে পথে চলেছি— তা-ই করতে, সেই পথে চলতে দ্বিতীয় অমল বাধ্য। কিন্তু এই বোধটি তার নেই। ধীরে ধীরে তার যে বয়স কমছে, সেটা জানার তার কোনও উপায় নেই। সে মনে করছিল তার স্বাধীন চিন্তা বা free will আছে, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তা ছিল না।
এক বিশাল বেদনাবোধে আমার প্রতিলিপির জন্য আমার মন বিষাদে আচ্ছন্ন হয়ে যায়। তারপর বুঝি এই পাহাড়, এই গুহা থেকে আমার মুক্তি নেই। আমি আমার ভবিষ্যৎ দেখেছি। আমার ভবিষ্যৎ হল আমার অতীত। সেই অতীত হয়তো শুরু হয়ে গেছে এর মধ্যেই। সেটা আমার বোঝার উপায় নেই। এই নতুন সময়ের স্রোত আমার অতীতকে মুছে দিতে থাকবে, যা কিনা ছিল দ্বিতীয় অমলের ভবিষ্যৎ। তবু সবকিছু মুছে যাবার আগে আমার এই অভিজ্ঞতাকে লিপিবদ্ধ করা দরকার, জীবনের এই ইউ-টার্নকে পৃথিবীকে জানানো দরকার, আমার প্রিয়জনদের জানানো দরকার। আমি ব্যাকপ্যাক থেকে আমার ডায়েরি বের করি, ডায়েরির সঙ্গে লাগানো কলমটা খুলে নিয়ে লিখতে আরম্ভ করি। আমি জানি না এই লেখা পাঠকদের কাছে পৌঁছাবে কি না। কিন্তু আপনারা যে এটা পড়ছেন তার মানেই হল এই ডায়েরিটা উদ্ধার করা গেছে। আমার পক্ষে সেটা অবশ্যই আর জানার উপায় নেই। শুধু জানবেন যে এই লেখা যে লিখেছে তার এক প্রতিলিপি কার্যকারণের অমোঘ চক্রে দেশ-কালের নিশ্চিত রেখায় সময়ের বিপরীতে চলছে। এই মহাবিশ্বকে সে কীভাবে দেখছে? তার অনুভূতির কি আলাদা কোনও মূল্য আছে?
আর আপনারা যারা এই লেখাটা পড়ছেন তাঁদের আমি অনুরোধ করব একটু থেমে আপনার দেয়ালে যদি কোনও ঘড়ি থাকে তার দিকে তাকাতে। আপনি কি নিঃসন্দেহ ঘড়ির কাঁটা সামনের দিকে চলছে? আপনি কি নিঃসন্দেহ যে আপনার জীবন ভবিষ্যৎমুখী? আপনি কি নিঃসন্দেহ যে এই লেখাটা আপনি আগে পড়েননি? নাকি আপনার হাতে গড়া সমস্ত ভবিষ্যৎ আর এক মহাবিশ্বের এক নিষ্ঠুর কালচক্রে ক্রমাগতই বিলীন হয়ে যাচ্ছে? হয়তো বেশির ভাগ পাঠকই এই লেখাকে পাগলের প্রলাপ বলে উড়িয়ে দেবেন, তবু তার মাঝে হয়তো একজন কি দুজন পাওয়া যাবে, যাদের মস্তিষ্কের সুপ্ত নিউরোনসমষ্টি হয়তো ধরে রেখেছে একটা আবছায়া স্মৃতি, হয়তো এই কাহিনিটিকে পূর্বে পড়ার স্মৃতি, হয়তো-বা তাদের হারিয়ে যাওয়া বার্ধক্য বা পৌঢ়ত্বের স্মৃতি। আমি তাঁদের অনুরোধ করব, আমার দেওয়া পাওলোর ই-মেইল ঠিকানায় তাঁদের কথাটা লিখে জানাতে। মহাবিশ্বের নির্মোহ সময়চক্রের পাঠোদ্ধার করতে হলে মানুষের স্মৃতির ক্রমান্বয় গাঁথাই একমাত্র পরিত্রাণ। সেই গাঁথায় যোগ দিতে পাঠকদের আমন্ত্রণ জানিয়ে আমি বিদায় নিচ্ছি।
পাওলোর কথা
আমার নাম পাওলো সিয়ুং, আমি অমলের বন্ধু। সেদিন শাস্তা পাহাড়ে আরোহণের সময় আমি অমল থেকে মাত্র কয়েক মিনিট এগিয়ে ছিলাম। রেড ব্যাংক্স দিয়ে ওঠার সময়ও আমি পেছনে তাকিয়ে দেখেছিলাম অমল বেশ ভালোভাবে উঠে আসছে। আমি ভেবেছিলাম তাড়াতাড়ি উঠে ওপর থেকে অমলের কয়েকটি ছবি তুলব। তাই দ্রুত পাথর থেকে পাথরে পা ফেলে উঠে এলাম, পাঁচ মিনিট সময়ও লাগল না। কিন্তু পেছন ফিরে অমলকে আর দেখতে পেলাম না। প্রথমে ভাবলাম কোনও বড় পাথরের আড়ালে পড়েছে, এখনই বেরিয়ে আসবে। এইভাবে প্রায় দশ মিনিট পার হয়ে গেলে খুব চিন্তা হল। আবার নীচে নেমে এলাম, এখান থেকে অমল গড়িয়ে পড়লেও তাকে দেখা যাবে। কিন্তু সেই সকালে, সুনসান অ্যাভালেঞ্চ গালচের শুভ্র তুষার-বরফের সমতল ঢালে একটি প্রাণীও ছিল না। আমি চিৎকার করলাম, ‘অমল, অমল!’ আমার ডাক প্রতিধ্বনিত হল বহু নীচের উঁচু জায়গায়গুলো থেকে— অমল… অমল…। তারপর ভাবলাম অমল পাশের আর একটি ছোট গিরিখাত দিয়ে হয়তো ওপরে উঠে গেছে। সেটাতে পৌঁছাতে পৌঁছাতে মিনিট পনেরো গেল, আর সেটা দিয়ে ওপরে উঠতে আরও আধঘণ্টা। রেড ব্যাংক্সের ওপরে কিছু জায়গা সমতল। এখান থেকে শাস্তার চূড়ায় ওঠা সহজ, ঘণ্টাখানেকের পথ। অমল কি এদিক দিয়ে উঠে আমাকে না দেখতে পেয়ে নিজেই চূড়ার দিকে রওনা হয়েছে?
অনেক নীচে এবার দেখলাম দুজন পর্বতারোহী উঠে আসছে। আমি তাদের জন্য বসে রইলাম। তাদের উঠে আসতে ঘণ্টাখানেক লাগল। আমি তাদের অমলের বর্ণনা দিলাম, তারা অমলকে নামতে দেখেনি। সেই পর্বতারোহীরাও চিন্তিত হল, পাহাড়ে সবাই সবার হিতাকাঙ্ক্ষী। আমি তাদের এগিয়ে যেতে বলে আরও কিছুক্ষণ রেড ব্যাংক্সের ওপর ঘোরাঘুরি করতে থাকলাম।
উধাও, উধাও, উধাও। আমার মাথা খারাপ হয়ে গেল। অমল, তুমি কোথায়? এ রকম সুন্দর একটা সকালে যখন দেড়শো মাইল দূরে দিগন্ত আর সত্তর মাইল দূরে দেখা যাচ্ছে মাউন্ট লাসেনের চূড়া, যেখানে অ্যাভালেঞ্চ গিরিখাতের প্রতিটি কোনা দেখা যাচ্ছে, সেখানে আমি অমলকে হারিয়ে ফেললাম। কীভাবে এটা হল? ক্ষোভে, দুঃখে মুহ্যমান হয়ে রইলাম। তারপর ভাবলাম অমল হয়তো অনেকক্ষণ আগেই উঠে এসেছে, তারপর চূড়ার দিকে রওনা হয়ে গেছে। তাই আমিও সেদিকে রওনা দিলাম। ঘণ্টাখানেক লাগল সবচেয়ে উঁচু জায়গাটায় পৌঁছাতে। সেখানে গিয়ে দেখি সেই আগের দুজন পর্বতারোহী বসে দুপুরের খাবার খাচ্ছে, অমলের সাক্ষাৎ তারা পায়নি।
আমার তখন করার আর কিছু ছিল না, দ্রুত নীচে নেমে অনুসন্ধান পার্টিকে খবর দিতে হবে। আমার সঙ্গে সেই দুজন পর্বতারোহীও নেমে এল। রেড ব্যাংক্স পার হয়ে তুষার ও বরফের ওপর বসে পিছল খেয়ে খেয়ে খুব অল্প সময়েই হেলেন লেকে পৌঁছে গেলাম। তবু সব মিলিয়ে পাঁচ ঘণ্টা লাগল নীচে নামতে। বলাই বাহুল্য, এর মধ্যে অমলের সাক্ষাৎ পেলাম না কোথাও। গাড়ি নিয়ে শাস্তা শহরে পৌঁছাতে আরও আধঘণ্টা। সন্ধ্যা হয়ে গেছে তখন। রেঞ্জার স্টেশন বন্ধ। পুলিশে ফোন করলাম, তারা সার্চ ও রেসকিউ পার্টির নম্বর দিল। সার্চ আর রেসকিউ বলল রাতে অনুসন্ধান করা যাবে না, সকাল ছ-টায় রেঞ্জার স্টেশনের সামনে দেখা করতে বলল।
পরের দিন অনুসন্ধান পার্টির সঙ্গে আবার ফিরে গেলাম পাহাড়ে। পুরো তিন দিন সেখানে ছিলাম আমি। হেলিকপ্টার ডাকা হল, পাহাড়ের চারদিকে ঘুরেও অমলের কোনও চিহ্ন পাওয়া গেল না। শাস্তার চূড়ার কাছাকাছি জায়গা খুব উন্মুক্ত, মৃত হোক জীবিত হোক অমলকে পাওয়া যাবার কথা ছিল। একটি জিনিস অবশ্য পাওয়া গেল। অ্যাভালঞ্চে গালচ দিয়ে আমরা উঠছিলাম। কিন্তু তার পুরোপুরি উলটোদিকে পাহাড়ের উত্তর-পশ্চিম দিকে যেখানে দু-একটা ছোটখাটো হিমবাহ আছে, তার ঢালুতে অমলের ডায়েরিটা পাওয়া গেল। অমলের লেখা পড়ে আমরা সবাই অবাক হয়েছিলাম। পাহাড়ের ওপর সেদিন কোনও কুয়াশা ছিল না, আর কোনও লাভার কুণ্ড থাকার তো প্রশ্নই আসে না। তদুপরি অমলের মতো দেখতে আর কাউকেই সেদিন পাহাড়ে দেখা যায়নি। কিন্তু ডায়েরির মলাটটা আধাপোড়া ছিল। সবচেয়ে আশ্চর্যের কথা, বন বিভাগ ডায়েরিটা পরীক্ষা করে মলাটে আগ্নেয়গিরির ছাই আবিষ্কার করেছিল।
ডায়েরিটা আমাকে কর্তৃপক্ষ দেয় অমলের বাড়িতে পৌঁছে দেবার জন্য। কিন্তু সেটা ফেরত দেবার আগে আমি তার একটা কপি করে নিই নিজের জন্য। অমল যেভাবে তার প্রতিলিপিকে বর্ণনা করেছে, পাহাড়ের কুয়াশা, সেই গুহা, উত্তপ্ত লাল লাভাকুণ্ড সেগুলি যে একেবারেই মনগড়া, সেটা বিশ্বাস করতে কষ্ট হল। অমলকে আমি অনেক বছর ধরে চিনি, সে জীবনকে খুব সিরিয়াসভাবে নিয়েছিল, সে কোনও ছলনার আশ্রয় নেবে না বলেই আমার বিশ্বাস। আর ডায়েরির শেষ কয়েকটা পাতা যে সেদিনই লেখা এ বিষয়ে আমি নিঃসন্দেহ ছিলাম। এর দু-দিন আগেই শাস্তার হোটেলে বসে সে এই ডায়েরিতে আমাদের সেদিনের গাড়িতে আসার বর্ণনা দিয়েছিল, হেলেন লেকের কথা লিখেছিল। এ ছাড়া ডায়েরির মলাটে আগ্নেয়গিরির অগ্ন্যুৎপাতের নিদর্শন পাওয়া গিয়েছিল। অমল যে একটি জীবন্ত আগ্নেয়গিরির ওপর বসে ছিল, তার বর্ণনা তো সে দিয়েই গিয়েছে।
আমি খুব মনোযোগ দিয়ে ডায়েরির শেষ কয়েকটা পাতা পড়ি। অমল তার প্রতিলিপির প্রতিটি ভঙ্গি খুব সতর্কতার সঙ্গে লিপিবদ্ধ করেছে। দ্বিতীয় অমল প্রতিটি মুহূর্তে পেছনে চলে যাচ্ছিল, সে যেন প্রথম অমলের প্রতিটি ভঙ্গির পুনরাবৃত্তি করছিল সময়ের উলটো দিকে। দ্বিতীয় অমলের কোনও স্বাধীন চিন্তা ছিল না, কিন্তু সেটা নিজে সে উপলব্ধি করতে পারছিল না। দেখলাম অমল আমার ই-মেইল ঠিকানাটা দিয়েছে। অমল কিছু একটা বুঝতে পেরেছিল, কী পেরেছিল সেটা সম্বন্ধে আমি নিশ্চিত হতে চাই। অমল জানত যে সে অন্য একটি সময়ের স্রোতে ঢুকছে, যে স্রোত আমাদের সময়ের বিপরীত দিকে বইছে, সেই স্রোত তাকে নিয়ে যাবে আর একটি দেশ-কালে, যার সঙ্গে আমার দেশ-কালের ছেদ হবে না কোনওদিন।
সত্যিই কি তাই? হঠাৎ আমার মাথায় একটা চিন্তা আসে। অমল রেড ব্যাংক্সে উঠে আসার আগে তার প্রতিলিপিকে দেখে। কিন্তু অমল নিশ্চয় আর রেড ব্যাংক্সে ওঠেনি, সে ইতিমধ্যে অন্য কোনও স্থান ও সময়ে চলে গিয়েছিল। সেই স্থান ছিল কুয়াশায় ঢাকা, সেখানে ছিল একটি গুহা, লাভাকুণ্ড। সেই গুহায় বসে সে সময়ের পেছন দিকে যেতে আরম্ভ করে, দ্বিতীয় অমলে রূপান্তরিত হয়। আর সেই রূপান্তর ও দ্বিতীয় অমলের পা খাদে পড়ার মধ্যে কতখানি সময় গিয়েছে? পাঁচ ঘণ্টা, ছয় ঘণ্টা? জানি না, সময়ের হিসাব এখানে রাখা মুশকিল। কুয়াশার মধ্যে বা গুহার সময়ের প্রবাহ কত দ্রুত, সে সম্বন্ধে আমরা তো কোনও ধারণা করতে পারি না।
কিন্তু আমি যদি দ্বিতীয় অমলের পথকে ব্যাকট্র্যাক করতে পারি, ভবিষ্যতে দ্বিতীয় অমলের আবির্ভাবের সময়গুলো এক্সট্রাপলেট করতে পারি তা হলে কি তার সঙ্গে আমার দেখা হবে? চারদিন আগে তার কোথায় থাকার কথা ছিল? এক সপ্তাহ আগে? পরের কয়েকটা দিন আমি চেষ্টা করলাম মনে করতে অমলের সঙ্গে আমার কোথায় কোথায় দেখা হয়েছে এর আগে। আমরা একসঙ্গে হেঁটেছি ক্যালিফোর্নিয়ার সিয়েরা নেভেডা পাহাড়ে, মেইন আর নিউ হ্যাম্পশায়ারের আপালাচিয়া পাহাড়ে, সুইজারল্যান্ডের আলপসে। কবে কোথায় আমরা একসঙ্গে ছিলাম, সেটা একটা খাতায় লিখতে আরম্ভ করি। সিয়েরা নেভাডা পাহাড়ে আমরা চার বছর আগে গিয়েছিলাম, যদি দ্বিতীয় অমলের সময় এই পৃথিবীর মতো একই গতিতে (কিন্তু পশ্চাৎ দিকে) বহমান হয়, তবে আজ থেকে চার বছর পরে সে সিয়েরাতে দেখা দেবে।
দেখা দেবে কি?
দ্বিতীয় অমল প্রথম অমলকে ক্ষণিকের জন্য দেখা দিয়েছিল। কিন্তু অন্যদের সে কীভাবে দেখা দেবে? এই পৃথিবীর সমস্ত বস্তু ও স্থান এক সম্মুখমুখী সময়ের মধ্যে নিমজ্জিত। তার মধ্যে একটিমাত্র মানুষ, একটি জৈবিক বস্তুর পশ্চাৎমুখী সময়ের অস্তিত্বকে কী করে ব্যাখ্যা দেওয়া যাবে? দ্বিতীয় অমলের শরীরের প্রতিটি অণু-পরমাণু এই মহাবিশ্বের অণু-পরমাণু ও স্থানের সঙ্গে যুক্ত। সেই যুক্ত অবস্থায় সে কীভাবে অন্য একটি সময় প্রবাহের সঙ্গে চলতে পারে? কোনওভাবেই দ্বিতীয় অমলের সেই দেহ এই মহাবিশ্বের মধ্যে ভ্রমণ করতে পারে না। নাকি দ্বিতীয় অমলের সময়ের বিপরীতমুখী কণাসমূহ ধীরে ধীরে এই মহাবিশ্বের সম্মুখগতিকে প্রভাবিত করছে?
এর উত্তর আমি খুঁজে পাই না। সময় চলে যায়, আমি দৈনন্দিন জীবনে ফিরে যাই—আমার স্কুলের শিক্ষকতায়। কিন্তু দ্বিতীয় অমলের কথা ভুলতে পারি না। চার বছর পরে, আর এক গ্রীষ্মে আমেরিকা ফিরে আসি। লস অ্যাঞ্জেলেসে নেমে গাড়ি ভাড়া করে উত্তরে বিশপ শহরের দিকে রওনা হই। কয়েক ঘণ্টা পরে লাল বাদামি পাথর আর মাটির মরুভূমি পার হয়ে উঁচু খাড়াই সিয়েরা নেভেডা পর্বতশ্রেণির কাছে পৌঁছাই। সন্ধ্যা হয়ে যায় বিশপ পৌঁছাতে, বিশপের পশ্চিমে সিয়েরা নেভেডার পেছনে তখন সূর্য অস্ত যাচ্ছে। ঠিক আট বছর আগে এই ছোট শহরে আমরা একটা হোটেলে ছিলাম, রাতে একটা রেস্তোরাঁয় খেয়েছিলাম। রেস্তোরাঁটা এখনও আছে। আজ রাতে কি দ্বিতীয় অমল সেখানে দেখা দেবে?
বিশপ খুবই ছোট শহর। কিন্তু চার হাজার লোকের ছোট এই শহর হোটেল আর রেস্তোরাঁয় ভরতি। কারণ সিয়েরা নেভাডা পাহাড়ের যত পর্যটক তাদের মধ্যে অনেকেই এখানে এসে রাত্রিবাস করে। আট বছর আগে এখানেই রাতে আমরা একটা মেক্সিকান রেস্তোরাঁয় খেয়েছিলাম। অমল, আমি ও আমার এক ফরাসি বন্ধু জন। আজ জন নেই, কিন্তু আমার ধারণা দ্বিতীয় অমল যদি বাধ্য হয় প্রথম অমলের পথের ওপর দিয়ে ভ্রমণ করতে, তবে আজ রাতে সে এই রেস্তোরাঁয় দেখা দেবে। সন্ধ্যায় সেই রেস্তোরাঁয় আমি একটা টেবিল নিয়ে খাবারের অর্ডার দিই। খাবার আসে, খাই, তারপরও বসে থাকি। প্রায় দু-ঘণ্টা। আর বসা চলে না। বিল মেটানোর জন্য পকেট থেকে মানিব্যাগ বের করে ঠিক ক্রেডিট কার্ডটা দিচ্ছি কি না সেটা ভালো করে দেখতে চাই। এর মধ্যে ত্রিশ সেকেন্ডও হয়তো পার হয়নি। চোখ তুলে দেখি অমল রেস্তোরাঁর দরজার ওপাশে যেন এই মাত্র রেস্তোরাঁ থেকে বের হয়েছে। আমি দৌড়ে বের হই, কিন্তু বিশপের রাতের রাস্তা নির্জন থাকে। কেমন করে সে আবার উধাও হয়ে যায়।
এতক্ষণ সে কি তা হলে রেস্তোরাঁতে ছিল? না, সে যে সেখানে ছিল না সে সম্পর্কে আমি নিশ্চিত। সেই রেস্তোরাঁয় ছিল মাত্র গোটাদশেক টেবিল। আমি সবাইকে চোখে চোখে রেখেছিলাম। কী রকম ছিল সেই অমলের চেহারা? অমলকে শেষ যখন দেখেছিলাম তখন থেকে তার বয়েস চার বছর কমেছে, আমার চার বছর বেড়েছে। কিন্তু সে কি আদৌ তার পারিপার্শ্বিক অবস্থা সম্পর্কে জ্ঞাত ছিল, সে কি বুঝতে পারছিল সে কোথায় আছে? আর এত দ্রুত সে কেমন করে হারিয়ে গেল? নাকি অমলের দেশ-কালের রেখা আমাদের রেখার কোনও কোনও বিন্দুকে মাত্র ছেদ করে, আমাদের ভাগ্য ভালো থাকলে— সেই বিন্দুর কাছাকাছি থাকলে মাত্র তাকে দেখা সম্ভব।
পরদিন গাড়ি নিয়ে পাহাড়ের পথে ঢুকি। পথ যেখানে শেষ, সেখানে পিঠে ব্যাকপ্যাক ঝুলিয়ে হাঁটতে আরম্ভ করি। এই ছিল চার বছর আগে আমাদের পথ। কয়েকটা পর পর বিশাল নীল-সবুজ হ্রদ পার হয়ে যাই। ওপরের হ্রদের জল ঝরনা হয়ে নীচে ছোট স্রোতস্বিনী জলধারায় পড়ছে। সেই জলধারা মাঠের মধ্যে খুবই ছোট খাদ সৃষ্টি করে নীচের হ্রদে যোগ দিচ্ছে। চারদিকে জংলি ফুল ফোটা— বেগুনি লুপাইন, লাল ইন্ডিয়ান পেইন্টব্রাশ, গোলাপি আলপাইন পেনস্টেমন, সবুজ ঘাস। দূরে মাউন্ট রিটারের মাথায় শুভ্র তুষার। চার বছর আগে এই মায়াবী উপত্যকার কাছে আমরা তাঁবু ফেলেছিলাম। এখানে ঘাসের ওপর শুয়ে ছোট জলধারার কলধ্বনি শুনতে শুনতে আর ওপরে অসিতোপল রঙের আকাশে অমল-ধবল মেঘের আনাগোনায় হারিয়ে গিয়ে মনে হয়েছিল সারা জীবনটা যদি এমন হত। মনে পড়ে অমল এখানে চেষ্টা করেছিল জোড়াসনে বসতে, পুরো হাঁটু ভাঁজ করতে পারেনি। সেই বসা অবস্থায় তার একটা ছবি তুলেছিলাম জলধারার পাশে, সে কি আজ আবার তেমন করে দেখা দেবে?
সেই সন্ধ্যায় ওই উপত্যকায় আমি তাঁবু ফেলি। রাতে আগুন জ্বালি, কিন্তু অমলকে দেখি না। পরদিন খুব ভোরে জল গরম করে কোনওরকমে এক কাপ কফি খেয়ে ক্যাম্প গুটিয়ে রওনা হই। উপত্যকা ছাড়িয়েই একটা খাড়া পাহাড়ের পথ। প্রায় একশোখানা পাকদণ্ডী সাপের মতো এদিক-ওদিক করে বাঁক খেয়ে প্রায় দু-হাজার ফুট উঠেছে। সেখানে নীচে দাঁড়িয়েই আমি অমলের দেখা পাই। অনেক ওপরে সে ততক্ষণে। আস্তে আস্তে ওপরে উঠছে অমল, পেছনে ভারী ব্যাকপ্যাক। কিন্তু সে উঠছে উলটোভাবে, পেছন ফিরে। মানে আট বছর আগে, সে এমন সময়ে নেমে আসছিল। আমি বড় ব্যাকপ্যাকটা একটা গাছের আড়ালে নামিয়ে রেখে, ছোট একটা ব্যাগে জল আর খাবার ভরে, পা চালাই। দৌড়ে উঠতে চাই, আমার শ্বাস পড়ে ঘন ঘন। প্রতিটি পাকদণ্ডীর মুখে অমলকে দু-তিনটে পাকদণ্ডী ওপরে দেখি, তারপর সে চলে যায় দৃষ্টির বাইরে। আমি পা চালিয়ে আর একটা পাকদণ্ডী পার হই, অমলকে আবার দেখতে পাই। আমার মনে হয় অমলের পা যেন মাটিতে পড়ছে না, সে যেন ভাসছে। কিন্তু সেটা দৃষ্টিভ্রম হতে পারে। চিৎকার করি, ‘অমল, অমল!’ আমার চিৎকার অমলের শুনতে পাবার কথা ছিল, কিন্তু সে থামে না। সেই সকালে আমার শত চেষ্টাতেও অমলকে ধরতে পারলাম না। অথচ আমার কাঁধে ব্যাকপ্যাকের বোঝা ছিল না, অমলের ছিল, তাকে সহজেই আমার ধরে ফেলার কথা ছিল। কিন্তু এই আট বছরে আমার বয়েস বেড়েছে, আট বছর আগে যেমন শারীরিক দক্ষতা ছিল তার থেকে এখন কম হওয়াই স্বাভাবিক। আর অমলের বয়েস বাড়েনি, বরং কমেছে।
পাকদণ্ডী পার হয়ে পথটা একটা লজপোল পাইন আর ফার গাছের বনে প্রবেশ করে। আমি আরও চার ঘণ্টা পথ হাঁটি কিন্তু অমলের দেখা পাই না। বিকেল চারটেয় আমি ফিরে আসার সিদ্ধান্ত নিই। আমার অন্তত সাত ঘণ্টা লাগবে গাড়ির কাছে ফিরতে। বড় ব্যাকপ্যাকটা উদ্ধার করে অন্ধকারে টর্চের আলোতে পথ খুঁজে খুঁজে গাড়ির কাছে পৌঁছাই। সেই রাতে হোটেলে ফিরতে আমার রাত বারোটা বেজে যায়। রাতে পাকদণ্ডীর স্বপ্ন দেখি। দেখি অমলকে প্রায় ধরে ফেলেছি, চিৎকার করে ডাকছি, ‘অমল, অমল।’ অমল আমার ডাক শুনতে পেল, মুখ ফেরাল, কিন্তু এ কী, এ তো অমল নয়! কিন্তু সকালে ঘুম ভাঙলে আমার মনে পড়ে না কার মুখ দেখেছিলাম স্বপ্নে।
এর পরে আরও চার বছর কেটে যায়। অমলের খোঁজে আমি দক্ষিণ ক্যালিফোর্নিয়া, নিউ হ্যাম্পশয়ার, প্যারিস, লুসার্ন—সব জায়গায় গিয়েছি। প্রতিটি জায়গায় অমলকে দেখেছি, দূর থেকে, ক্ষণিকের জন্য। অমলের বয়েস এর মধ্যে কমেছে। প্যারিসে নটারদাম গির্জার উলটোদিকে শ্যন নদীর পাশে বসে আমরা কফি খেয়েছিলাম উন্মুক্ত আকাশের নীচে। সেখানেও শেষ মুহূর্তে তাকে দেখেছিলাম, একটা টেবিল থেকে উঠে ভিড়ে মিশে গিয়েছিল সে, পেছন পেছন হেঁটে, হাওয়ায় ভেসে। আর কেউ কি তাকে খেয়াল করেনি? আমিই কি একমাত্র লোক যে তার এই অদ্ভুত ভঙ্গি খেয়াল করেছিলাম?
সুইজারল্যান্ডের লুসার্ন শহরের ওপরে ছাদ দিয়ে ঢাকা কাঠের সেতুর ওপর দিয়ে আমরা হেঁটেছিলাম। চাপেল ব্রিজ নামে বিখ্যাত এই সেতু পরে আগুনে পুড়ে যায়, এখন আবার তাকে নির্মাণ করা হয়েছে আগের মতোই। আমরা এর পরে লুসার্ন লেকের পাশে বসে বিয়ার খেয়েছিলাম। এখানেও প্যারিসের মতো ঘটনা ঘটল। আমি ভেবেছিলাম যেহেতু ভিড় নেই, অমলকে এখানে আমি চোখে চোখে রাখতে পারব। কিন্তু হ্রদে একটা পালতোলা ইয়ট ভেঁপু বাজাল, আমি সেদিকে তাকালাম, দু-সেকেন্ডও বোধহয় হয়নি, এদিকে তাকিয়ে দেখি অমল বড় রাস্তা পার হয়ে একটা ছোট রাস্তায় ঢুকে যাচ্ছে, সে রকমভাবেই উলটোদিকে হেঁটে। আমি জানতাম তার পেছন নিয়ে আর কোনও লাভ নেই। আমার যাত্রা এখানেই শেষ, অমলকে আমি কখনই ধরতে পারব না।
কিন্তু এত বছরের একটা উন্মাদনা আমাকে ধীরে ধীরে বদলে দিয়েছিল। অমলের অশরীরী প্রত্যাবর্তনকে আমি দেখেছি এবং একমাত্র আমিই দেখেছি। বৈজ্ঞানিকভাবে কীভাবে এটা সম্ভব, তা নিয়ে আমি কম ভাবিনি।
জুরিখের বিখ্যাত শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান ইকোল পলিটেকনিক বা ইটিএইচ। এখানে স্বয়ং আইনস্টাইন পড়াশোনা করেছেন, এর সঙ্গে জড়িত অনেকেই নোবেল পুরস্কার পেয়েছেন। আমার সৌভাগ্য, আমার এক ঘনিষ্ঠ বন্ধু সেখানকার পদার্থবিদ্যা বিভাগের সঙ্গে যুক্ত। তাকে আপনারা অনেকেই চিনতে পারেন, তাই আপাতত তাকে আমি লিয়ান্দ্রো বলে সম্বোধন করব (এটা তার আসল নাম নয়)। লিয়ান্দ্রোকে যে আমি এককথায় আমার গল্প বিশ্বাস করাতে পেরেছিলাম তা নয়। অমল হারিয়ে যাবার পর আমেরিকা থেকে ফিরে এসেই তাকে অমলের ডায়েরিটা দেখিয়েছিলাম। আমার গল্পে এমন একটা বিস্ময় ছিল যে, সেটা লিয়ান্দ্রোকে শেষাবধি এ ব্যাপারে কৌতূহলী করে তোলে। সে আমাকে পরে বলেছিল, ‘জানো পাওলো, আমি কখনই তোমার কাহিনির ঘটনাগুলি বাস্তব বলে মনে করিনি। কিন্তু তাত্ত্বিকভাবে এটা একটা ইন্টারেস্টিং সমস্যা। মনে করো একটি মহাবিশ্ব কোনও একটি কারণে দুটি মহাবিশ্বে বিভক্ত হয়ে গেল। এর পেছনে কোয়ান্টাম ব্যতিচার হেন-তেন অনেক কারণ থাকতে পারে, সেসবের মধ্যে আমি না-ই গেলাম। নতুন যে দুটি মহাবিশ্ব হল, এর মধ্যে একটি আদি মহাবিশ্বের সময় যেদিকে বইছিল সেদিকেই গেল, কিন্তু দ্বিতীয় মহাবিশ্বের সময় আদি মহাবিশ্বের উলটোদিকে প্রবাহিত হতে থাকল। কিন্তু উলটোদিকে প্রবাহিত হতে হলে একটা রেফারেন্স লাগবে। সেই রেফারেন্সটা হল আদি মহাবিশ্বের সময়। আদি মহাবিশ্বে এন্ট্রোপি ক্রমাগত বাড়ছে, সুসংহত শক্তি অকার্যকরী শক্তিতে পরিণত হচ্ছে, আর দ্বিতীয় অমলের মহাবিশ্বে এন্ট্রোপি কমছে, অসংহত শক্তি আবার কার্যকরী শক্তিতে পরিণত হচ্ছে। ভাঙা ডিম জোড়া লাগছে, পোড়া পেট্রোল থেকে যে মুক্ত গ্যাস, তা আবার তরল পেট্রোলে রূপান্তরিত হচ্ছে।’
সেদিন লিয়ান্দ্রো আরও বলেছিল, ‘কিন্তু পাওলো, এই দুটি মহাবিশ্বের সমান্তরাল থাকার কথা, তাদের মধ্যে কোনও সমচ্ছেদ থাকবার কথা নয়। অর্থাৎ এক বিশ্বের মানুষের পক্ষে কখনই অন্য বিশ্বের কোনও কিছুকে অবলোকন করা সম্ভব নয়, যেটা অমল বা তুমি করেছ। তবু তর্কের খাতিরে এটা মেনে নিলে কিছু ইন্টারেস্টিং উপসংহারে উপনীত হওয়া সম্ভব।’
লিয়ান্দ্রোর কথা বলার ধরনটা বেশ ফর্মাল, তবে আমার সেটা শুনতে খারাপ লাগে না। আমি জিজ্ঞেস করি, ‘কী উপসংহার, লিয়ান্দ্রো?’
সে বলে, ‘প্রথম অমল যদি ওই মহাবিশ্ব থেকে দ্বিতীয় অমল হিসেবে এই মহাবিশ্বে আসতে পারে, তা হলে ভেবে দেখো শুধু অন্য মানুষ নয়, জীবজন্তু, গাছপালা, সাধারণ অজৈবিক বস্তু, যন্ত্র, গাড়ি বিমান সবই তাদের অর্থাৎ উলটোমুখী সময়ের মহাবিশ্বের সীমানা পার হয়ে এই মহাবিশ্বে উপনীত হতে পারবে। যেমন ধরো বনের মধ্যে একটি গাছ। সেই গাছটা যদি অমলের মতো সময়ের বিপরীত দিকে চলতে শুরু করে তোমার পক্ষে সেটা বোঝা একেবারেই অসম্ভব হবে। গাছ স্থবির, সেই স্থবিরতায় গাছটার বয়েস আসলেই কমছে কি না, সেটা দেখতে হলে তোমাকে বছরের পর বছর অপেক্ষা করতে হবে। কে জানে, আমাদের পৃথিবীতে হয়তো অমলের মতোই কোটি কোটি গাছ সময়ের উলটোদিকে ভ্রমণ করছে, আমাদের চোখের সামনেই, কিন্তু আমাদের পক্ষে সেটা বোঝা একেবারেই সম্ভব হচ্ছে না।’
লিয়ান্দ্রো তারপর নিজের মনেই হাসে। বলে, ‘আর পাওলো, এমন হতে পারে প্রকৃতির অনেক অংশেই সময়ের বিপরীতমুখী চলছে। ধরো পাহাড়ে একটা বিরাট পাথরের কথা। সেই পাথরের পরমাণুগুলোর সময় যদি ঋণাত্মক হয়, তবে সেটা আমাদের বোঝার কোনও উপায় নেই।’
‘আমার সঙ্গে ঠাট্টা করছ, লিয়ান্দ্রো?’ আমি একটু বিরক্তই হই।
লিয়ান্দ্রো আবার হেসেছিল। বলেছিল, ‘মহাবিশ্বের মতো অসম্ভব জিনিস যখন সংঘটিত হচ্ছে, সেই মহাবিশ্বকে বোঝার জন্য আবার মানুষের চেতনার মতো একটা জটিল ব্যাপারের উদ্ভব হয়েছে, তখন কোনও কিছুকেই অসম্ভব বলাকে আমি সংগত মনে করি না। একটা গাণিতিক সেটে অমলকে যদি একজন সদস্য বলা যায় এবং তার স্থান-কাল বা দেশ-কালের রেখা যদি এমন অদ্ভুতভাবে ভ্রমণ করে, তবে সেটের অন্য সদস্যদের ভাগ্য কেন অন্যরকম হবে? অমল কি বিশেষ কেউ? না, অমল এই মহাবিশ্বের একটি সাধারণ অংশ। সেই অংশ যদি একটা বিশেষ পথে চলে, আমি বলব সেই পথটা বিশেষ নয়। গাছ-পাথরসহ আমরা সবাই এই পথে চলতে পারি।’
লিয়ান্দ্রো হয়তো কথাটা গুরুত্ব দিয়েই বলেছিল, ঠাট্টা করে নয়। কিন্তু আমি সেটা নিয়ে খুব বেশি দিন ভাবনার সুযোগ পাইনি; কারণ এর মধ্যে আর একটা ঘটনা ঘটল বলে।
আমি আগে বলিনি, কিন্তু এখন বলছি… আমার স্ত্রীর নাম এমা। এমা একজন ফার্মাসিস্ট, একটি হাসপাতালের ফার্মেসিতে কাজ করে। বছর বারো আগে স্কি করতে গিয়ে একটা দুর্ঘটনায় আমার পা ভাঙে। এমার হাসপাতালে আমাকে এক সপ্তাহ থাকতে হয়, পরে ওষুধ আনতে প্রায়ই যেখানে যেতে হত। তখন থেকেই এমার সঙ্গে পরিচয়, প্রেম ইত্যাদি। প্রায় দশ বছর হয়ে গেল আমরা একসঙ্গে আছি। আর আনুষ্ঠানিকভাবে আমাদের বিয়ে হয়েছে আট বছর আগে, শাস্তা যাবার কিছু দিন আগে।
শাস্তা ওঠার সময় এমা আমার সঙ্গে যায়নি, কিন্তু শাস্তার ঘটনাটা সে পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে আমার কাছে থেকে জেনেছে। কিন্তু লিয়ান্দ্রো যেমন আমার কাহিনিটাকে অন্তত তাত্ত্বিকভাবে সম্ভব কি না সেটা নিয়ে চিন্তা করছিল, এমা প্রথম থেকেই এই পুরো ব্যাপারটাই অবাস্তব বলে আখ্যায়িত করেছিল। আমি যে দিন-রাত অমলের অলৌকিক আবির্ভাব নিয়ে মানসিকভাবে আচ্ছন্ন ছিলাম, সেটা এমাকে খুবই ভাবিয়ে তুলছিল। আমাকে সিয়েরা নেভাডায় ফিরে যেতে সে না করেছিল, আমি মানিনি। পরবর্তীকালে প্যারিস আর লুসার্ন যেতেও সে নিষেধ করেছিল। ধীরে ধীরে সে আমার ব্যাপারে হতাশ হয়ে পড়ছিল। অবশেষে একদিন রাতে এমা বলল, ‘পাওলো, এমন করে তোমার সঙ্গে থাকা আমার পক্ষে সম্ভব নয়। তুমি এই বাস্তব জগতে আর বাস করছ না। আগামী সপ্তাহে আমি একজন সাইকিয়াট্রিস্টের সঙ্গে অ্যাপয়েন্টমেন্ট নিয়েছি। ওঁর নাম এলিনা এগার। আমাদের হাসপাতালে উনি মাঝেমধ্যেই আসেন। মঙ্গলবার সকালে অ্যাপয়েন্টমেন্ট, তোমার ক্লাস নেই, আর আমি ছুটি নিয়ে তোমার সঙ্গে যাচ্ছি। তুমি যদি নিজে থেকে এই আচ্ছন্নতা থেকে না বের হতে পারো, অন্তত কোনও পেশাদারি উপদেশ তোমাকে সাহায্য করতে পারে।’
আমি চুপ করে থাকি। এমা আমার জন্য যথাসাধ্য করেছে, এই সম্পর্ক টিকিয়ে রাখার জন্য ও যা করেছে তা সবাই করবে না, ওকে আমি দোষ দিতে পারি না। আমি একটা অপার্থিব ঘটনার স্বাদ পেয়েছি, সেই অনুভূতি নিতান্তই আমার একার, সেটা অন্য কাউকে বলে বোঝানো যাবে না। আমাদের ঘরে অন্ধকার আরও গাঢ় হয়ে ওঠে। এমা আমার বুকে তার ডান হাত রেখে বলে, ‘তোমাকে আমি খুব ভালোবাসি, পাওলো। কিন্তু তুমি বদলে গেছ। সময়ের সঙ্গে মানুষ বদলায়, কিন্তু তুমি দৈনন্দিন কোনও ব্যাপারেই আর আগ্রহ পাও না। শাস্তায় যা হয়েছে সেজন্য তুমি নিজেকে দোষ দাও সেটা আমি জানি। তুমি খুব সংবেদী মানুষ, কিন্তু এখন সময় হয়েছে তোমার ঘরে ফিরবার।’
আমি আমার বুকে এমার হাতে হাত রাখি। তাকে যেন সাহস দিতে চাই। কিন্তু মুখ ফুটে কিছু বলতে পারি না। আমাদের তিনতলা অ্যাপার্টমেন্টের বাইরে রাতের শেষ ট্রামের চাকার ঘর্ষণের শব্দ শোনা যায়। এমা ঘুমিয়ে পড়লেও আমি ঘুমাতে পারি না। কোনও একটা অবোধ্য অজানা ভয় আমার সারা শরীর অধিকার করে রাখে। হৃৎপিণ্ড দ্রুত চলে, আমি তাকে শান্ত করতে চাই।
পরের মঙ্গলবার এমার সঙ্গে যাই সাইকিয়াট্রিস্ট এলিনা এগারের সঙ্গে দেখা করতে। ডক্টর এগারের কাজের ঘরটা ছোটই। সেখানে কোনও আলাদা সোফা বা বিছানা ছিল না, আমি ভেবেছিলাম মনোরোগী বিশেষজ্ঞদের সেটা থাকতে হয়। এমা আর আমি পাশাপাশি দুটো চেয়ারে বসলাম, আর এলিনা এগার সামনের একটি চেয়ারে। আমাদের মাঝে কোনও টেবিল ছিল না। কিন্তু পাশের কফি টেবিলের ওপর একটা ছিমছাম ফুলদানিতে সদ্য-তোলা ফুল ছিল। কী ফুল ছিল, এখন মনে করতে পারছি না। আর জানালার নীচে একটা চৌকানো টবে লাল-নীল ছোট ছোট ফুলের সমাহার ছিল।
ডক্টর এগারের বয়েস আমার মতোই হবে, বছর চল্লিশেক। বাদামি চুল ছোট করে ছাঁটা, তাঁর চশমা যেন পেশার সঙ্গে মানিয়েই চোখের ওপর বসানো হয়েছে।
আমি সেই শাস্তা পাহাড়ের ওপর অমলের হারিয়ে যাবার ঘটনাটা দিয়ে কথা শুরু করলাম। অমলের দিনপঞ্জির কথা বললাম, বিশপ শহরের রেস্তোরাঁ, সিয়েরা নেভাডা পাহাড়, প্যারিস, লুসার্ন কিছুই বাদ রাখলাম না। লিয়ান্দ্রোর কথাও বললাম। এলিনা এগার আমার কথায় বাধা দিলেন না। কোনও কিছুতেই যেন আশ্চর্য হলেন না। আমার কথা শেষ হলে এমার দিকে তাকালেন।
এমা বলল, ‘শাস্তা পাহাড়ের সেই পাওলো অমল থেকে একটু এগিয়ে গিয়েছিল। শাস্তা টেকনিক্যাল পাহাড় নয়, সেটাতে কোনও অভিজ্ঞতা ছাড়াই সবাই চড়তে পারে, আর অমল একেবারে অনভিজ্ঞ আরোহণকারী ছিল না। অ্যাভালেঞ্চ খাঁড়ি আমি যতটুকু বুঝেছি খুব সহজেই বুটের নীচে ক্রাম্পন ব্যবহার করে ওঠা যায়। সেইক্ষেত্রে পাওলোর অমলকে পেছনে ফেলে ওপরে উঠে যাওয়া দায়িত্বহীন কোনও কিছু ছিল না। কিন্তু সেই সুন্দর মেঘমুক্ত আকাশের নীচে অমলকে যখন আর পাওয়া গেল না, পাওলো নিজেকে দোষ দিল, যেন তার জন্যই অমলের ভাগ্য এ রকম হয়েছে। সেই দোষবোধ গত আট বছর পাওলোকে তাড়া করে বেড়াচ্ছে। আমি মনে করি পাওলো বিশপ শহরে বা সিয়েরা নেভেডায় ফিরে গিয়ে যে অমলকে দেখার কথা বলছে, সেটা নিতান্তই তার মনের কল্পনাপ্রসূত সৃষ্টি। এখন সময় হয়েছে অমলের এই অলীক আবির্ভাব থেকে মুক্ত হবার। এভাবে চললে পাওলো ধীরে ধীরে পাগল হয়ে যাবে, আর বলাই বাহুল্য, আমাদের সম্পর্কও ধ্বংস হয়ে যাবে।’
এলিনা এগার আমার দিকে তাকালেন। আমি আমার কাঁধে ঝোলানো ব্যাগটা যেটা পাশের কফি টেবিলের ওপর রেখেছিলাম, সেটা থেকে অমলের ডায়েরিটা বের করে তাঁর হাতে দিলাম। বললাম, ‘এই ডায়েরিটা পাহাড়ের ওপর অমল অদৃশ্য হবার পরদিনই পাওয়া গিয়েছিল। অমলের শেষ লেখাটা যে তার আগের দিনই লেখা হয়েছে সেটা আমি নিশ্চিত করে বলতে পারি, কারণ শাস্তায় ওঠার পূর্বে যে হোটেলে আমরা ছিলাম, সেই রাতে অমল ডায়েরিতে যা লিখেছিল সেটা আমাদের সেই দিনের কার্যক্রমের সঙ্গে মিলে যায়। অমল হালকা প্রকৃতির লোক ছিল না এবং এভাবে অসত্য কথা বিস্তারিতভাবে বলার মতো লোকও ছিল না। এমা আপনাকে সেটার সাক্ষ্য দিতে পারে।’
এমা মাথা নুইয়ে আমার কথায় সায় দেয়।
আমি বলি, ‘আর তা ছাড়া এই ডায়েরির মলাটে, পাতায় আগ্নেয়গিরির ছাইয়ের নমুনা পাওয়া গেছে। সেটার কোনও ব্যাখ্যাই আমরা দিতে পারিনি।’
ডক্টর এগার আমার দিকে তাকিয়ে বললেন, ‘আপনাকে এটা মানতেই হবে যে আপনি যা বলছেন সেটা অলৌকিক একটা ব্যাপার। আপনি বলছেন অমল জীবন সম্পর্কে সিরিয়াস ছিল। এমন কি হতে পারে, সে তার জীবন থেকে পালাতে একটা বিরাট ছলনার আশ্রয় নিয়েছিল?’
আমি ও এমা দুজনেই একটু আশ্চর্য হই এলিনা এগারের কথায়। এগার বলতে থাকে, ‘আপনি অমলের বন্ধু ছিলেন, কিন্তু খুব নিকট বন্ধু ছিলেন বলে আমার মনে হয় না। এমন হতে পারে অমলের জীবনে এমন একটা সংকট দেখা দিয়েছিল যে সে সেই জীবন থেকে পালিয়ে যেতে চেয়েছিল, হয়তো অন্য কোনও নাম নিয়ে— অজ্ঞাতভাবে। আমি জানি না সেই সংকট কী ধরনের হতে পারে, সেটা আপনারা ভেবে নিতে পারেন। এর জন্য সে অনেক দিন ধরে পরিকল্পনা করে, আগ্নেয়গিরির ছাই জোগাড় করে, শাস্তা ওঠার আগের রাতে হোটেলেই শাস্তা ওঠার কাহিনি লিখে ফেলে। দু-দিন পরে পাহাড়ে চড়ার সময় আপনি এগিয়ে গেলে, সে অন্য একটা পথ ধরে নেমে আসে।’
আমি মাথা নেড়ে আপত্তি জানাই। বলি, ‘ডক্টর এগার, অমলের যদি সেই পাহাড় থেকেও উধাও হবারই ইচ্ছা থাকত তা হলে দ্বিতীয় অমল, বিপরীত সময় এতসব উদ্ভট আষাঢ়ে গল্প ফাঁদার তার দরকার ছিল না। আপনি যেটা বলছেন অর্থাৎ অন্য একটা পথ ধরে সে নেমে আসতে পারত। কিন্তু শাস্তা এমনই একটা পাহাড় যে অন্য যে-কোনও পথ ধরে নেমে এল তার পদচিহ্ন আমরা পেতাম। আর হেলেন লেকের পাশে রাতে ঝড়ের যে বর্ণনা অমলের ডায়েরিতে আছে, সেটা তো আগে থেকে লেখা সম্ভব নয়।’
ডক্টর এগার শান্ত মুখে আমার কথা শুনলেন। তারপর বললেন, ‘ঠিক আছে। এবার বলুন এই ডায়েরিটা ক-দিন ধরে লেখা হয়েছে?’
আমি উত্তর দিলাম, ‘ডায়েরিতে দুটো এন্ট্রি আছে। একটা আমরা যেদিন শাস্তা শহরে সারাদিন গাড়ি চালিয়ে পৌঁছলাম সেদিন, আর একটি পাহাড়ের সেই অলীক গুহার মাঝে।’
এলিনা এগার বললেন, ‘এবার আপনাকে আর একটা সম্ভাবনার কথা বলছি। যে সম্ভাবনার কথাটা আপনার স্ত্রী আগেই বলেছেন। এমন কি হতে পারে আপনি অমলের হারিয়ে যাওয়ার জন্য নিজেকে দায়ী করেছেন এবং সেই মনঃপীড়ন থেকে নিজেরই একটা চরিত্র সৃষ্টি করেছেন, যে চরিত্রের অস্তিত্ব সম্পর্কে আপনি নিজেই অবগত নন। সেই চরিত্র অমলের ডায়েরি সৃষ্টি করেছে। নিজেই দ্বিতীয় অমল ইত্যাদি ব্যাপার বানিয়েছে। তবে আগ্নেয়গিরির ছাই কোনখান থেকে এসেছে সেটা আপাতত আমি ব্যাখ্যা করতে পারব না।’
আমি ডায়েরির পাতা উলটে বললাম, ‘কিন্তু এই হাতের লেখা, এই ইংরেজি আমার নয়। অমল আমার থেকে ভালো ইংরেজি জানত। আমি কখনই এ রকম ইংরেজি ভাষা ব্যবহার করতে পারব না।’
এগার এবার উত্তর দিতে সময় নিলেন। তারপর বললেন, ‘আপনি পদার্থবিদ্যায় পিএইচডি করেছেন ফরাসি ভাষায়, বড় হয়েছেন জার্মান ভাষার বিদ্যালয়ে, চৈনিক ভাষা সম্পর্কেও আপনার জ্ঞান আছে, আর ইংরেজি আপনার পেশাগত কারণে সবসময় ব্যবহার করতে হয়েছে। বিদেশি ভাষার ব্যবহার আপনার পক্ষে অজানা কিছু নয়। আপনার অন্য চরিত্র ইংরেজি লিখেছে কোনও সচেতনতা ছাড়াই, হতে পারে সেই ইংরেজি আপনার দৈনন্দিন ব্যবহৃত ইংরেজি থেকে ভিন্ন।’
‘আর হাতের লেখা?’
‘হ্যাঁ, এই হাতের লেখা আপনার হয়তো নয়, কিন্তু এই লেখা আপনার অন্য ব্যক্তিত্বের, অন্য পারসোনালিটির হতে পারে। আপনি নিজে সেই সম্বন্ধে হয়তো সচেতন নন। যা-হোক, এইসব সম্ভাবনার কথা আমি আপনাদের বললাম, যাতে এই নিয়ে আপনারা নিজেদের মধ্যেও কথা বলতে পারেন। আমি এই পর্যন্ত যা ঘটেছে তার কোনওটাকেই খাটো করে দেখছি না। কিন্তু আমি চাই আপনারা দুজনেই প্রতিটি সম্ভাবনার কথা খোলা মনে বিশ্লেষণ করবেন। আপনাদের সঙ্গে আমি দু-সপ্তাহ পরে আবার দেখা করতে চাই। আশা করি আপনাদের তাতে আপত্তি নেই।’
আমরা ডক্টর এগারের অফিস থেকে যখন বেরিয়ে এলাম তখন আকাশে কোনও মেঘ ছিল না। সেই শীতের উজ্জ্বল দিনে আমরা দুজন অনেকদিন পরে পুরোনো শহরে বেড়াতে গিয়েছিলাম, লিমাট নদীর ধারে একটা কাফেতে বসে কফি খেয়েছিলাম। এমার কাছে হয়তো সেই দিনটা ছিল আমাদের জীবনকে আবার নতুন করে ভাবার। কিন্তু দূরে চার্চের সবুজ লম্বা চূড়ার দিকে তাকিয়ে আমার মনে হল, এই মুহূর্তটার অভিজ্ঞতা আমার আগেও হয়েছিল। অন্য কোনও এক শীতের দিনে, হাস্যোজ্জ্বল তরুণ-তরুণীর হালকা হাসিতে, অন্য টেবিলে বসা বৃদ্ধ-বৃদ্ধাদের মৃদু কথাবার্তার মাঝে আমার মনে হল এইসবের মাঝখান দিয়ে আমি আগেও গেছি। এমা সেদিন অনেক ভারমুক্ত ছিল, তার হালকা সোনালি লম্বা চুলকে খুলে দিয়েছিল ঘাড়ের ওপর, তার কথা ভাসছিল বাতাসে তুলোর মতো। কিন্তু সেগুলোর কিছুই আমার কানে ঢুকছিল না।
এর এক সপ্তাহ পরে এমাকে না জানিয়ে আমি বোস্টনের টিকিট কেটে সুইস এয়ারে চেপে বসি। আটলান্টিক মহাসাগর পাড়ি দিতে দিতে নীচে সুনীল সাগরের অস্পষ্ট ঊর্মি দেখি, ভাবি কী ধরনের উন্মাদনা আমার জীবন পরিচালনা করছে। জীবনের যা কিছু সত্য, বাস্তব— সব কিছু আমি অস্বীকার করছি। এমাকে হারাচ্ছি। আজ থেকে ঠিক ষোলো বছর আগে এই দিনে আমি এই ফ্লাইটে জুরিখ থেকে বোস্টনে খুব সকালে পৌঁছেছিলাম। অমল আমাকে বিমানবন্দর থেকে তুলে নিউ হ্যাম্পশায়ারে নিয়ে যায়। চারদিক তুষারে ঢাকা ছিল।
কিন্তু এবার বোস্টনে নেমে আমি অমলের দেখা পাই না। একটা গাড়ি ভাড়া করে উত্তর দিকে রওনা হই। সকাল তখন ন-টা হবে। ষোলো বছর আগে অমল নিউ হ্যাম্পশায়ারের বনে একটা কেবিনে থাকত, তার এক মার্কিন বন্ধু তাকে সেখানে থাকতে দিয়েছিল। সেদিন অমল আমাকে বিমানবন্দর থেকে তুলে তার কেবিনে নিয়ে গিয়েছিল, সেখানে দু-দিন থেকে আমি আমার কাজের জায়গায় চলে যাই। বোস্টন বিমানবন্দর থেকে আজ আমার সেই কেবিনে পৌঁছাতে প্রায় আড়াই ঘণ্টা লাগে। বড় রাস্তা থেকে একটা সুরকি ঢালা রাস্তা নিতে হয়, কিন্তু তুষারে সব সাদা হয়ে ছিল। বার্চ, ম্যাপেল আর বিচ গাছের এই বন হেমন্তে একেবারে রঙের বন্যায় ভেসে যায়। কিন্তু আজ সব পাতা ঝরে গেছে। বহু দূর পর্যন্ত বনের ভেতর দেখা যায়। তুষার ঢাকা বনের মধ্যে মাঝে মাঝে বাড়ি দেখা যায়। তাদের চিমনি থেকে ধোঁয়া উঠছে। এই কেবিন যার— অমলের বন্ধু জেফ— তাকে আমি ই-মেইলে যোগাযোগ করে বলেছিলাম যে আমি কেবিনটা একটু দেখতে চাই। সে হয়তো অবাকই হয়েছিল, কিন্তু সেটা লেখেনি, লিখেছিল কেবিনটা যে রকম ছিল সে রকমই আছে। দরজাটা একটা ছিটকিনি দিয়ে আটকানো, তালা দেওয়া নেই। আমি চাইলে সেখানে থাকতে পারি, কিন্তু থাকার মতো কোনও ব্যবস্থা নেই, বিদ্যুৎও নেই।
কেবিনের তিনদিক গাছ দিয়ে ঢাকা, প্রায় কুড়ি একরের একটা বন। গাড়ি পার্ক করে কেবিনের দিকে তাকালাম। দেখি কেবিনের চিমনি দিয়ে ধোঁয়া উঠছে। আমার হৃৎপিণ্ড আবার বন্ধ হয়ে গেল। জেফ বলেছে, সেখানে কেউ থাকে না। কে তা হলে এখানে? অমল? আমি কেবিনের দিকে এগোই। সন্তর্পণে। কিন্তু আমার পায়ের নীচে জুতোর চাপে তুষার আর বরফে কড়মড় কচমচ শব্দ হয়। থেমে যাই, শুনতে চাই কেবিনের ভেতর থেকে কোনও শব্দ আসছে কি না। কোনও কিছু শুনতে পাই না। কেবিনের সামনে কাঠের বারান্দায় উঠি, কাঠের ক্যাচম্যাচ শব্দ হয়। দরজায় এসে টোকা দিই, বলা যায় না, কোনও অজানা লোক এখানে আস্তানা গাড়তে পারে। কেউ উত্তর দেয় না। দরজায় ছিটকিনি দেওয়া নেই। আমি দরজা ঠেলা দিয়ে ভেতরে উঁকি দিই।
ভেতরে কেউ ছিল না। কিন্তু ঘরের কোনায় লোহার ফারনেসে কাঠ জ্বলছে, তার ধোঁয়াই চিমনি দিয়ে বের হচ্ছিল। একটা টেবিল আর দুটো চেয়ার। ঘরে আর কিছু নেই, শুধু কোনায় একটা স্তম্ভে সাজানো কিছু বই ছাড়া। টেবিলের ওপর দুটো মগ বা কাপ, তাদের মধ্যে কালো কফি, কফি থেকে তখনও ধোঁয়া বের হচ্ছে। দুটো কফির মগ মানে দুজন মানুষ এখানে আছে। আশপাশেই কোথাও।
তারপর দেখলাম টেবিলের নীচে একটা বই পড়ে আছে। কবিতার বই। বইটা খোলা একটা পাতায়। চার স্তবকের কবিতা, নাম- The Road Not Taken. একটা স্তবকের দুটো লাইন লাল কালি দিয়ে দাগানো।
Yet knowing how way leads on to way,
I doubted if I should ever come back.
রবার্ট ফ্রস্টের কবিতা। মনে পড়ল সেদিন অমল আমাকে বলেছিল রবার্ট ফ্রস্ট নামে একজন বিখ্যাত মার্কিন কবির বাড়ি নাকি এই কেবিনের কাছাকাছিই ছিল। অমল তখনই এই বইটা থেকে এই কবিতাটা পড়ে শুনিয়েছিল। দুটো রাস্তার মাঝে যে রাস্তাটার ব্যবহার কম হয়, সেটাই কবি বেছে নিয়েছিলেন।
অমলই যে এখানে আছে, সে বিষয়ে আমার আর সন্দেহ রইল না। কিন্তু দুটো কফির কাপ কেন? বহু বছর আগে বিশপ শহরে আমি একটা স্বপ্ন দেখেছিলাম। আমি স্বপ্ন দেখেছিলাম যে পাহাড়ের পাকদণ্ডী বেয়ে আমি অমলকে প্রায় ধরে ফেলেছি। চিৎকার করে আমি তাকে ডাকছিলাম। আমার ডাক শুনে অমল মুখ ফেরাল, কিন্তু সেই মুখ অমলের ছিল না। আজ বুঝলাম সেই মুখ আমারই ছিল। আমার অতীত যাত্রা বহু আগেই শুরু হয়েছে।
আমি চেয়ারে বসে অমলের ডায়েরিটা বের করে আজকের অভিজ্ঞতা লিখি। মনে পড়ল শীতের সেই ছোট দিনে, সূর্য ডোবার আগে আমরা কেবিনের পেছনের তুষার ঢাকা ম্যাপেল আর বার্চের বনে হাঁটতে গিয়েছিলাম। আমার হাত ঠান্ডায় খুব সহজেই জমে যায়, তাই আজ আমি হাতে দস্তানা পরে নিই। তারপর দরজা খুলে শ্বেত-শুভ্র তুষার সাম্রাজ্যে বের হই।
এমার কথা
আমার নাম এমা মেরিয়ান। আমি পেশায় একজন ফার্মাসিস্ট। পাওলো সিয়ুংয়ের স্ত্রী (ছিলাম)। আমার ভাগ্যেই হয়তো এই ট্র্যাজিক কাহিনির সমাপ্তি টানার ভার পড়েছে। তাই ইচ্ছা না থাকলেও অমলের দিনপঞ্জিতে এই কথাগুলো আমি লিখে যাচ্ছি।
পাওলো যে নিউ হ্যাম্পশায়ার যাচ্ছে, সেটা আমাকে সে বলেনি। কিন্তু পাওলো জানত যে মুহূর্তে সে আটলান্টিক পাড়ি দেবার জন্য বিমানে উঠেছে, সেই মুহূর্তে আমাদের সম্পর্কের ইতি হয়েছে। এত সব জেনেও পাওলো একটা চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নিয়েছিল। আমি ভেবেছিলাম ডক্টর এলিনা এগার যেসব সম্ভাবনার কথা বলেছিলেন, সেগুলো নিয়ে সে কিছুদিন ভাববে। হয়তো সে ভেবেছে, আমি জানি না। কিন্তু এক ধরনের অপার্থিব অভিজ্ঞতা তাকে তাড়া করে বেরিয়েছে, সেটা থেকে সে মুক্ত হতে পারেনি। বোস্টন বিমানবন্দরে নেমে পাওলো আমাকে ফোন করেছিল, বলেছিল তাকে ক্ষমা করতে। আমি ক্ষোভে, দুঃখে, অপমানে কথা বলতে পারিনি। পাওলো বলেছিল, আমাকে ই-মেইলে জেফের ই-মেইল আর কেবিনের ঠিকানা পাঠিয়েছে। আমি উত্তর না দিয়ে ফোন রেখে দিয়েছিলাম। ভেবেছিলাম তার সঙ্গে এই শেষ কথা, এমন দায়িত্বহীন লোকের সঙ্গে সম্পর্ক গড়াই আমার ভুল হয়েছে। কিন্তু এক সপ্তাহ কেটে গেলে পাওলোর আর কোনও ফোন না পেয়ে আমি উতলা হয়ে উঠি। জেফকে ই-মেইল করি, কিন্তু সে উত্তর দেয় এর মধ্যে পাওলোর সঙ্গে তার কোনও যোগাযোগ হয়নি। আমি অস্থির হয়ে উঠি, না থাকতে পেরে বিমানের টিকিট কেটে বোস্টন রওনা হই। পাওলোর মতোই আমার প্লেন খুব সকালে বোস্টন নামে। গাড়ি ভাড়া করে নিউ হ্যাম্পশায়ারের দিকে রওনা হই।
এর আগে আমি আমেরিকা আসিনি। কিন্তু দেশ দেখার মতো মানসিকতা আমার ছিল না। নিউ হ্যাম্পশায়ারে কেবিনের পথে তুষার-ঢাকা রাস্তায় গাড়ি চালাতে হয়। অবশেষে কেবিনটা খুঁজে পাই। কেবিনের সামনে একটা গাড়ি পার্ক করা ছিল। পাওলোর ভাড়া করা গাড়ি ছিল সেটা। আর কেবিনের ভেতরে ছিল শুধু একটা টেবিল, দুটো চেয়ার, এক কোনায় গাদা করা কিছু বই। সেই সকালে আমি জেফকে ফোন করি, জেফ এসে আমার সঙ্গে কথা বলে, পুলিশে খবর দেয়। বনের মধ্যে কিছু পায়ের ছাপ ছিল, কিন্তু পাওলোকে আর পাওয়া যায় না।
সেই কেবিনের টেবিলের ওপর আর একটা জিনিস ছিল—অমলের ডায়েরি। ডায়েরির শেষ ক-টা পাতায় পাওলোর শেষ দিনের অভিজ্ঞতা লেখা ছিল। সেদিন কেবিনের ঠান্ডায় চেয়ারে বসে আমি পাওলোর শেষ কথাগুলি পড়ি, মনের মধ্যে গড়তে চাই তার শেষ দিনটির কথা। ততদিনে কেন জানি আমি আর পাওলোর শাস্তা পাহাড়ের কাহিনিকে অবিশ্বাস করতে চাইনি। আমি ভাবি, দস্তানা পরে পাওলো বের হয় অপরাহ্ণের হেলে-পড়া সূর্যের আলোয়। ঠান্ডায় তার প্রশ্বাস ঘনীভূত হয় হালকা কুয়াশার মতো। বনের পাতাহীন গাছগুলোর মধ্যে যেতে যেতে অল্প কিছুক্ষণের মধ্যেই তার চোখে পড়ে এক জোড়া পায়ের ছাপ… অমলের? সে অনুসরণ করতে থাকে সেই ছাপ, কিছু দূরে দেখে সে এক জোড়া হরিণ। তারপর একটা ছোট জলধারা পার হয়, সেখানে কিছু হাঁস খাবারের খোঁজ করে। পায়ের ছাপ এক জায়গায় এসে মোড় নেয় কেবিনের দিকে। এক জোড়া ছাপের বদলে দেখা যায় দু-জোড়া ছাপ। হঠাৎ কেমন করে এই বাড়তি ছাপজোড়া এল? এমন যেন আর একজন মানুষ অলৌকিকভাবে আবির্ভূত হয়েছে। কে হতে পারে সেই দ্বিতীয় ব্যক্তিটি? বন পেরিয়ে কেবিনটা আবার দেখা যায়। দু-জোড়া পায়ের ছাপ কেবিনের দিকে গেছে। না, আসলে পায়ের ছাপগুলো কেবিন থেকেই এসেছে। পাওলো ধীরে ধীরে কেবিনে পৌঁছায়, তার হৃৎপিণ্ড দ্রুত বয়। দরজার পাশে এসে সে কান পেতে শুনতে চায়, ভেতরে চাপা কথাবার্তার আওয়াজ আসে, কিন্তু সেই কথাগুলো তার বোধগম্য হয় না। যেন কোনও রেকর্ড বা টেপকে উলটোদিকে চালানো হচ্ছে। কোনও পাহাড়ের গুহায় অমল তার ভবিষ্যৎমুখী সময় যে শেষ হয়ে এসেছে সেটা কল্পনা করতে পেরেছিল, আজ তার নিজের সময় যে শেষ হচ্ছে সেটা পাওলো বুঝতে পারে। এর পরে তার যাত্রা হবে অতীতমুখী, নাকি বহুদিন হল সেই যাত্রা শুরু হয়ে গেছে? স্বাধীন-চিন্তারহিত এক যাত্রা। পাওলো কেবিনের দরজা খুলে ভেতরে ঢোকে…
এভাবেই পাওলো চলে গেল, আমি ভাবি। সেই দিন আমার জন্য ফার্নেসে আগুন জ্বলছিল না, টেবিলে কফির কোনও কাপ ছিল না, টেবিলের নীচে কোনও কবিতার বই ছিল না। তবু অমলের ডায়েরিটা শক্ত করে ধরে ভাবি, পাওলোর সঙ্গে আমার দেখা হবার অনেক সম্ভাবনা আছে। অনেকবার। আমাদের হাসপাতালের ফার্মেসিতে, পুরোনো শহরে, লেক জুরিখের ধারে। আর তার সঙ্গে আমার দেখা হবে আমাদেরই অ্যাপার্টমেন্টে। হয়তো প্রতিদিনই, প্রতিরাতেই। পাওলোর বয়েস যত কমবে আমার বয়েস তত বাড়বে, তারপর হয়তো পাওলোর মতোই আমি প্রবেশ করব আমার অতীতমুখী সময়ে। এ যেন একটা ছোঁয়াচে ব্যাপার। সেই অতীতমুখী মহাবিশ্ব আমাদের মহাবিশ্ব থেকে একটি একটি করে জীবন, বস্তু, স্থান-কালের রেখাকে হরণ করে তার মহাবিশ্ব গড়ছে। শেষাবধি এই মহাবিশ্বের প্রতিটি পরমাণু, মৌলিক কণা সেই অতীত যাত্রার পথে সঙ্গী হবে। মহাবিশ্বের প্রসারণ থেমে যাবে, সে সংকুচিত হবে, কিন্তু সেই সংকোচন তার অতীত প্রসারণের পথ ধরেই হবে, তার মাঝে স্বাধীন চিন্তার কোনও স্থান থাকবে না। সবচেয়ে বড় কথা, সেই সংকোচনে যেসব সচেতন প্রাণী অংশগ্রহণ করবে, তারা বুঝতেও পারবে না যে তাদের সময় উলটোদিকে বইছে। কারণ তাদের ভবিষ্যৎ ক্রমাগতই মুছে যেতে থাকবে। হোরহে লুইস বোরহেস অতীত ও ভবিষ্যৎ সময়কে অস্বীকার করে একটি প্রবন্ধ লিখেছিলেন, তাতে তিনি বৌদ্ধ পুরাণের উদ্ধৃতি দিয়েছিলেন— পৃথিবী নাকি নিজেকে প্রতিদিন ৬৫ কোটি বার ধ্বংস করে আবার পুনর্গঠিত করে, আর মানুষের ক্রমান্বয় অস্তিত্ব একটি মায়া মাত্র, কারণ আলাদা আলাদা বিচ্ছিন্ন একক মানুষের এক-একটি মুহূর্তের অস্তিত্বের সমষ্টিকেই আমরা ক্রমান্বয়তা ভাবি।
আপনারা—পাঠকেরা—যারা এই কাহিনি পড়ছেন, অমলের মতোই আমি বলব, আপনাদের ঘরে যদি সেকেন্ডের কাঁটাসম্পন্ন কোনও দেয়ালঘড়ি থাকে সেটা খুব ভালো করে খেয়াল করুন, সেই কাঁটা কি সত্যিই সামনের দিকে ঘুরছে? আপনি কি সত্যিই কোনটা ভবিষ্যৎ আর কোনটা অতীত, সেটা বুঝে নিতে পেরেছেন? হয়তো আপনার জীবনে যা ঘটার ছিল সবই ঘটে গেছে। আপনি এখন যেটা ভবিষ্যৎ ভাবছেন, যেটা সময়ের প্রবাহে সংঘটিত হবে ভাবছেন, সেটা ইতিমধ্যে হয়ে গেছে, আর এখন আপনি একটা অদ্ভুত অপার্থিব খাঁচায় বন্দি, যার থেকে বের হবার কোনও উপায় নেই।
হয়তো এই কাহিনি পড়ে কৌতূহলী হয়ে অনেকে আমার খোঁজ করবেন। আমি শুধু এটুকু বলতে পারি, ঘটনাপরম্পরায় সমস্ত কৌতূহলী মানুষের পরিণতি যে পাওলো বা অমলের মতো হবে না তার প্রতিশ্রুতি আমি দিতে পারি না। যদি আপনার মনে হয় সময়ের বিপরীতমুখী স্রোতের সামান্যতম ইশারা আপনি পেয়েছেন, তবে যোগাযোগ করবেন, ঠিকানাটা তো অমলই দিয়ে গেছে। অমলের ডায়েরিটা আপনাকে দিয়ে যাব।


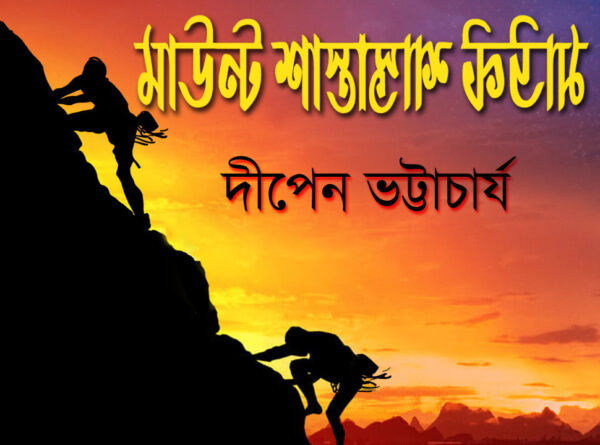

আহা! জাদুকরী লেখা! কি বলবো ভেবে পাচ্ছি না। গল্পটা পড়ার পর থ মেরে বসে আছি আর ভাবছি, “এভাবেও ভাবা যায়?”
মাঝেমধ্যেই সময় নিয়ে অনেক উদ্ভট ভাবনা জন্ম হয়। নিজেকে পাগল পাগল লাগে। প্রায়ই খেই হারিয়ে ফেলি। এই গল্পটা পড়ার পর সেইসব ভাবনায় নতুন পালক না কেবল, বলতে গেলে নতুন ডানা যুক্ত হলো।
এমন একটা লেখা পড়ার সুযোগ করে দেওয়ার জন্যে লেখকের প্রতি বিনম্র শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করছি। কল্পবিশ্বকেও অনেক ধন্যবাদ।
কালাবর্ত্ম্যের বক্রতা গদ্যের নির্মেদ চরণে সপ্রাণ অবয়ব পেয়েছে। আধুনিক বিজ্ঞানে সময়ের যে দ্বান্দ্বিক চরিত্র প্রতিষ্ঠিত হয়েছে তাকে গল্পের শরীরে আত্তীকৃত করা মুন্সিয়ানার দাবী রাখে। শ্রী দীপেন ভট্টাচার্যের লেখনী বাংলা কল্পবিজ্ঞানে এক অনাস্বাদিতপূর্ব অক্ষর অভিযানের সাক্ষর। মুগ্ধ হয়েছি পাঠ অভিজ্ঞতায়।
এক অসামান্য কল্পবিজ্ঞান কাহিনি পড়লাম। লেখক দীপেন ভট্টাচার্যের লেখা আরও পড়তে চাই। কল্পবিশ্বকে ধন্যবাদ এমন একটা লেখা প্রকাশের জন্য।
অসামান্য লেখা। এরকম লেখা ভাবতে বাধ্য করে প্রত্যেককে। সময়ের গতি আর ব্যবহার নিয়ে আমরা প্রায় কিছুই জেনে উঠতে পারিনি এখনও। লেখককে কুরনিশ জানাই।
এই লেভেলের কল্পনাশক্তি, মনন ও প্রজ্ঞা… অভাবনীয়! কুর্নিশ জানাই লেখকের উদ্দেশে।
লেখাটা ত দারুন হয়েছে। সাহিত্য গুণে অসাধারণ। কল্পবিজ্ঞানের দিক থেকে একটা খটকা লাগল, অবশ্য হতে পারে আমিই বিজ্ঞান আর কল্পবিজ্ঞানকে গুলিয়ে ফেলছি। তাই আগাম মার্জনা চেয়ে রাখলাম।
” যে মুহূর্তে আমি সরে যাই সেই মুহূর্তে সে আমার পূর্বতন জায়গায় তার ডান পা-টা রাখে। ”
এটা কি করে সম্ভব? একটা টাইম ডাইমেনশন একটা স্পেস দিয়ে এগোচ্ছে আর সেই স্পেস দিয়েই আরেকটা টাইম ডাইমেনশন পিছিয়ে আসছে। তা’হলে দুটি ডাইমেনশনের একটিই (অমল A, অমল B) অবজেক্ট একই সময়ে দুটি আলাদা স্পেস পয়েন্টে পা রাখল কি করে?
যা হোক, কাজকর্মের চাপে সাহিত্যচর্চা খুব কম হয়, তাই আমিই ভুল করে ফেলতে পারি, লেখক অনুগ্রহ করে কুন্ঠিত হবেন না।