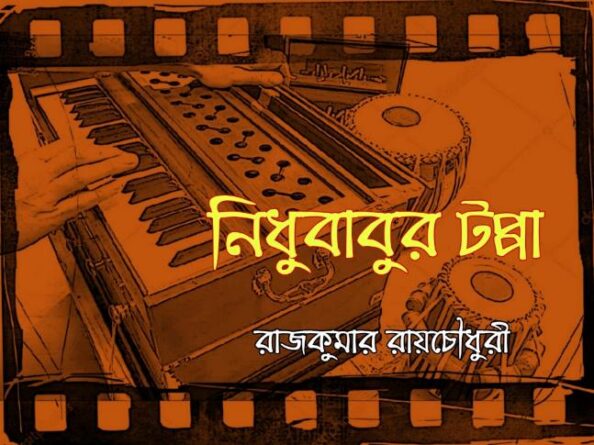নিধুবাবুর টপ্পা
লেখক: রাজকুমার রায়চৌধুরী
শিল্পী: সৌরভ ঘোষ
ভূমিকা
আমি আমার যে অভিজ্ঞতার কথা এখানে বলব তার প্রধান কুশীলব আমি নই। আমি শুধু ঘটনাটার একটা বৈজ্ঞানিক বা যুক্তিসম্মত ব্যাখ্যা খোঁজার চেষ্টা করেছি। প্রথমেই বলে রাখি আমি এই লেখাটা ২০১৫ সালে লিখেছিলাম৷ নানান কাজে ব্যস্ত থাকায় ছাপানোর চেষ্টা করিনি৷ কয়েকটি মন্তব্য ছাড়া লেখাটির পরিবর্তন করিনি৷
(১)
বেশ কয়েক বছর আগের ঘটনা হলেও কিছুদিন আগে একটি মর্মান্তিক মৃত্যুর খবর শুনে ঘটনাটি আবার মনে পড়ল৷ মনে হল এই তো সেদিনের ঘটনা৷ আমি যে কাণ্ডকলাপের কথা বলব তার প্রধান কুশীলব অম্বরিষ সরখেল এর একটা বিজ্ঞানসম্মত ব্যাখ্যা দিলেও এখনও পুরোপুরি সন্তুষ্ট হতে পারিনি। বিশেষ করে অতীতের একটি অপরাধ কি করে অম্বরিষবাবুর গবেষষণায় ধরা পড়ল সেটা ও যথেস্ট রহস্যজনক৷ আর অম্বরিষ সরখেলের গবেষণা শেষ হওয়ার আগেই একটা পোড়োবাড়িতে তাঁর আকস্মিক মৃত্যু, এই সমস্ত ঘিরে একটা রহস্য জাল তৈরি হয়েছিল৷ তারপর যা হয়, আস্তে আস্তে সবাই ঘটনাটা ভুলে যায়৷ পুরো কাহিনি শুনে বিচারের ভার পাঠকের হাতেই ছেড়ে দিচ্ছি৷ প্রণাম ধরের কাছেই প্রথম আমি এ ব্যাপারে অবহিত হই৷ সম্প্রতি একটি বিজ্ঞান পত্রিকায় কোয়ান্টাম মেকানিকসে টাইম ট্র্যাভেলের উপর যে এক্সপেরিমেন্টের কথা পড়েছি সরখেলের আবিষ্কার সেরকম কিছু কিনা ভাবার চেষ্টা করেছি৷ জটিল অংকের মাধ্যমে যেটা বিজ্ঞানীরা বলতে চেয়েছেন তা হল কিছু ক্ষেত্রে ওঁরা একটা ইলেকট্রনকে আগের অবস্হায় নিয়ে আসতে পেরেছেন৷ এর বেশি বোঝা আমার বিদ্যেতে সম্ভব নয়৷ বলা বাহুল্য ম্যাক্রোস্কোপিক লেভেলে এখনও টাইম ট্র্যাভেল সম্ভব নয়৷ কিন্তু প্রণাম ধরের কাছে যা শুনলাম এবং পরে আমি ও সত্যেশবাবু যা প্রত্যক্ষ করেছিলাম তার কথাই এখানে বলছি৷ আমার নিজের বিশ্বাস সরখেল যা আবিষ্কার করেছিলেন সেটার পক্ষে যথেস্ট প্রমাণ থাকা সত্বেও সব গবেষকরা এখনও তাঁর তথ্য বা এক্সপেরিমেন্ট সম্পর্কে সন্দেহ প্রকাশ করেন৷ যদিও এবিষয়ে গবেষণা চলছে বিভিন্ন দেশে কিন্তু সেটা বিচ্ছিন্নভাবে৷
(২)
প্রণাম ধরের সঙ্গে প্রথম আলাপ হর কি দুনের পথে। ১৯৯৮ সালে৷ আমি আর সত্যেশবাবু হর কি দুন যাব ঠিক করেছিলাম। জানা ছিল পথ খুব দুর্গম নয়। তাও একটু চিন্তায় ছিলাম। সত্যেশবাবুর বয়স প্রায় ষাট বছর, তবে এর আগে মনিমহেশ গিয়েছিলেন আমার সঙ্গে৷ এখনও খুবই ফিট৷ হর কি দুনে গিয়ে দেখলাম সত্যিই তাই৷ দু-একটা জায়গায় কঠিন চড়াই থাকলেও তা দুঃসাধ্য নয়৷ পথের দৃশ্য সব কষ্ট ভুলিয়ে দেয়। তমসা নদীর তীর ধরে পথ৷ ফেরার পথে ভাবলাম তালুকাতে দু-রাত কাটিয়ে যাব। এখানে কর্ণের ও দুর্যোধনের মন্দির আছে বলে শুনেছি। এটা দ্রৌপদীর দেশ। পান্ডবেরা এখানে ব্রাত্য। এক মেয়ের একাধিক স্বামী থাকা এখানে অস্বাভাবিক নয়। আমাদের পোর্টার ছিল অল্পবয়সি দুটো পাহাড়ি ছেলে। এদের একজনের দুটি বাবা আছে। ও বলত বড় বাবা আর ছোট বাবা।
প্রণাম ধরের সঙ্গে দেখা তালুকায়। প্রণাম ধর কিন্তু হর কি দুনে যাননি৷ ওঁর নেশা হল হিমালয়ের নানান জায়গায় ঘুরে বেড়ানো৷ প্রত্যেক বছর মে থেকে জুন একমাস হিমালয়ে ঘুরে বেড়ান৷ উনি প্রচলিত অর্থে ট্রেকার নন৷ তবে ট্যুরিস্টদের প্রিয় জায়গাগুলি এড়িয়ে চলেন৷ যেমন উখীমঠ গেছেন কিন্তু কেদারনাথ যাননি৷ জিএসআই-তে কাজ করতেন৷ কিন্তু নেহাতই মামুলি চাকরি৷ চিরকাল গানবাজনায় আগ্রহ ছিল৷ বিশেষ করে আমরা যাকে বলি পুরাতনী গান তাতে ওঁর বিশেষ আগ্রহ ছিল৷ ওঁর যখন আটান্ন বছর বয়স ওঁর স্ত্রী ক্যানসারে মারা যান৷ উনি নিঃসন্তান৷ কোনও পিছুটান নেই৷ স্বেচ্ছায় অবসর নিয়ে পড়াশুনা, গানবাজনা আর হিমালয়ে ভ্রমণ নিয়ে জীবন দিব্যি কেটে যায়৷ ফোটোগ্রাফিতেও শখ আছে৷ অবশ্যই এ সমস্ত তথ্য ওঁর সঙ্গে আলাপ করে জানতে পারি৷ তালুকায় ফেরবার পথে রেস্ট হাউসে একটা ঘর খালি ছিল৷ আমরা এই ঘরটাতেই উঠি৷ পোর্টার বলল পাশের ঘরে এক বাঙালিবাবু আছেন৷ তালুকায় আমরা যখন আসি প্রচণ্ড ঠান্ডা৷ পোর্টাররা ঘরে কাশ্মীরি কায়দায় ফায়ার প্লেস জ্বালিয়ে চলে গেল৷ এখানে ওদের আত্মীয় আছে তাদের বাড়িতে দু-রাত কাটাবে৷ ফায়ার প্লেস মানে বড় একটা লোহার কড়াইতে জ্বলন্ত কয়লা৷ বাঙালিবাবু পাশের ঘরে আছে৷ তাও হিমালয় ভক্ত! আমি আর সত্যেশবাবু ওঁর ঘরে গিয়ে আমন্ত্রণ জানালাম আমাদের ঘরে এসে চা খেতে৷ চৌকিদার বানাবে পাহাড়ি চা৷ বোধহয় ভেড়ার দুধ দিয়ে বানায়৷ এই ঠান্ডায় মন্দ লাগে না৷ প্রণাম ধর, নামটা তখনই জানতে পারলাম, বললেন যে উনি একটু পরেই আসছেন৷কতক গুলি ফোটোগ্রাফ আমাদের দেখাতে চান৷ ওগুলো নিয়ে আসবেন৷
কিছুক্ষণের মধ্যেই প্রণাম ধর এসে হাজির৷ বুদ্ধি করে নিজের ঘর থেকে একটা চেয়ার নিয়ে এসেছিলেন৷ এই বাংলোটাতে প্রত্যেক ঘরে একটা টেবিল, দুটো চেয়ার আর একটা সস্তা ডবল বেড ছাড়া আর কোনও ফার্নিচার নেই৷ আর দরকারও নেই৷ দু-এক রাতের বেশি কেউ এখানে থাকে না। ধর মশাই ঠিক সময়েই হাজির হয়েছেন৷ চৌকিদার সবেমাত্র তিন কাপ গরম চা দিয়ে গেছে৷ চায়ের পর্ব শেষ হলে প্রণাম ধর আমাদের ওঁর সঙ্গে আনা ফোটোগুলি দেখালেন৷ তুষার শৃঙ্গের ছবি খুব কম৷ বেশির ভাগই নানান বয়সে পাহাড়ি স্ত্রীপুরুষের ছবি৷ পটু হাতের ফোটোগ্রাফ৷ কয়েকটা তো পুরস্কার পাওয়ার যোগ্য৷ কিন্তু ‘আপনাদের একটা অদ্ভুত ছবি দেখাই’ বলে যে ফোটোগ্রাফটা দেখালেন তাতে আমরা অবাক হলাম৷ একটা অস্পস্ট কালোসাদা ছবি৷ মনে হয় আউট অব ফোকাস এবং অপটু হাতে তোলা৷ ফোটোটি দেখে মনে হয় একটি শীর্ণ গোছের লোক গত শতাব্দীর তিরিশ-চল্লিশ দশকের কামিজের মতো একটা পোষাক পরে গান গাইছে৷ সঙ্গে সঙ্গত দিচ্ছে সারেঙ্গী বাদকা ও তবলা বাদক৷ আরও কিছু লোক নানান ধরনের বাদ্যযন্ত্র নিয়ে বসে আছে৷ বাদ্যযন্ত্রগুলো ঠিক চিনতে পারলাম না৷ মনে হয় বেশ পুরোনো ফোটো৷
‘এটা তো দুষ্প্রাপ্য ছবি, কোথা থেকে পেলেন’ সত্যেশবাবুর প্রশ্নে উত্তরে ধর বললেন, ‘এটা ছ-মাস আগে তোলা৷ ওই যে লোকটা দেখছেন, ও যে গানটা গাইছে ওই গান পুরাতনী সঙ্গীত৷ খুব সম্ভব নিধুবাবুর টপ্পা৷ এটা অবশ্য শশীকান্ত চক্রবর্তীর মতো৷ তবে গানটা না শুনে উনি সঠিক কিছু বলতে পারবেন না এটাও বলে ছিলেন।’
‘শশীকান্ত চক্রবর্তী মানে যিনি পুরাতনী সঙ্গীতের উপর গবেষণা করেন’ আমার কথা শুনে ধর বললেন, ‘আপনি চেনেন নাকি? শশীকান্তবাবু নিজেও খুব ভালো টপ্পা গান।’
আমি ওঁকে জানালাম শশীকান্তবাবু আমার এক কাকার বন্ধু হন৷ সেই সূত্রে চিনি৷ ‘কিন্তু আপনি বললেন এই ছবি ছ-মাস আগে তোলা৷ সেটা কী করে সম্ভব?’
আমার প্রশ্নের উত্তরে ধর বললেন এই ছবি উনি তোলেননি৷ ওঁর এক পরিচিত ভদ্রলোক, বাস্তবে ওঁর ঘনিষ্ঠ বন্ধু, তুলেছেন৷ ওঁর নাম অম্বরিষ সরখেল৷ উনি অতীতের ছবি তোলার উপর কাজ করছেন।
‘অতীতের ছবি? উনি কি টাইম ট্র্যাভেল করেন নাকি?’ সত্যেশবাবুর প্রায় ব্যাঙ্গোক্তি শুনেও প্রণাম ধর বিচলিত হলেন না৷ বললেন যে অম্বরিষবাবু বহু পুরোনো বনেদী বাড়িতে একটি বিশেষ পদ্ধতিতে অতীতের ছবি তোলেন৷ বেশ কয়েকটা স্টিল ফোটোগ্রাফ তুলেছেন৷ এই ফোটোটা উনি অম্বরিষবাবুর কাছ থেকে নিয়েছেন শশীকান্তবাবুকে দেখাবেন বলে৷ অম্বরিষবাবুর কথা অনেকেই বিশ্বাস করে না৷ তবে প্যারাসাইকোলজি চর্চা করেন এরকম কিছু লোক আসেন৷ ওঁদের ধারণা অম্বরিষবাবু হয়তো পুরোনো বাড়িতে আত্মার ছবি তোলার চেষ্টা করছেন৷ আমি বললাম যে আমি টিভিতে একটা প্রোগ্রাম দেখেছিলাম, ইংলান্ডে কিছু লোকের কাজই এই। যে সব বাড়ির হন্টেড বলে খ্যাতি আছে সেখানে ক্যামেরা ও অন্যান্য যন্ত্রপাতি নিয়ে ভূতের ছবি তোলার চেষ্টা করেন৷ ধর মশাই আমার কথা শুনে মাথা নাড়েন৷ ‘না না অম্বরিষ এই সব আত্মাফাত্মা বিশ্বাস করেন না৷ ওঁর মতে এ বিষয়টা একেবারেই বৈজ্ঞানিক ব্যাপার৷ প্যারাসাইকোলজিরও ব্যাপার নয়।’
আপনাদের যদি অম্বরিষের ফোটোগ্রাফ দেখার ইচ্ছে হয় কলকাতায় ফিরে অম্বরিষের সঙ্গে দেখা করতে পারেন৷ ও এখন অতীতের ঘটনার ভিডিয়ো রেকর্ডিং করার চেষ্টা করছে৷ ও ইলেক্ট্রিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং এর প্রফেসর ছিল৷ ও কাজ ছেড়ে দিয়েছে৷ মাঝে মাঝে দু-একটা প্রাইভেট কলেজে আর ইউনিভার্সিটিতে ক্লাস নেয়৷ পয়সাকড়ির খুব একটা অভাব নেই৷ গল্প করতে করতে খেয়াল হয়নি রাত হয়ে গেছে৷ আমরা কাল রাতও এখানে থাকব৷ কিন্তু ধর মশাই কাল সকালেই হাঁটা শুরু করবেন৷ ওঁর সঙ্গে একজন শেরপা আছে যে পোর্টার কাম কুকের কাজ করে৷ উনি দেরাদূন হয়ে মুসৌরী যাবেন৷ ওখান থেকে নাগ টিব্বা গিয়ে দেরাদুনে ফিরবেন৷ পরেরদিন দুন এক্সপ্রেসে হাওড়া৷ বাড়ি ফিরতে আরও দিনদশেক লাগবে৷ আমরাও ঠিক করেছি মুসৌরী থেকে চক্রাতায় দু-রাত থাকব৷ হিসেব করে দেখা গেল আমরা বোধহয় একই দিনে কলকাতায় ফিরব৷ আমরা অবশ্য দিল্লী থেকে রাজধানী এক্সপ্রেস ধরব৷
(৩)
কলকাতা আমরা যে দিন ফিরলাম তার দু-দিন পরেই রাত্রের দিকে আমি প্রণাম ধরকে ফোন করলাম৷ উনি ফোন ধরে বললেন যে উনি সেদিনই সকালে ফিরেছেন৷ আবহাওয়া খুব খারাপ থাকার জন্য নাগ টিব্বা অবধি যেতে পারেননি৷ উনি বললেন আজকে রাতেই উনি অম্বরিষবাবুকে ফোন করবেন৷ কাল আমাকে জানাবেন কখন আমরা অম্বরিষবাবুর সঙ্গে দেখা করতে পারি৷
আমি ঘুম থেকে দেরিতে উঠি৷ কিন্তু সকালে ফোনের শব্দে ঘুম ভেঙে গেল৷ প্রণাম ধরের ফোন৷ আমি জিজ্ঞেস করলাম, ‘অম্বরিষবাবুর সঙ্গে আপনার কথা হয়েছে?’
‘হ্যাঁ৷ আপনারা সামনের রবিবার বিকেল চারটে নাগাদ আসুন, আমি একটা বাড়ির ঠিকানা দিচ্ছি লিখে নিন।’
আমি ঠিকানাটা লিখে নিয়ে বললাম, ‘এটা তো পাথুরিয়া ঘাটায়।’
‘হ্যাঁ, ঠিকই বলেছেন, বহু পুরোনো বাড়ি৷ এককালে অনেক বিখ্যাত ব্যক্তি এই বাড়িতে আসতেন৷ মিউনিসিপ্যালিটি এখনও ঠিক করতে পারেনি বাড়িটাকে ভাঙ্গবে না হেরিটেজ বিল্ডিং হিসেবে গণ্য করবে৷ আপনি যখন পাথুরিয়া ঘাটা চেনেন তখন আসতে অসুবিধে হবে না আশা করি৷ সঙ্গে একটা টর্চ নিয়ে আসবেন৷’
প্রণামবাবু যে ঠিকানাটা দিয়েছিলেন সেটা আমি চিনে নিতে পারব৷ ওই অঞ্চলটাতে বেশ কয়েকবার গেছি৷ আমার বাবার এক পিসতুতো ভাই ওখানে থাকতেন৷ আমরা সমুকাকা বলে ডাকতাম৷ সমুকাকার বাড়িতে বেশ কয়েকবার গেছি৷ সমুকাকা মারা যাওয়ার পরে ওঁর দুই ছেলে শুনেছি বাঙ্গুরে একটা বাড়ি কিনে ওখানে চলে গেছে৷ বহুদিন ওদের সঙ্গে যোগাযোগ নেই৷ যাই হোক আমি সত্যেশবাবুকে এই খবরটা দিলাম৷ সত্যেশবাবু কিছুদিন মিলিটারিতে ছিলেন৷ তারপর কেন্দ্রীয় সরকারের বিভিন্ন দপ্তরে কাজ করেছেন৷ বেশ কিছুদিন দিল্লীতে ছিলেন৷ এখন কেন্দ্রীয় সরকারের অধীনস্থ কয়েকটি জুট মিলের দায়িত্বে রয়েছেন। কোনও জুট মিলই কোলকাতা থেকে খুব বেশি দূর নয়৷ ঠিক হল আমি রবিবার তিনটের সময় সত্যেশবাবুর বাড়ি যাব৷ ওখান থেকে ওঁর গাড়িতে পাথুরিয়া ঘাটায় যাব৷
(৪)
আমরা যখন পাথুরিয়া ঘাটার প্রণাম ধরের ঠিকানার প্রাচীন বাড়িতে পৌঁছলাম তখন চারটে বাজতে দশ মিনিট বাকি৷ বাড়িটা অনেকখানি জায়গা জুড়ে৷ এককালে বোধহয় জমকালো গেট ছিল৷ এখন ভগ্নদশা৷ গেটের সামনে একটা বড় পাকুড় গাছ৷ গাছের নীচেই ধর মশাই অপেক্ষা করছিলেন৷ ‘আপনারা ঠিক সময়ে এসে গেছেন৷ বাড়ির ভিতর অম্বরিষ আছে৷ চলুন আমার সঙ্গে।’ ভগ্নবাড়ি হলেও দোতলার কয়েকটি ঘর একেবারে ভেঙে পড়েনি৷ দোতলায় একটা বড় ঘরে একটা টেবিল ও চেয়ার৷ এগুলি খুব একটা পুরোনো নয়৷ টেবিলের উপর একটা বিশাল ইলেকট্রিক ভোল্টেজ স্টেবিলাইজের মতো যন্ত্র৷ তবে মনে হল ভোল্টেজ স্টেবিলাইজার নয়৷ চেয়ারে অম্বরিষবাবু বসেছিলেন৷ দরজার দিকে ওঁর মুখ ছিল৷ আমাদের দেখে উঠে এসে করমর্দন করে বললেন, ‘আমার নাম অম্বরিষ সরখেলা৷ প্রণাম বোধহয় আমার গবেষণার কথা আপনাদের বলেছে।’
‘অম্বরিষ আমি তো টেকনিক্যাল কিছু ওঁদের বলিনি কারণ আমি নিজেই পুরোটা বুঝিনি৷ কিন্তু রাজীববাবুকে তুমি বুঝিয়ে বললে উনি বোধহয় বুঝবেন৷ উনিও একজন বিজ্ঞানী৷ উনি অতীতের ছবি কী করে তোলা হয় এসব ব্যাপারে খুবই আগ্রহী।’
অম্বরিষবাবুর বয়স বোধহয় পঞ্চাশের মতন হবে৷ সুগঠিত চেহারা৷ রং ফর্সার দিকে। একটা কালো জিনস ও হলুদ রঙের টি শার্টে বেশ স্মার্ট দেখাচ্ছিল৷ হাইট দেখে মনে হয় পাঁচ দশ৷ চোখ দুটো বাদামি আর খুবই উজ্বল৷ মনে হয় টেনিস খেলতেন একসময়৷ হয়তো এখনও খেলেন৷ প্রণামবাবুর কথা শেষ হলে আমি অম্বরিষবাবুকে জিজ্ঞেস করলাম, ‘আপনি কোন ক্যামেরায় এই অতীতের ছবি তোলেন?’ ‘এটা ক্যামেরা নয়, এক ধরনের ইলেকট্রোগ্রাফ বলতে পারেন। ইলেকট্রোগ্রাফ মানে যে যন্ত্রকে কিরলিয়ান ফোটোগ্রাফ বলা হয়।’
‘আপনি দেখছি এ ব্যাপারে কিছু জানেন।’ অম্বরিষবাবুর কথা শুনে আমি বললাম যে প্যারাসাইকোলজির উপর কিছু লেখা পড়ে এটার ব্যাপারে কিছুটা জানতে পেরেছি।
‘এটাই কিরলিয়ানের দুর্ভাগ্য। প্রথমদিকে ওঁর আবিষ্কারকে সিরিয়াসলি নেওয়া হয়নি। শেষ জীবনে অবশ্য উনি স্বীকৃতি পেয়েছিলেন। আসলে উনি দাবি করেছিলেন খুব অল্প সময়ের জন্য হলেও উনি অতীতের ছবি তুলতে পেরেছিলেন।’
‘সেটা কীরকম?’ আমার প্রশ্ন শুনে অম্বরিষ বললেন, ‘একটা গাছের পাতার উনি ছবি তুলেছিলেন যার একটা অংশ কেটে দেওয়া হয়েছে৷ ওঁর ফোটোগ্রাফে ওই অংশটার ছবি উঠেছিল৷ পরে অবশ্য অন্য বিজ্ঞানীদের পরীক্ষায় এটা ধরা পড়েনি৷ বিজ্ঞানীদের মতে ইলেকট্রিক্যাল ডিসচার্জের এফেক্ট ফিল্মের উপর পড়েছে, তার বেশি কিছু এটা নয়। কিন্তু ওঁর আবিষ্কারের উপর এখনও কাজ চলছে।’
সত্যেশবাবু বললেন, ‘এটা কি নতুন ধরনের ক্যামেরা৷ এরকম ক্যামেরার নাম তো আগে শুনিনি।’
‘আসলে এটা ঠিক ক্যামেরা নয়৷ বরং একটা ইলেকট্রিক্যাল গ্যাজেট বলতে পারেন। একটা ধাতব প্লেটের উপর একটা ফিল্ম থাকে৷ খুব হাই ভোল্টেজ কারেন্ট ওই ধাতব পদার্থের মধ্য দিয়ে প্রবাহিত হলে যে বস্তুর ছবি তুলতে চান তা ওই ফিল্মের সাহায্যে তোলা যায়৷ আমি হয়তো খুব সহজ করে বললাম৷ টেকনিক্যাল সংজ্ঞা জানতে আগ্রহী থাকলে আমার একটা লেখা আছে পড়তে পারেন, এখন আপনি এ বিষয়ের উপর বই কিনে নিজেই এটা বানাতে পারেন৷ কিন্তু আমি এর সঙ্গে ডিজিটাল ক্যামেরা জুড়তে পেরেছি৷ ডিজিটাল ক্যামেরায় যা ছবি উঠবে একটা কমপিউটারে তা রেকর্ড হয়ে যাবে।’
‘আপনি কি এক্টোপ্লাজমের ছবি তোলার ছবি তোলার চেষ্টা করছেন?’ সত্যেশবাবুর প্রশ্ন শুনে অম্বরিষ হো হো করে হেসে উঠলেন। ‘দেখুন আমি প্যারাসাইকোলজির লোক নই। এটা পুরোপুরি বৈজ্ঞানিক ব্যাপার। কি করে কয়েকটা স্টিল ছবি কমপিউটারে রেকর্ডেড হয়ে গেল আমি বুঝতে পারছি না। তবে এবার আশা করি ভিডিয়োর মতো কিছু অতীতের দৃশ্য পাব আশা করছি।’
আমি বললাম হয়তো আপনার ক্যামেরা বা ইলেকট্রোগ্রাফ টাইম ট্র্যাভেল করছে খুব অল্প সময়ের জন্য।’
‘সেটা সম্ভব নয়৷ টাইম ট্র্যাভেল এখনও সায়েন্স ফিকশন৷ তবে ভবিষ্যতে কী হবে জানি না।’
এরপর অম্বরিষবাবু আরও কয়েকটা ফোটোগ্রাফ দেখালেন। পোষাকআষাক দেখে বোঝা যায় অন্তত পঞ্চাশ বছর আগের ছবি। একটি ছবিতে একটি মেয়ে নাচের ভঙ্গীতে দাঁড়িয়ে আছে।’
সত্যেশবাবু রসিক লোক। বললেন ‘এই রেটে গেলে আপনি ডাইনোসরের ছবিও পেয়ে যাবেন।’ সত্যেশবাবুর কথা শুনে অম্বরিষবাবু হাসলেন না৷ শুধু বললেন, ‘অতদূর আশা করি না।’
অম্বরিষবাবু আশ্বাস দিলেন উনি ইন্টারেস্টিং কিছু ছবি তুলতে পারলে আমাদের জানাবেন৷ এরপর সৌজন্যমূলক দু-চার কথার পর আমরা বিদায় নেলাম৷
(৫)
এরপর ঘটনা নাটকীয় মোড় নিল৷ পাথুরিয়া ঘাটা যেদিন গিয়েছিলাম তার দু-দিন পরই প্রণাম ধরের ফোন এল৷ অম্বরিষবাবু নাকি একটা বিচিত্র ভিডিয়ো তুলতে পেরেছেন ওঁর যন্ত্রে, যেটার উনি নাম দিয়েছিলেন কিরলিয়ান ভিডিয়োগ্রাফ৷ আমরা যেন বিকেলে অবশ্যই আসি অম্বরিষবাবুর বাড়িতে৷ প্রণামবাবু যে ঠিকানাটা বললেন ওটা টালিগঞ্জে কবিশেখর কালিদাস রায়ের বাড়ির কাছে৷
আমি সত্যেশবাবুকে ফোন করে জানাতে উনি বললেন উনি সোজা অফিস থেকে আমার বাড়ি থেকে আমাকে তুলে নিয়ে যাবেন৷ আমি রাসবিহারী এভিনিউতে থাকি৷ এখান থেকে অম্বরিষবাবুর বাড়ি খুব কাছে৷ আমি যখনকার কথা বলছি তখনও মোবাইল ফোন কলকাতায় খুব একটা চালু হয়নি৷ ১৯৯৫ সালে আগস্ট মাসে তৎকালীন বাংলার মুখ্যমন্ত্রী জ্যোতি বসু প্রথম ঐতিহাসিক মোবাইল কলটি করেছিলেন তৎকালীন কেন্দ্রীয় টেলিকমমন্ত্রী সুখরামকে৷
যাইহোক সত্যেশবাবুর গাড়িতে করে আমরা যখন অম্বরিষবাবুর বাড়িতে পৌঁছলাম তখন সাড়ে পাঁচটা বেজে গেছে। অম্বরিষবাবু বাড়ির সামনেই দাঁড়িয়েছিলেন। কোনও ভূমিকা না করে ওঁর ল্যাবরেটরি কাম রিডিং রুমে আমাদের নিয়ে গেলেন। ঘরের এক কোণে একটা বড় টেবিল। দুটো কমপিউটার। শুনলাম আমেরিকা থেকে আনিয়েছেন। ইলেকট্রোগ্রাফ যন্ত্রটা তো আছেই। তখন ডিজিটাল ক্যামেরার সাইজও বেশ বড় ছিল। এখনকার মুভি ক্যামেরার মতো নয়। অম্বরিষবাবু বোঝাচ্ছিলেন পরপর ছবিগুলো তুলো কমপিউটারে দেখলে মনে হবে কেটে কেটে যাওয়া মুভি। ইলেকট্রোগ্রাফ ও ডিজিটাল ভিডিয়ো ক্যামেরার সংমিশ্রণ ওঁরই আবিষ্কার উনি কিছু দিন রাশিয়াতে ছিলেন। কিরলিয়ান ফোটোগ্রাফি বিশেষজ্ঞ আলোকজান্দার ইওফের সঙ্গে কাজ করেছেন। অবশ্য ইওফেরই বয়স ছিল তখন সত্তরের কাছাকাছি। অম্বরিষবাবু এবার একটা কমপিউটারে কিছু ছবি আমাদের দেখালেন। মনে হল কতকগুলি স্টিল ফোটো খুব দ্রুত বদলাচ্ছে। এর সঙ্গে অডিয়ো রেকর্ডিংও আছে। মানে উনি শুধু অতীতের ছবি নয় শব্দও ধরতেও সক্ষম হয়েছেন।
যেটুকু দেখলাম তাতে মনে হল তানপুরা হাতে নিয়ে বহু পুরোনো দিনের পোষাক পরা মাঝবয়সি একটি লোক গান গাইছে৷ মাথায় সাদা পাগড়ি। সামনে মাটিতে সতরঞ্চির উপর বেশ কিছু লোক বসে আসে৷ আর জমিদার সুলভ বেশ রাশভারী চেহারার দুটি লোক গায়কের দু-পাশে চেয়ারে বসে আছে। এদের মাথায় বেশ বড় পাগড়ি। দেখে মনে হয় জমজমাট গানের আসর। গানের দুটি কলিই গায়ক বার বার গাইছিল। বেশ সুরেলা গলা। আমি যতদূর বুঝতে পারছিলাম গানটির প্রথম দুটি লাইন ছিল ‘আমি কি কখনও তোমারে না দেখে সইতে পারি৷’ হঠাৎ সত্যেশবাবু বলে উঠলেন ‘আরে এ যে নিধুবাবুর টপ্পা গাইছে।’ আমি জানতাম সত্যেশবাবুর পুরাতনী সঙ্গীতের উপর খুব আগ্রহ আছে। বাড়িতে পুরাতনী সঙ্গীতের ভালো কালেকশন আছে। ‘আপনি বুঝলেন কী করে এটা নিধুবাবুর টপ্পা।’ আমার প্রশ্ন শুনে সত্যেশবাবু উত্তেজিত হয়ে বললেন, ‘তুমি অমরগীতি দেখনি। তরুন মজুমদারের ছবি। নিধিবাবু মানে রাম নিধি গুপ্তের জীবনী অবলম্বনে করা হয়েছে, এই গানটা ওই সিনেমায় বোধহয় আরতি মুখার্জী নাাহলে অরুন্ধতী হোমচৌধুরী গেয়েছিলেন।’ প্রণাম ধর বললেন, ‘শশীকান্তবাবুকে এটা দেখিয়েছিলাম। উনি বললেন এটা নিধুবাবুরই গান। তবে উনি বললেন অমরগীতি ছবির সব গানগুলি নিধিবাবুর নয়। তবে ওঁর নামে চলে আসছে। ওঁর মতে সবচেয়ে জনপ্রিয় গান, ‘অনুগত জনেরে প্রিয়ে কেন এত প্রবঞ্চনা’ এই গানটা নিধুবাবুর নামে চলে আসছে কিন্তু এটা নিধুবাবুর গান নয়৷ আমি বললাম ‘ইলেকট্রোগ্রাফের তোলা ফোটোতে যার ছবি দেখছি সে লোকটি কে?’
আমার প্রশ্ন শুনে ধর বললেন, ‘শশীকান্তবাবুর মতে ওটা কালীপ্রসাদ ঘোষ স্বয়ং অথবা তাঁর কোনও ছাত্র হতে পারে৷’ অম্বরিষবাবু এতক্ষণ চুপচাপ আমাদের কথা শুনছিলেন। কমপিউটারের দিকে চোখ রেখেই বললেন, ‘শশীকান্তবাবুকে একটা জিনিস দেখাইনি আপনাদের দেখাচ্ছি।’ আমরা সবাই একসঙ্গে কমপিউটারের সামনে ঝুঁকে দাঁড়িয়ে পড়লাম অবশ্য ধরমশাই ছাড়া। উনি নিশ্চয়ই এটা আগে দেখেছেন৷ অম্বরিষবাবু বোধহয় আমাদের যা দেখাবেন তা একটা আলাদা ফাইলে রেখে দিয়েছিলেন৷
ফাইল খুলে আমাদের বললেন, ‘ভিডিয়োটা একটু অস্পষ্ট কিন্তু বুঝতে পারবেন আশা করি।’ ভিডিয়োর যে অংশটা আমরা দেখতে পেলাম তাতে গায়কের এবং বিভিন্ন বাদ্যযন্ত্রের বাদকদের দেখা যাচ্ছে না। শুধু শ্রোতাদের এক অংশ দেখা যাচ্ছিল, তাও যারা একেবারে পিছনে ঘরে দরজাটার সামনে। পিছনে একজন লোক বসেছিল মাথায় লালচে রং এর ফেজ টুপি। ঠিক তার পিছনে একটি দোহারা চেহারার লোক বসে৷ প্রায় সারা শরীরই আলোয়ানে ঢাকা৷ মাথায় সাদা পাগড়ি। হাত দুটি আলোয়ানের ভিতর ঢোকানো। গানের আওয়াজ শোনা যাচ্ছে। হঠাৎ আলোয়ানপরা লোকটি ডান হাতটা আলোয়ান থেকে বার করল। আমরা অবাক হয়ে দেখলাম লোকটার হাতে একটা আট ইঞ্চির মতো লম্বা ছুরি৷ নিমেষের মধ্যে সে ছুরিটা ফেজ টুপির পিঠে শির দাঁড়ার নিচের দিকে ঢুকিয়ে দিল৷ ফেজ টুপি আর্তনাদ করে উঠলে সব শ্রোতাদের দৃষ্টি তার দিকে পড়ল৷ প্রায় সবাই একসঙ্গে কথা বলতে শুরু করল আর এই হইচই এর সুযোগ নিয়ে আলোয়ান বাইরে পালিয়ে গেল৷ ভিডিয়োটাও শেষ হয়ে গেল৷ অম্বরিষবাবু বললেন, ‘এরপর আর কোনও ছবিই তুলতে পারিনি।’
‘আপনার ভিডিয়োটা তো পুলিশকে জমা দেওয়া উচিৎ।’ সত্যেশবাবুর কথা শুনে অম্বরিষবাবু একটু শুকনো হাসি হেসে বললেন, ‘পুলিশ? বিজ্ঞানীদেরই বোঝাতে পারছি না৷ পুলিশ হয়তো আমাকেই হাজতে রেখে দেবে৷ আপনাদের ডাকলাম কারণ আপনারা হয়তো বিশ্বাস করবেন এরকম ভিডিয়ো নিজে বানানো যায় না। সত্যেশবাবু কী যেন ভাবছিলেন৷ হঠাৎ বললেন, ‘হ্যাঁ, মনে পড়েছে কেন আমি পুলিশের কথা বললাম৷ এরকম একটা ঘটনা আমার বাবার এক বন্ধুর কাছে শুনেছি৷ ওঁর নাম ছিল গোপাল কিশোর চৌধুরী৷ উনি টপ্পা গানের খুব ভক্ত ছিলেন৷ আপনি যে গানের আসর দেখালেন আমার মনে হয় এটার কথাই একদিন গোপালবাবু আমাদের বলেছিলেন৷ যে লোকটি খুন হয় সে একজন মুসলিম গায়ক ছিল৷ বেশ নাকি ভালো কালোয়াতি গান গাইত৷ কিন্তু ওই খুনের রহস্য পুলিশ ভেদ করতে পারেনি কিন্তু এটা সত্যিই তাজ্জব ব্যাপার যে এই খুনের ব্যাপার আপনার ইলেকট্রোগ্রাফে ধরা পড়ল।’
‘এর কারণ আমি এমন ব্যবস্থা করেছিলাম যে আমার বানানো যন্ত্রটা আস্তে আস্তে ঘোরে৷ একবার ডানদিকে তারপর সোজা তারপর বাঁ-দিকে যাতে প্রায় ঘরের সব জায়গা কভার করে।’
অম্বরিষবাবুর ব্যাখ্যা শুনে সত্যেশবাবু বললেন, ‘খুব ভালো ব্যবস্থা৷ আপনার যন্ত্র দেখছি ক্রাইম ডিটেকশনে ও খুব উপকারে আসবে।’
অম্বরিষবাবু বললেন যে পাথুরিয়া ঘাটায় আর বোধহয় কোনও ছবি তোলা যাবে না৷ উনি ঠিক করেছেন উনি বেনারসে যাবেন৷
‘বেনারসে কেন?’ আমার প্রশ্ন শুনে অম্বরিষবাবু বললেন যে বেনারসে কে পি শর্মা বলে একজন ইঞ্জিনিয়ারিং এর অধ্যাপক আছেন৷ উনিও নিজের উদ্যোগেই ইলেকট্রোগ্রাফ নিয়ে কাজ করছেন৷ কতকগুলো ইন্টারেস্টিং ছবি তুলে অম্বরিষবাবুকে পাঠিয়েছেন৷ ড. শর্মার সঙ্গে অম্বরিষবাবুর রাশিয়ায় আলাপ হয়৷ এর পরে অম্বরিষবাবুর নিজের বানানো টার্কিশ কফি খেয়ে আমরা বিদায় নিলাম৷ আরও কিছু ইন্টারেস্টিং ছবি পেলে উনি আমাদের আবার ডাকবেন বলে প্রতিশ্রুতি দিলেন৷
সত্যেশবাবুর সঙ্গে গাড়িতে বাড়ি যাওয়ার সময় সত্যেশবাবু বললেন, ‘রাজীব তোমার কী মনে হয়? সত্যি কি অতীতের ছবি তোলা যায়? তুমি তো একজন বিজ্ঞানী।’
আমি বললাম, ‘ব্যাপারটা পুরো বুঝতে পারছি না৷ আজকে যা দেখলাম সেটা পুরো উড়িয়ে দিতে পারছি না৷ পুরোটাই ম্যানুফ্যাকচারড এটা বিশ্বাস করা শক্ত৷ অম্বরিষবাবুর কথা অনেক বিজ্ঞানী বিশ্বাস করছেন না এর কারণ হিংসাও হতে পারে৷ বিজ্ঞানে এরকম প্রচুর উদাহরণ আছে৷ লামার্কের কথাই ধরুন না৷ ওঁর থিয়োরি ডারউইনের থিয়োরির সঙ্গে মিলছিল না বলে প্রচুর বিদ্রুপের সম্মুখীন হয়েছেন৷ প্রচণ্ড দারিদ্রে শেষ জীবন কেটেছে৷ অথচ এখন বিজ্ঞানীরা নতুন করে ওঁর থিয়োরি আলোচনা করছেন আমার মনে হয় যে সব বিজ্ঞানীরই সিধুজ্যাঠার মতো মনের সব ক-টি জানলা খুলে রাখা উচিৎ৷ ওঁর যন্ত্র হয়তো খুব অল্প সময়ের জন্য টাইম ট্র্যাভেল করছে।’
সত্যেশবাবু বললেন, ‘সত্যিই তাই৷ কত কিছুই আমরা জানি না।’ আমাকে আমার বাড়িতে নামিয়ে দিয়ে সত্যেশবাবু চলে গেলেন৷
(৬)
এরপর বেশ কিছু দিন কেটে গেছে৷ প্রণাম ধর বা অম্বরিষবাবুর সঙ্গে আর যোগাযোগ হয়নি৷ সত্যেশবাবু ইংল্যান্ডে চলে যান ওঁর ছেলের কাছে৷ ওঁর ছেলে অরিজিত বার্মিংহামে থাকে৷ আমিও তিন মাসের জন্য ইটালিতে ছিলাম৷ ইটালি থাকার সময় একটা আমেরিকান পত্রিকায় অম্বরিষবাবুর কাজের উপর একটা লেখা পড়েছিলাম৷ কিন্তু সেখানেও উল্লেখ ছিল যে ওঁর গবেষণা এখনও প্রাতিষ্ঠানিক স্বীকৃতি পায়নি৷
ইটালি থেকে ফেরার প্রায় একমাস পর একদিন প্রণাম ধরের ফোন আসে৷ উনি তো খুবই খারাপ খবর দিলেন৷ অম্বরিষবাবু বেনারসে হঠাৎ হার্টফেল করে মারা যান৷ উনি একটি প্রায় দুশো বছরের পুরোনো বাড়িতে ওঁর যন্ত্র দিয়ে অতীতের ছবি তোলার ব্যবস্থা করার সময় হঠাৎ মাটিতে পড়ে যান৷ ওঁর সঙ্গে তখন কে পি শর্মাও ছিলেন৷ হাসপাতালে নিয়ে যাবার পথেই ওঁর মৃত্যু হয়৷ অথচ ওঁর হার্টের কোনও সমস্যাই ছিল না৷ ওঁর ইলেকট্রোগ্রাফ এখন ড. কে পি শর্মার কাছে আছে৷ তবে উনি বেনারস যাওয়ার আগে ওঁর গবেষণা সংক্রান্ত সব রিপোর্টের একটা কপি প্রণাম ধরকে দিয়ে যান৷ এ ছাড়া অম্বরিষবাবুর নিজের হাতে টাইপ করা একটা থিসিসও প্রণাম ধরের কাছে আছে৷ এরপর প্রণাম ধর যা বললেন তাতে আমি অবাক হলাম। ‘জানেন রাজীববাবু আমার মনে হয় বেনারসে যাবার আগে উনি বোধহয় টের পেয়েছিলেন অতীতের ছবি তুলতে তুলতে উনিও একদিন অতীত হয়ে যাবেন।’ আমি ওঁর কথা শুনে বললাম, ‘কেন আপনার এরকম মনে হচ্ছে?’
‘দেখুন ওঁর মধ্যে একটা হতাশার ভাব এসেছিল৷ কোনও নামকরা জার্নালে উনি কোনও পেপার ছাপাতে পারেননি৷ রাশিয়া ও পোলান্ডের অখ্যাত কয়েকটি জার্নালে কয়েকটি পেপার উনি ছাপিয়ে ছিলেন৷ সেগুলিও এখন দুষ্প্রাপ্য৷ আর উনি যাবার আগে আমায় জোর করে বেশ কিছু টাকা দিয়ে যান৷ বলেছিলেন ওঁর মৃত্যুর পর যেন থিসিসটা ছাপানো হয়৷ যে সব বিজ্ঞানীদের কাছে থিসিস পাঠাতে হবে তার একটা লিস্টও উনি আমাকে দিয়ে যান৷ আর আপনার নাম করে আমাকে বললেন দরকার পড়লে রাজীববাবুর সাহাষ্য নিও।’ আমি ওঁকে আশ্বাস দিলাম ভালো পাবলিশার্স যাতে এটা ছাপায় সেটা আমি দেখব৷
সত্যেশবাবু ইংল্যান্ড থেকে ফিরে অফিসের কাজে দিল্লী গিয়েছিলেন৷ গতকালই ফিরেছেন৷ আমি ওঁকে ফোন করে অম্বরিষবাবুর মৃত্যুর খবরটা দিলাম৷ সত্যেশবাবু বললেন, ‘রাজীব খুবই খারাপ খবর৷ আচ্ছা রাজীব তোমার কী মনে হয় আমাদের জগদীশ বোসের মতো অম্বরিষ ওয়াজ অ্যাহেড অব হিজ টাইম?’ আমি বললাম, ‘আমার ও তাই মনে হয়৷ আমার মনে হয় অম্বরিষবাবু একটা পথ দেখিয়ে গেছেন৷ আমি নিশ্চিত এ বিষয়ে দেশে বিদেশে আরও কাজ হবে।’
(৭)
অম্বরিষবাবু মারা যাওয়ার পর বহুদিন হয়ে গেছে৷ সময় তো আর কারুর জন্য অপেক্ষা করে না৷ আমিও বার্ধক্যের দোরগোড়ায় এসে পৌঁছেছি৷ দশ বছর হল সত্যেশবাবু মারা গেছেন৷ অনেকদিন ধরে কিডনীর প্রবলেমে ভুগছিলেন৷ আমি অম্বরিষবাবুর থিসিস ছাপানোর ব্যবস্থা করে দিয়েছিলাম৷ প্রণাম ধর অম্বরিষ বাবুর লিস্ট অনুযায়ী বেশ কিছু বিজ্ঞানীদের কাছে একটা করে কপি পাঠিয়েছিলেন৷ কয়েকজন বেশ উৎসাহজনক চিঠি লিখে পাঠিয়েছিলেন৷ কিন্তু তা দেখার লোকটাই তো ছিল না৷ এখন শুনছি বিদেশে অনেকেই ইলেকট্রোগ্রাফের উপর কাজ করছেন৷ জানি না কোনওদিন অম্বরিষবাবুর কাজ স্বীকৃতি পাবে কি না৷ গতকালই আর একটা খারাপ খবর পেলাম প্রণাম ধর মারা গেছেন৷ মর্মান্তিক ঘটনা৷ একটা হাইরাইজ বিল্ডিং-এর ছাদ থেকে লাফ দিয়ে আত্মহত্যা করেছেন৷ ওঁর এক ভাইপো আমায় ফোন করে খবরটা দেয়৷ তালুকার সেই সন্ধ্যা, পাথুরিয়ার ঘাটার সেই বাড়িতে যাওয়া, অম্বরিষবাবুর যন্ত্রে তোলা নিধুবাবুর টপ্পা গান আর সেই রোমহর্ষক হত্যার দৃশ্য এখনও মাঝে মাঝে চোখের সামনে ভাসে৷ মনের থেকে ভালো ইলেকট্রোগ্রাফ আর কি হতে পারে!

Tags: কল্পবিজ্ঞান গল্প, পঞ্চম বর্ষ তৃতীয় সংখ্যা, রাজকুমার রায়চৌধুরী, সৌরভ ঘোষ